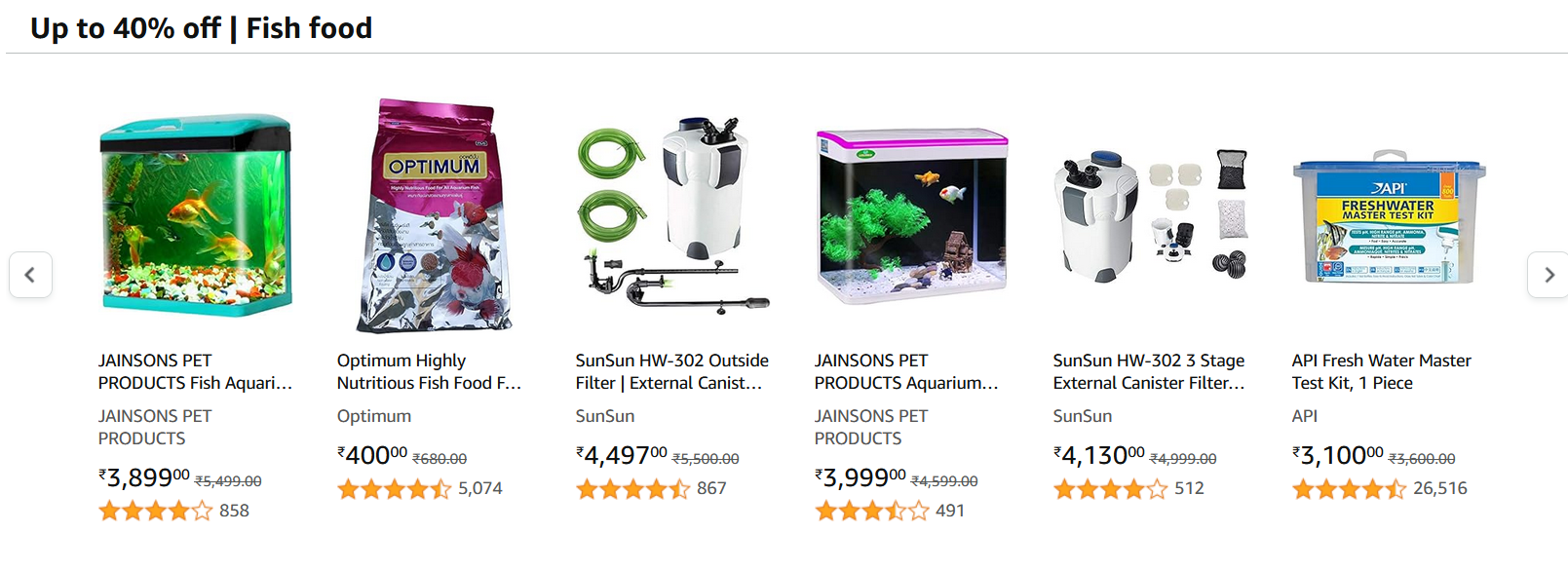|
| মনসামঙ্গলের কাহিনী |
মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল মঙ্গলকাব্য। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত—এমনকি তারও পরে অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। গোটা বাংলাদেশেই এই মঙ্গলকাব্যসমূহের অসাধারণ প্রভাব দেখা যায়। এখনও পল্লী অঞ্চলে মঙ্গলকাব্যের কোনো কোনো দেবদেবীর ঘটা করে পূজা হয়। এই উপলক্ষে দেবদেবীর মহিমাবিষয়ক গান করা হয়। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচারসম্বন্ধীয় একপ্রকার আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে। এই দেবদেবীদের অনেকেই আর্যপরিমণ্ডলের নন, বাংলার গ্রাম্য পরিবেশে ও সমাজে এঁদের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। তাই এঁরা লৌকিক ও অপৌরাণিক গ্রামীণ আদর্শ থেকেই উদ্ভূত। এ-দেশে আর্যসংস্কৃতি ও দেবদেবী-তত্ত্ব দৃঢ়মূল হবার আগে অস্ট্রিক গোত্রসম্ভূত আর্যেতর জাতি বাস করত তা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। পরে আর্য হয়ে যাবার পর প্রাচীন বাঙালি তার পুরাতন সংস্কার ভুলে গেল, অতি দ্রুত আর্য শিক্ষাসংস্কৃতিতে দীক্ষা নিল, আৰ্য দেবদেবীকে নিজেদের উপাস্য দেবতা বলে গ্রহণ করল। এই ব্যাপার সমাধা হতে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছে। তবু পুরাতন আর্যের দেব-বিশ্বাস বাঙালির মন থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি। বিশেষত সমাজের নিম্নস্তরে এবং স্ত্রী-সমাজে, যেখানে আর্য-প্রভাব পৌঁছতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল, সেখানে তথাকথিত অনার্য প্রভাব বিশেষত দেবদেবীদের প্রভাব অনেক দিন প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল। এখনও বাংলার পল্লীতে নানা গাছতলায় যে সমস্ত দেবদেবী মহিলাসমাজ কর্তৃক পূজিত হন, তাঁদের কেউ-ই সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা পরিশুদ্ধ নন। পুরাণ গ্রন্থে তাঁদের ঠাঁই মেলেনি। চণ্ডী, মনসা, বাশুলী, ধর্ম, পঞ্চানন প্রভৃতি লৌকিক অর্থাৎ গ্রামের দেবদেবী বাঙালির আর্যের সংস্কার বহন করছেন।
বিপদে-আপদে পড়লে মানুষ ভয়ে ভক্তিতে দেবদেবীর শরণ নেয়। বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উৎপত্তির মূলে এই রকম নানা ধরনের আধিভৌতিক আপদ-বিপদের প্রভাব আছে। হিংস্র শ্বাপদের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনা, সাপের বিষদত্ত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার পরিকল্পনা। বসন্তু রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শীতলার উৎপত্তি ; এমনকি বাঘের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিম্নবঙ্গে বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের মূর্তি গড়িয়ে পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী অনেক পূর্ব থেকে ছড়ায়, পাঁচালিতে, মেয়েলি ব্রতকথায় নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে সাহিত্য ও সমাজে নতুন করে তাঁদের প্রভাব দেখা গেল। তখন বাংলাদেশে পাঠান আমল চলেছে, তারপর এলো মুঘল আমল। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দারুণ বিপর্যয়ের ফলে সাধারণ বাঙালি হিন্দুর মনে শান্তি ছিল না। তারা তখন এই সমস্ত উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য এমন শক্তিশালী দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল, যাঁদের স্বল্পতম কৃপাকটাক্ষ লাভ করলে ফকিরও রাজা হতে পারে, মূর্খ ব্যাধও বন কেটে রাজত্ব ফাঁদতে পারে। তাই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী, বিশেষত দেবীরা, ভক্তের কাছে বরাভয় মূর্তিতে হাজির হয়েছেন। ভক্তের জন্য তাঁরা পারেন না, এমন কোনো কাজ নেই। ভক্তের জন্য তাঁরা ন্যায়-অন্যায়বোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে ভক্তের শত্রুর বিরুদ্ধে বিনা কারণে খড়াহত হয়েছেন। তাই তাঁদের রুমি-তুষ্টি বড়ো ভয়ংকর। এই সমস্ত দেবদেবীর পরিকল্পনার মূলে কিঞ্চিৎ রূঢ়-রুক্ষ আর্যের প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সমাজে পৌরাণিক প্রভাব গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরাও জাতে উঠতে লাগলেন। আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য ব্যাধ জাতির দেবী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। সাপের দেবী ভয়ংকরী মনসা যে আর্যমণ্ডল-বহির্ভূত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সমন্বয়ের যুগে তাঁকে শিবের মানসকন্যা বলে প্রচার করা হল। পুরুষ-দেবতা ধর্মঠাকুর পৌরাণিক না হলেও তাঁকে প্রায় বিষ্ণু করে তোলা হয়েছে। তাই একদা এই সমস্ত আর্যের গ্রাম্য দেবদেরী নিম্নসমাজে পূজিত হলেও খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে সমন্বয়ের যুগ শুরু হলে তাঁরা উচ্চ বর্ণেরও শ্রদ্ধা লাভ করলেন। ব্রাহ্মণ কবিরা পূর্বতন সংস্কার বিস্মৃত হয়ে চণ্ডী-মনসা-বাণ্ডলী-ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা ও তাঁদের মহিমা প্রচারক কাব্য-রচনায় মহানন্দে আত্মনিয়োগ করলেন।
সাধারণত অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর পূজা প্রচারিত হয় আর সেই প্রচারকার্য সমাধা হয় দেবীর কোনো ভক্তের দ্বারা—যিনি পূর্বে ছিলেন স্বর্গের অধিবাসী। তাঁর দ্বারা মর্ত্যধামে পূজা প্রচারের জন্য দেবী তাঁকে বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে শাপ দিয়ে মর্ত্যে মানুষ- জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচারের পর তবে শাপভ্রষ্ট দেবকুমার বা স্বর্গের কোনো নর্তকী মর্ত্যদেহ ত্যাগ করে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যাবার অনুমতি পান। তাই মঙ্গলকাব্যের খানিকটা অংশে দেবকাহিনী, বাকি অংশে মর্ত্যকাহিনী বর্ণিত হয়। প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভ ভাগে শিবের ঘরগৃহস্থালি জীবন্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এই শিবের গ্রাম্য মানসিকতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, বাঙালির আর্যের সংস্কারের সঙ্গে শিবের যোগাযোগ বহুদিন পূর্ব থেকেই চলে আসছে। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবদেবী মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও শিবকে কেন্দ্র করেই অনেকগুলি আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে। একদা এঁদের ভক্তসংখ্যা ছিল অনেক—এখনও গাছতলে ও পুরাতন মন্দিরে এঁদের শিলামূর্তি বা মৃন্ময় মূর্তির পূজা হয়, সেই পূজা উপলক্ষে দেবদেবীর মহিমাবিষয়ক মঙ্গলকাব্য পঠিত ও গীত হয়। বর্তমানকালে গ্রামে মনসা ও ধর্মঠাকুরের খুব ঘটা করে পূর্জা-অর্চনা হয়ে থাকে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মহিমা এখন নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও মনসা ও ধর্মঠাকুর এবং উক্ত দেবদেবীর মহিমাজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্য জনসাধারণের মধ্যে বেশ উৎসাহ সঞ্চার করে। এর ওপরে আর্য-সংস্কার ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের পালিশ পড়লেও পুরাতন আর্যেভর সংস্কার দুর্নিরীক্ষ্য নয়। চণ্ডী, মনসা ও ধর্মঠাকুরের লীলাকাহিনী-বিষয়ক মঙ্গলকাব্যগুলি সাহিত্যের দিক থেকে প্রশংসনীয় বলে আমরা এই গ্রন্থে প্রধানত এই তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য আলোচনা করব। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে কয়েকখানি মনসা- মঙ্গল কাব্য লেখা হয়েছিল বলে এই অধ্যায়ে শুধু মনসামঙ্গলের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।
মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা, কেতকা, পদ্মাবতী। তাই এই কাব্যকে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ বলে। মনসাভক্ত কবিরাও নিজেদের কেতকাদাস বলতেন। পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলের একজন বিখ্যাত কবি ক্ষেমানন্দ নিজের নামের সঙ্গে কেতকাদাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর পুরো নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। মনসাদেবী সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; লৌকিক ভয়-ভীতি থেকেই তাঁর আবির্ভাব এবং সর্প-সংকুল পূর্ববঙ্গ যে দেবীর প্রধান পীঠস্থান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য সারা বাংলাদেশ জুড়ে, এমনকি বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও মনসার প্রভাব ও মনসামঙ্গলের আখ্যান প্রচলিত আছে। কোনো কোনো অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে তাঁকে শিবের মানস কন্যা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রাচীন পুরাণে মনসার বা শিবের কোনো মানস কন্যার উল্লেখ নেই। অবশ্য কোনো প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থেই যেন সর্পের দেবীর বেশি উল্লেখ আছে। 'বিনয়বস্তু ও 'সাধনমালা' নামে দু'খানি বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর স্পষ্ট বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা'য় দেবীকে 'জাঙ্গুলি' বা 'জাঙ্গুলিতারা' বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে সাপের রোঝাকে বলা হত 'জাঙ্গুলিক। প্রাচীন পুরাণ ও মহাভারতে যে সর্পের দেবীর উল্লেখ আছে, তিনি হচ্ছেন জরৎকারু, আস্তিক তাঁর ছেলে। বাংলার মঙ্গলকাব্যে জরৎকারু ও মনসাকে এক করে ফেলা হয়েছে। পদ্মপুরাণ, দেবী-ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার উল্লেখ আছে। বাংলাদেশেও দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে সর্পভূষণা মনসার প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। আদিবাসীদের মধ্যেও মনসাদেবীর পুজোপাসনা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ভারতে মঞ্চাম্মা' নাম্নী সর্গের দেবী ও বাংলার মনসার মধ্যে শব্দগত সাদৃশ্য আছে। এই সব তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে বিষনাশিনী সর্পের দেবী অজ্ঞাত ছিলেন না। মনসা নামটি কোনো কোনো অর্বাচীন পুরাণেও পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরাণে যেখানে মনসা নাম ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে তা পরবর্তিকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়। বাংলার মনসাদেবী আযেতর অস্ট্রিক সংস্কার থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন, পরে তাকে আর্যদেবমণ্ডলে স্থান দেবার জন্য পৌরাণিক কাহিনী, বিশেষত শিবের সঙ্গে মনসার পিতাপুত্রীর সম্পর্ক জড়িত করে কাব্যাদি রচিত হয়।
মনসামঙ্গল কাব্যেই দেবীর যথার্থ স্বরূপ ফুটে উঠেছে। সর্পের দেবী যে কিছু কোপনস্বভাব উগ্রমূর্তি হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? তাঁর পূজা প্রচারের জন্য মনসামঙ্গলে যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পদ্মবনে শিবের মন থেকে মনসার জন্ম হয়। তাই তিনি শিবের মানস- কন্যা। কোপনস্বভাব মনসার সঙ্গে বিমাতা চণ্ডীর কলহের ফলে তাঁর একটি চোখ কানা হয়ে যায়। তাই তিনি চাঁদসদাগরের দ্বারা গালিচ্ছলে 'কানী' বলে নিন্দিত হয়েছেন। মর্ত্যে কি করে তাঁর পূজা প্রচারিত হয়, এজন্য তিনি প্রথমে রাখাল প্রভৃতি নিম্নবর্ণের কাছ থেকে বলপূর্বক পূজা আদায় করলেন। কিন্তু তখন উচ্চতর সমাজে স্ত্রী-দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল না, সমাজে সম্পন্ন বলতে বণিকদের বোঝাত—সেই বণিকদের প্রধান চাঁদসদাগর ধর্মমতে ছিলেন শৈব। তিনি যদি মনসার পূজা করেন, তবে বণিক সমাজে সহজেই দেবীর প্রাধান্য স্থাপিত হবে। কিন্তু শিবের ভক্ত চাঁদসদাগর নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। দেবীর প্রচণ্ড আক্রোশ অবহেলা করেও তিনি শিবের পূজা করতে লাগলেন, দেবীকে অশিষ্ট ভাষায় গালি দিলেন, এমনকি তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করতেও পিছপা হলেন না। মনসার ক্রোধে চাঁদের ছটি পুত্র মরে গেল, তাঁর সর্বনাশ হল, ব্যবসা-বাণিজ্যে গিয়ে নৌকোডুবির ফলে তিনি নানা নির্যাতন ভোগ করে সর্বস্বান্ত হয়ে দেশে ফিরলেন। ইতিমধ্যে তাঁর একটি পুত্র হয়েছে। তার নাম লখীন্দর। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি তার সঙ্গে একটি সুলক্ষণা কন্যা বেহুলার বিয়ে দিলেন। পাছে মনসা তাঁর এই পুত্রটিকেও বিনাশ করেন এই আশঙ্কায় তিনি সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে পুত্র-পুত্রবধূকে বাসরযাপন করতে পাঠালেন। কিন্তু দেবতার সঙ্গে মানুষের বিরোধে মানুষ কি জয়ী হয়ে পারে? লোহার বাসরের একস্থানে একটি সূচীভেদ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র ছিল। মনসা তা জানতেন। বাসরে লখীন্দর ও বেহুলা ঘুমিয়ে পড়লে দেবী তাঁর অনুচর কালনাগকে পাঠিয়ে দিলেন। বিষধর কালনাগের দংশনে বাসরেই লখীন্দরের মৃত্যু হল। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল, মা সনকা তারস্বরে কাঁদতে লাগলেন, অনেকে নতুন বউকে অলক্ষুণে মনে করে বেহুলার নিন্দায় জ্বলে উঠল। কিন্তু জেদী চাঁদের চোখের জল মহাক্রোধে আগুন হয়ে জ্বলতে লাগল। 'কানী'র উচ্ছিষ্ট পুত্রকে ঘরে রেখে কি হবে? কলার ভেলায় করে লখীন্দরের শবদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ হতে লাগল। তখন সতীশিরোমণি বেহুলা ঐ ভেলায় স্বামীর শবের পাশে ঠাঁই করে নিল। তার পণ—সে স্বর্গে গিয়ে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবে, তা নইলে আর ফিরে আসবে না।
জলপথে বেহুলাকে নানা বিপদে পড়তে হল, মনসার ক্রোধও তাকে অনুসরণ করতে লাগল। নানা প্রলোভন জয় করে অসাধারণ সতীধর্মের জোরে বেহুলা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছল, তারপর দেবতাদের নৃত্যগীতে তুষ্ট করে স্বামীর জীবনভিক্ষা চাইল। শিবের নির্দেশে অনিচ্ছার সঙ্গে মনসা লখীন্দরের জীবন ফিরিয়ে দিয়ে সম্মত হলেন। তবে তিনিও বেহুলাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, বেহুলা ফিরে গিয়ে শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পূজা করিয়ে নেবে। কারণ চাঁদসদাগর দেবীর পূজা না করলে মর্ত্যে উচ্চবর্ণের মধ্যে মনসার পূজা প্রচারিত হবার সম্ভাবনা ছিল না। বেহুলা তাতেই সম্মত হল। তার স্বামী লখীন্দর বেঁচে উঠল, ছয় ভাশুর প্রাণ ফিরে পেল, শ্বশুরের নিমজ্জিত বাণিজ্যের নৌকাও ভেসে উঠল। জয়ধ্বনিসহ সে স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি হাজির হল। চাঁদের পরিবারে চাঁদের হাট বসল। প্রথমটা চাঁদসদাগর মনসার পূজা ব্যাপারে বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু মনসার রক্তচক্ষুকে অবহেলা করলেও তিনি পুত্রবধূ বেহুলার অশ্রুকাতর মিনতি এড়াতে পারলেন না মনসার পূজায় কোনও প্রকারে রাজি হয়ে গেলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্নেহের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলেও, তিনি খুব যে একটা ভক্তির সঙ্গে মনসার পূজা করেছিলেন, তা মনে হয় না। তিনি ডান হাত দিয়ে দেবীর পূজা করতে কিছুতেই রাজি হলেন না। ও-হাতে তিনি মহাদেবের পূজা করেন, ওর দ্বারা তিনি স্ত্রী-দেবতার পূজা কি করে করবেন? তাই বাম হাত দিয়ে দেবীর উদ্দেশে ফুল ফেলে দিলেন। অবশ্য তাতেই দেবীকে খুশি হতে হল—কারণ এর ফলে তিনি উচ্চ সমাজে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন। বেহুলা-লখীন্দরের দ্বারা দেবীর পূজা মর্ত্যধামে প্রচার লাভ করল। কিন্তু আসলে বেহুলা লখীন্দর স্বর্গের দেবদেবী — ঊষা ও অনিরুদ্ধ। দেবীর অভিশাপে মর্ত্যজন্ম গ্রহণ করে তারা মনসার পূজা প্রচারে সাহায্য করল, তারপর শাপের অবসানে স্বর্গের দেবদেবী স্বর্গে ফিরে গেল। এই হল মনসামঙ্গলের কাহিনীর সূত্র।
বাংলার নানা অঞ্চলে এবং বাংলার বাইরে এ কাহিনীর অল্প-স্বল্প বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ- ভারতের লোকসাহিত্যেও মনসামঙ্গলের অনুরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বিহারে মনসামঙ্গলের যে আখ্যান হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে, তাও অনেকটা বাংলার মতো,—বোধ হয় বাংলার প্রভাবেই পরিকল্পিত। বাংলায় মনসামঙ্গলের তিনটি ধারা দেখা যায়।
- ১. রাঢ়ের ধারা (বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সীতারামদাস, রসিক মিশ্র প্রভৃতি কবি),
- ২. পূর্ববঙ্গের ধারা, প্রায়শই যা পদ্মাপুরাণ নামে পরিচিত (নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি),
- ৩. উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা (তন্ত্র-বিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রভৃতি)।
কাহিনীর দিক থেকে উত্তরবঙ্গের ধারা একটু পৃথক ধরনের। এতে ধর্মমঙ্গলের বেশ প্রভাব আছে।
কেউ কেউ মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ ও ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য বেহুলার অপূর্ব সতীধর্ম এবং চাঁদসদাগরের অনমনীয় পৌরুষ মহাকাব্যেরই উপযুক্ত। কিন্তু এই বিষয়বস্তুকে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালির গ্রাম্য স্তর থেকে মহাকাব্যের রসে উন্নীত করার মতো মহাকবির প্রতিভা মনসামঙ্গলের কোনো কবিরই ছিল না- কোনো মঙ্গলকাব্যেই মহাকাব্যের লক্ষণ বড়ো একটা পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গলের কাহিনীটি ঐতিহাসিক কি না সে
বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাংলার প্রায় গ্রামেই চাঁদসদাগরের ভিটে ও বেহুলার ঘাট আছে। সুতরাং এ রকম লোককাহিনীর পশ্চাতে কোনো সুদূর যুগের কোনো ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচ্ছন্ন থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এখন আর তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।
আমরা পূর্বেই বলেছি যে, প্রথম দিকে (চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে) মঙ্গলকাব্যের কাহিনী স্ত্রী-সমাজে ব্রতকথা ও ছড়ার মধ্যে বেঁচে ছিল। পরে পঞ্চদশ শতকের দিকে বাংলা সাহিত্যের গঠনের যুগে এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর মহিমাবিষয়ক ব্রতকথাটি দীর্ঘবিস্তারী আখ্যানকাব্যের আকার লাভ করল। আমাদের অনুমান বাংলাদেশে মনসামঙ্গলের রচনা সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়— পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে, তখন মনসামঙ্গলের কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয়েছিল। তারা হলেন বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদের ও বিপ্রদাস পিপলাই। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন পূর্ব- বঙ্গের কবি, তৃতীয় জন হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের কবি। কিন্তু কারও কারও মতে মনসামঙ্গল ধারার আদিকবি হলেন কানা হরিদত্ত। বিজয়গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণের প্রারম্ভে মনসামঙ্গলের আদিকবি কানা হরিদত্তের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, মনসামঙ্গলের প্রথম গীতিকার কানা হরিদত্ত। কানা হরিদত্তের বিচারবুদ্ধি সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁর ত্রুটিপূর্ণ পাঁচালি দেবীর মনঃপূত হয়নি। তিনি তখন বিজয়গুপ্তকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বিশুদ্ধতর কাব্য লিখতে নির্দেশ দিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'পদ্মার সর্পসজ্জা' শীর্ষক কয়েকটি ছত্রকে কানা হরিদত্তের রচনা বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ ভাষা আদৌ পুরাতন নয় বলে আমরা এই রচনাকারকে প্রাচীন কবি বলে গ্রহণ করতে রাজি নই। অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে হরিদত্ত নামে মনসামঙ্গলের একাধিক কবি জন্মগ্রহণ করেন। দীনেশচন্দ্র উল্লিখিত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' সেই ধরনের কোনো আধুনিক হরিদত্তের রচনা। তবে বিজয়গুপ্তের কাব্যের উল্লেখ থেকে মনে হচ্ছে হরিদত্ত নামে কোনো কবি তাঁর আগে পাঁচালি ধরনের কোনো রচনায় মনসামঙ্গলের কাহিনী বিবৃত করেছিলেন। কিন্তু এঁর বিষয়ে শুধু বিজয়গুপ্তের উল্লেখ ভিন্ন আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এবার আমরা পঞ্চদশ শতকের কয়েকজন প্রধান কবির কথা বলি।
বিজয়গুপ্ত ॥ বরিশাল জেলার আধুনিক গৈলা গ্রামে (প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী) বিজয়গুপ্তের জন্ম হয়। তাঁর আবির্ভাবের সন-তারিখ সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাঁর কোনো কোনো পুঁথিতে পুঁথিসমাপ্তির শকাব্দের উল্লেখ আছে বটে। তাই থেকে মনে হয় কবি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সনাতন, জননী রুক্মিণী—এর বেশি কোনো পরিচয় কবি দেননি। শোনা যায়, তিনি নাকি স্বগ্রামে মনসার মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এখনও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বরিশাল থেকে বাংলা ১৩০৩ সালে সর্বপ্রথম বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তারপর এর একাধিক পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। অবশ্য মুদ্রিত গ্রন্থের ভাষা বিশেষ প্রাচীন নয়, এর মধ্যে বিজয়গুপ্তের ভণিতার সঙ্গে আরও অনেকের ভণিতা আছে। সুতরাং কোনো কোনো সমালোচক বিজয়গুপ্তের প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে এ সন্দেহ অমূলক। কারণ বিজয়গুপ্তের পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। আমরা মুদ্রিত কাব্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখেছি, ছাপাগ্রন্থের অনেক জায়গায় কলম চালানো হয়েছে। সুতরাং বিজয়গুপ্তের পুঁথি খুব বিশুদ্ধ ও প্রাচীন তা মনে হয় না। এর ভাষা অনেক স্থলে আধুনিক কালের মতো, কোথাও কোথাও পশ্চিমবঙ্গীয় বাগধারার প্রভাবও আছে। মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও পূর্ববঙ্গের বিজয়গুপ্তের কাব্যের সমধিক সমাদর হয়েছিল। এই দু'খানা কাব্য মনসামঙ্গলের কাব্যের মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রণের গৌরব লাভ করে। অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য বিজয় গুপ্তের ভাষার নানা পরিবর্তন হয়েছে। তাই বলে তাঁর কাব্যকে অপ্রামাণিক বলে তাচ্ছিল্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। কোন্ মধ্যযুগীয় কাব্যেই বা হস্তক্ষেপ হয়নি? কৃত্তিবাসি রামায়ণ ও চণ্ডীদাসের পদাবলী তার উৎকট দৃষ্টান্ত। কৃত্তিবাসি রামায়ণে বহু পরিবর্তন হয়েছে বলে কি তাঁর কাব্যকে আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে বহিষ্কৃত করতে পারি? বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে আমরা একই যুক্তি পেশ করতে চাই।
বিজয়গুপ্তের পুঁথির সংখ্যা খুব বেশি নয়। যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে, তার কয়েকখানিতে কাব্যরচনার শকাব্দের উল্লেখ আছে হেঁয়ালির ভঙ্গিতে, এবং হেঁয়ালির ভাষাও সব পুঁথিতে এক নয়। সেই হেঁয়ালির মর্মোদ্ঘাটন করলে এই খ্রীস্টাব্দগুলি পাওয়া যাবে—–১৪৯৪, ১৪৭৮, ১৪৮৪ অব্দ। তাঁর কাব্যের একস্থলে সুলতান হুসেন শাহের উল্লেখ আছে। ১৪৭৮ বা ১৪৮৪ খ্রীঃ অব্দে বাংলার সিংহাসনে হুসেন শাহকে পাই না। তিনি ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। তাই মনে হয় বিজয়গুপ্তের কাব্য হুসেন শাহের সিংহাসন লাভের পর রচিত হয়—১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দে হলেও হতে পারে।
বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে অনেকে খুব প্রশংসাসূচক বাক্য ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্যলক্ষণের বিচারে তাঁর কাব্য বিশেষ প্রশংসা পাবে না। মনসার ঈর্ষাকুটিল বিষাক্ত চরিত্রটি মোটামুটি মন্দ হয়নি। শিবের হাস্যকর ভাঁড়ামি ধূলিধূসর মঙ্গলকাব্যের আদর্শকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চাঁদসদাগরের চরিত্রে প্রচণ্ড পৌরুষের সঙ্গে স্থূলতার সমাবেশে এর মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে বেহুলার চরিত্রাঙ্কনে কবি সমস্ত মাধুর্য ও পবিত্রতা ঢেলে দিয়েছেন। স্থুল রঙ্গরসে বৈদ্য- কবির বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, তা স্বীকার করতে হবে। সে যাই হোক, কাব্যটি যতটা জনপ্রিয় হয়েছে ততটা কাব্যগুণের অধিকারী নয়।
বিপ্রদাস পিল্লাই৷ প্রায় সমসাময়িক কবি বিপ্রদাস পিপ্লাই যে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তার নাম 'মনসাবিজয়'। এই কবি সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্বেও অনেকে কিছু জানতেন না। এঁর খান চারেক পুঁথি পাওয়া গেছে, তাই থেকে এঁর কাব্যের পরিচয় উদ্ধার করা হয়েছে। অবশ্য একখানি বাদে আর সমস্ত পুঁথি এত গোলমালে ভরা যে, কবির যথার্থ কাব্যরূপ নির্ধারণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে।
বিপ্রদাস বসিরহাটের নিকট (চব্বিশ পরগণা) বাদুড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুঁথিগুলিও কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি যে পশ্চিবঙ্গের কবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্যের প্রারম্ভে কবি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে নাদুড়া বটগ্রাম, মতান্তরে বাদুড়িয়া গ্রামে পিল্লাই শাখা-ভুক্ত ব্রাহ্মণবংশে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবি ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দে কার্য সমাপ্ত করেন, পুঁথিতে যে সন শকাব্দের উল্লেখ আছে, তা থেকেই এই খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু পুঁথির ভাষা প্রাচীন। নয়, কোনো কোনো স্থানে উৎকট আধুনিক বাক্যবিন্যাসও আছে। বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপিত হলে বিপ্রদাস সম্বন্ধে ও অনুরূপ সংশয় অনায়াসেই উঠতে পারে। বিশেষত এ কাব্যে এমন কতকগুলি আধুনিক স্থানের উল্লেখ আছে যে, এর প্রাচীনত্বের কিছু সংশয় জন্মায়। কবি যেভাবে কলকাতা ও খড়দহের উল্লেখ করেছেন, তাতে তাঁকে উত্তর-চৈতন্যযুগের কবি বলে মনে হয়। তবে এই উল্লেখ প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। প্রাপ্ত পুঁথিগুলির পাঠেও বিভ্রান্তি অপনোদিত হতে চায় না। সুতরাং তাঁর পুঁথিগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ আছে।
কবি প্রাচীন হলেও ইদানীং তাঁর পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কিছুকাল পূর্বে কবি ছাপার অক্ষরে উঠেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। কাহিনী ও চরিত্র- চিত্রণে বিপ্রদাসের কৃতিত্ব বিজয়গুপ্তের চেয়ে বেশি তা স্বীকার করতে হবে। বিশেষত হাসান- হুসেন পালায় তিনি যেভাবে মুসলমান সমাজের বর্ণনা করেছেন, তাতে মুকুন্দরামকে ছেড়ে দিলে এই সম্বন্ধে তার সমান বিচক্ষণ কবি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে কবি কিঞ্চিৎ কৌতুকরসেরও আমদানি করেছেন—যদিও কবি বড়ো গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর কাব্যে বিজয়গুপ্তের মতো হাস্যতরল বর্ণনা নেই বললেই চলে। বেহুলা, সনকা, চাঁদ সদাগরের চরিত্রগুলি মন্দ হয়নি, কিন্তু কবির বক্তব্য চারুত্ববর্জিত — নিতান্তই সাদাসিধে ধরনের। চাঁদের বাণিজ্য প্রসঙ্গে কবি যে পথঘাটের উল্লেখ করেছেন, পূর্ববঙ্গীয় কবির চেয়ে সে বর্ণনা অধিকতর বাস্তবনিষ্ঠ হয়েছে———কারণ তিনি ছিলেন স্থানীয় কবি। তাঁর এই পথের বর্ণনায় ভাটপাড়া, মূলাজোড়, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, রিসড়া, খড়দহ, কামারহাটী এঁড়েদহ, ঘুসুড়ি, চিতপুর, বেতড় ও কলকাতার উল্লেখ আছে—এবং উল্লেখ আছে বলেই এ-কাব্যের প্রাচীনতায় ও প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দেহ জন্মে। সে যাই হোক, সহজ বর্ণনায় বিপ্রদাসের মনসাবিজয় নিতান্ত মন্দ হয়নি, মনসার চরিত্রের রুক্ষ নির্মমতাও অনেকটা অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কবিকে অতি প্রশংসার বিশ্বদলে পূজা করবারও প্রয়োজন দেখি না। সর্বোপরি কবির পুঁথির পাঠ সম্বন্ধে নানা গণ্ডগোল আছে বলে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলা যায় না।
নারায়ণদেব। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে নারায়ণদেব বিশেষ স্থান দাবি করতে পারেন। একমাত্র তার কাব্যই বাংলা ও অসমে প্রচার লাভ করেছে। তার পুরা ভণিতা সুকবিবল্লভ নারায়ণদেব। অনেকে মনে করেন সুকবিবল্লভ ও নারায়ণদেব দু'জন পৃথক কবি। কিন্তু এ অনুমান যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। তাঁর পদ্মাপুরাণের ভণিতা থেকে সুকবিবল্লভ' বা 'কবিবল্লভ' খেতাব বলে মনে হচ্ছে। ইনি যে একজন অতি প্রাচীন কবি, তার প্রমাণ ১৬৯৫ খ্রীঃ অব্দে নকল করা তাঁর একখানি পুঁথি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। তাঁর এ-কাব্যের আরও অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে। কাজেই কবি একদা ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টে অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পুঁথিতে সংক্ষেপে যে আত্মপরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস রাঢ়ভূমি। তাঁরা দেব-উপাধিক কায়স্থ। তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধারণদেব রাঢ়দেশ ছেড়ে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত বোরগ্রাম এখন ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত হলেও একদা নাকি এই গ্রাম শ্রীহট্টের মধ্যে ছিল। শ্রীহট্টে তাঁর কাব্য বেশ প্রচারিত আছে, এখনও ছাপা হয়। ‘সুকবিবল্লভ’ নারায়ণ ভণিতাটি শ্রীহট্টীয় উপভাষায় 'সুকনান্নি'তে পরিণত হয়েছে। এখন শ্রীহট্টে সুকনান্নির যে পদ্মাপুরাণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ময়মনসিংহের নারায়ণদেবের কাব্যের সামান্য স্থানীয় উপভাষা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তাই অনুমান হয় শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহের বোরগ্রামের ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য নারায়ণদেবের কাব্য শ্রীহট্টেও বেশ প্রচার লাভ করেছিল এবং সেইজন্য শ্রীহট্টীয়েরা কবিকে নিজেদের অঞ্চলের কবি বলে দাবি করেছেন—যদিও সে দাবি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়। নারায়ণদেবের সময় সম্বন্ধে কোনো সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর কোনো পুঁথিতে কালানির্ণয়-সংক্রান্ত কোনো ইঙ্গিত নেই। অবশ্য বাংলাদেশ বিভক্ত হবার আগে ঐ গ্রামে তাঁর বংশধারা বর্তমান ছিল। তাঁদের কাছে রক্ষিত বংশতালিকা থেকে অনুমান হয় কবি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি বর্তমান ছিলেন। তা হলে তাঁর কাব্য বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাসের সমকালেরই হতে পারে। তবে এ-ও আমাদের অনুমান মাত্র। কবি হুসেন শাহের সময়ে কাব্য রচনা করলে প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতানের নাম উল্লেখ করতে ভুলতেন না, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস দু'জনেই সুলতানের নাম করেছেন। কেউ কেউ তাকে বিপ্রদাসের পরবর্তী বলতে চান। আমরা এ অনুমানও সমর্থন করি না। কারণ বিপ্রদাসের ভাষার চেয়ে তাঁর ভাষায় প্রাচীনত্বের অধিকতর লক্ষণ আছে—যদিও তাঁর কাব্য বহুবার নকল হয়েছে। বেশি জনপ্রিয় বা নকল হলে কাব্যের ভাষা বদলে গিয়ে যুগোপযোগী রূপ ধারণ করে। নারায়ণদেবের ভাষা কিন্তু সেই দিক দিয়ে অনেকটা প্রাচীন।
নারায়ণদেব যে একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন, তা তাঁর বিরাট পুঁথি থেকেই বোঝা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক দিন আগে তাঁর যে কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে পালাবিন্যাসে নানা গণ্ডগোল আছে; সেই গ্রন্থ থেকে কবি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। নারায়ণদেব লৌকিক মঙ্গলকাব্য ফাঁদলেও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তার নানা প্রমাণ সমগ্র কাব্যের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। তিনি একটু পুরাণ-ঘেঁষা কবি ছিলেন, লৌকিক মনসাকাহিনীর চেয়ে পৌরাণিক দেবদেবীর লীলার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাভারত, শৈব পুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত উপাদান থেকে তাঁর দেবখণ্ডের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। হরপার্বতী লীলায় বহুস্থলে কুমারসম্ভবের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে। রঙ্গব্যঙ্গ ও করুণরসে তাঁর সমান অধিকার বিস্ময়কর, বিশেষত ব্যঙ্গের তির্যকতা তাঁর কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। বণিক সম্বন্ধে তাঁর ব্যঙ্গোক্তি চমৎকার :
কাক হস্তে সেয়ানা জে বানিয়া ছাওয়াল।
বানিআ হস্তে ধুত্ত যেই তারে দেই পানি ।
স্বামীর মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে বেহুলার বিলাপ খুবই মর্মস্পর্শী
জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে ।
প্রভু রে তুমি আমি দুই জন।
জানে তব সর্বজন ।
তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।
চরিত্রসৃষ্টি, রসবৈচিত্র্য ও কাহিনী গ্রন্থনে নারায়ণদেব বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর স্থান বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের চেয়ে অনেক উঁচুতে। কেউ কেউ তাঁর কাব্যের বিস্তার, করুণ রস ও চরিত্র-চিত্রণ স্মরণ করে তাঁকে মহাকবি আখ্যা দিতে চান, এ -সব অতিভক্তির বাড়াবাড়ি। মধ্যযুগে একজনও মহাকবি জন্মাননি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছাড়া বাংলাদেশে, কী মধ্যযুগ, আর কী আধুনিক যুগ—দ্বিতীয় কোনো মহাকবির আবির্ভাব হয়নি। এখানে মধ্যযুগের আদিপর্ব অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্যযুগের আলোচনা শেষ হল। এই সামান্য পরিচয় থেকে নিশ্চয় বোঝা যাবে, এই যুগে বাংলা সাহিত্যের শুরু হয়েছে, কিন্তু তখনও পুরো উৎকর্ষ লাভ হয়নি। পঞ্চদশ শতকের শেষপ্রান্তে চৈতন্যাবির্ভাবের পর থেকে তাঁর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের যে অভুতপূর্ব উন্নতি হল, পরের পর্বে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব।



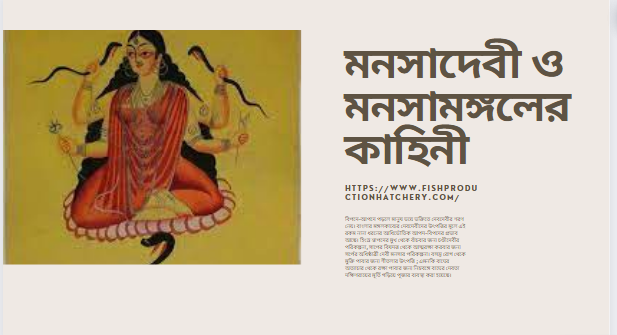
.jpg)
.png)