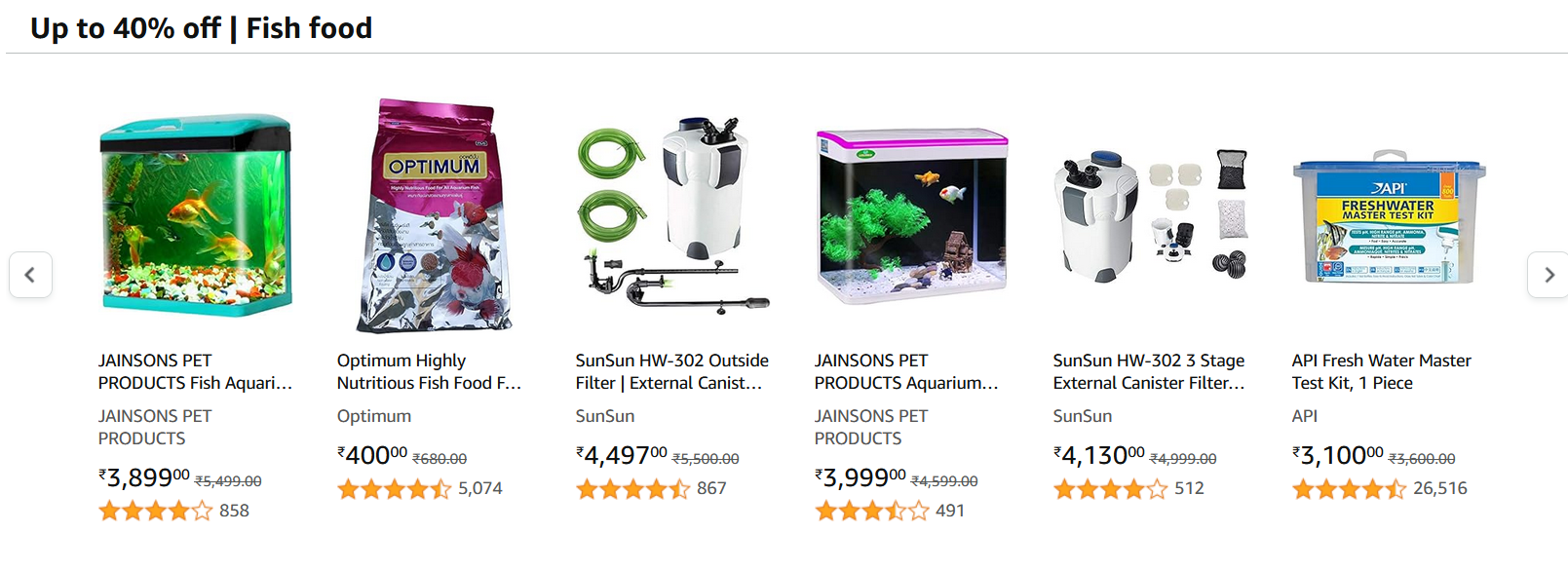অভিযোজন
অভিযোজন কাকে বলে ? [What is ADAPTATION in Bengali ]
সূচনা (Introduction) :
প্রত্যেক জীব সবসময়েই চেষ্টা করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নিতে—সেই পরিবেশ থেকে নানান রকমের সুবিধা পেতে। পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যেও নিজেকে ঠিকমতো মানিয়ে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকা এবং বংশবৃদ্ধি করার জন্য জীবের নানান রকমের পরিবর্তন ঘটে; — এই পরিবর্তন গঠনগত হতে পারে, শারীরবৃত্তীয় হতে পারে কিংবা আচরণগতও হতে পারে। এর ফলে জীব যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তা পরের প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয়। এভাবে প্রত্যেক প্রজন্মে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে একসময় সরল জীব থেকে নতুন জটিল এক জীবের উদ্ভব ঘটে, অর্থাৎ জৈব বিবর্তন ঘটে। যে সমস্ত পরিবর্তন জৈব বিবর্তনে সাহায্য করে তাদেরকেই বলা হয় অভিযোজন।
অভিযোজনের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা (Definition and Explanation of Adaptation)
অভিযোজনের সংজ্ঞা:
পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য জীবদেহের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত যে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে (যা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে জৈব অভিব্যক্তির পথকে সুগম করে), তাকেই অভিযোজন বা অ্যাডাপটেশন বলে।
বিভিন্ন জীব বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে। ওই পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলার জন্য জীবের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। যেমন মাছ জলে বাস করার জন্য তার দেহটি মাকু আকৃতির হয়েছে। জলে সাঁতার কাটার জন্য পাখনা এবং শ্বাসকার্য চালানোর জন্য ফুলকা সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য জীবদেহের যেসব বৈশিষ্ট্যের অবির্ভাব ঘটে এবং জীবদেহের গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাদের অভিযোজন বলে।
অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য (Importance & Purpose of Adaptation):
অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা : অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেহেতু পরিবেশ নিয়ত পরিবর্তনশীল, সেহেতু কোনও পরিবেশে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেখানকার জীবদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, নতুবা তাদের অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এই কারণেই পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সেখানকার জীবদের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত অর্থাৎ অভিযোজিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়।
অভিযোজনের উদ্দেশ্য : অভিযোজনের প্রধান উদ্দেশ্য হল :
1. পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে জীবনধারণ ও বংশবিস্তার করাই হল অভিযোজনের প্রধান উদ্দেশ্য।
2. পরিবর্তিত পরিবেশে গঠনগত, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকাই হল অভিযোজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।
3. পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামস্য রেখে নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে আপন প্রজাতির
অস্তিত্বরক্ষা হল অভিযোজনের আর একটি উদ্দেশ্য।
4. অভিযোজনের
ফল হিসেবে জীবদেহে যে অনুকূল পরিবর্তন আসে তা বংশপরম্পরায় উত্তর পুরুষের দেহে
সঞ্চারিত হয়ে বিবর্তনের পথকে সুগম করে।
অল্পকথায়, পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ
খাওয়াবার অবিরাম প্রচেষ্টাই হল অভিযোজনের মূলসূত্র।
অভিযোজন ও অভিব্যক্তির সম্পর্ক (Relation between Adaptation and Evolution):
অভিযোজনের সঙ্গে বিবর্তনের সম্পর্ক নিম্নলিখিত তিনটি উক্তিতে প্রকাশ করা যায়।
1. পরিবর্তিত পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার মাধ্যমে জীবদের বিবর্তন ঘটে :
প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য নির্দিষ্ট পরিবেশে
বসবাসকারী জীবদের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা থাকে। কেননা, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে
অভিযোজিত হতে না পারলে তাদের অবলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কোনও প্রজাতির
অন্তর্ভুক্ত সব সদস্যের পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা
সফল হয় না। দেখা গেছে, এই ধরনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ জেনেটিক গঠন- বিশিষ্ট
সদস্যের প্রচেষ্টা অন্যান্যদের তুলনায় সফল হয়। যাদের ক্ষেত্রে এই সাফল্য ঘটে,
তারা পরিবর্তিত পরিবেশে স্থায়ী আসন লাভ করে এবং অন্যান্যরা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত
হয়ে যায়। পরিবর্তিত পরিবেশে এইভাবে ধারাবাহিক অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে জৈব
বিবর্তন ঘটে। অভিযোজনগত এইসব বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই নতুন
নতুন প্রজাতির জীবের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে, অভিযোজন ও অভিব্যক্তি
পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।
2. বিবর্তনের পথে কোনও বৈশিষ্ট্যের একবার অবলুপ্তি ঘটলে তার পুনরাবির্ভাব
ঘটে না :
একথা আমরা জানি যে সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেছে মাছের
মত জলচর পূর্বপুরুষ থেকে। শ্বাসযন্ত্র বা ফুলকা ত্যাগ করে তার পরিবর্তে
স্থলবাসী প্রাণীরা ফুসফুস অর্জন করেছে। কোনও কোনও স্থলবাসী প্রাণী, যেমন :
তিমি, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি নানা কারণে আবার জলের জীবনে ফিরে গেছে, কিন্তু জলে
শ্বাসকার্য চালানোর জন্য ফুলকা তারা আর ফিরে পায়নি।
3. কোনও প্রজাতি নির্দিষ্ট পরিবেশে একবার পরিপূর্ণরূপে অভিযোজিত হওয়ার পর
তার পুনরায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। যেমন : প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে বিলুপ্ত লাং ফিস - সেরাটোডাস যে ধরনের
বসতিতে বাস করতো, তার বর্তমান বংশধর অস্ট্রেলিয়াবাসী ‘নিওসেরাটোডাস' প্রায়
একই ধরনের বসতিতে বাস করে। ফলে উভয়ের মধ্যে গঠনগত পরিবর্তন বিশেষ কিছু
ঘটেনি।
• উপরোক্ত তিনটি আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অভিযোজনের
মাধ্যমেই জীবের বিবর্তন ঘটে।
উদ্ভিদের অভিযোজন
[ADAPTATION OF PLANTS]
পদ্ম, ক্যাকটাস ও সুন্দরী গাছের অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করা হল :
পদ্মের অভিযোজন (Adaptation of Lotus ) :
পদ্মের কাণ্ড ও মূল জলের নীচে কাদায় গাঁথা থাকে, কিন্তু পাতা, ফুল ও ফল
ইত্যাদি জলের উপর থাকে, তাই পদ্মকে আংশিক নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। জলে বাস
করার জন্য পদ্মের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

|
| Adaptation of Lotus |
2. কাণ্ড : (i) পদ্মের কাণ্ড গ্রন্থিকাণ্ড অর্থাৎ রাইজোম জাতীয়। (ii) কাণ্ডটি জলের নীচে কাদার মধ্যে অনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায়। (iii) কাণ্ডের ত্বক কিউটিকলবিহীন, ত্বকে মোম জাতীয় আবরণ এবং রোম থাকে না। (iv) কান্ড স্পঞ্জের মতো নরম এবং কাণ্ডের মধ্যে অনেক বাতাবকাশ থাকে। (v) যান্ত্রিক কলা থাকে না বা থাকলেও সুগঠিত নয়। (vi) কাণ্ডের সংবহন কলা সুগঠিত নয়।
3.পাতা
পত্রবৃত্ত : (i) পদ্মের
পত্রবৃন্ত এবং পুষ্পবৃত্তগুলি বেশ দীর্ঘ, বৃত্তের বহির্দেশ সূক্ষ্ম কাঁটা দিয়ে
ঢাকা থাকে। জলজ প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এমন অভিযোজন; (ii)
বৃত্তের মধ্যে প্রচুর বাতাবকাশ থাকে। বাতাবকাশগুলিতে অক্সিজেন এবং কার্বন
ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে। শ্বসন এবং সালোকসংশ্লেষের সময় গাছ ওই গ্যাস ব্যবহার
করে; (iii) বৃত্তের ত্বক কিউটিকল্বিহীন; (iv) বৃত্তের সংবহন কলা অনুন্নত এবং
যান্ত্রিক কলার পরিমাণ কম।
• পত্র ফলক : (i) পদ্মের
পাতাগুলি প্রথম অবস্থায় জলের ওপরে ভেসে থাকে, কিন্তু পরিণত অবস্থায় পাতাগুলো
জলের কিছু ওপরে বাঁকাভাবে অবস্থান করে। (ii) পাতার ফলকগুলি আকারে বেশ বড় এবং
গোলাকার। (iii) ফলকের ওপরের তল মসৃণ এবং মোমজাতীয় আবরণ দ্বারা আবৃত। (iv)
পাতার ত্বকে কিউটিকল আছে। পত্ররন্ধ্র কেবল ঊর্ধ্বত্বকে অবস্থিত। (v) পাতার
সংবহন কলা সুগঠিত, যান্ত্রিক কলা অনুপস্থিত।
4. ফুল : (i)
পদ্মের ফুলগুলি পতঙ্গ পরাগী। (ii) ফুলগুলি বেশ বড় এবং উজ্জ্বল বর্ণের (iii)
পুষ্পাক্ষ স্পঞ্জের মতো এবং বাতাবকাশযুক্ত; (iv) স্ত্রীস্তবক শাঙ্কবাকার; (v)
পুংকেশরের সংখ্যা অসংখ্য।
5. বীজ : (i) পদ্মের বীজত্বক খুব
শক্ত এবং অভেদ্য। (ii) পদ্মবীজের বহুদিন পর্যন্ত (কয়েক বছর থেকে কয়েক শ' বছর)
অঙ্কুরোদাম শক্তি রক্ষা করার ক্ষমতা আছে।
6. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : (i) পদ্মগাছের বেশিরভাগ অংশ জলে নিমজ্জিত থাকায় এদের বাষ্পমোচনের হার খুব কম; (ii) পদ্ম অঙ্গজ জননের দ্বারা বংশবিস্তার করে; (iii) পদ্মের সারা দেহ দিয়েই জলশোষণের ক্ষমতা আছে।
ক্যাকটাস-এর অভিযোজন (Adaptation of Cactus)
ফণীমনসা, তেসিরা, মনসা ইত্যাদি ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ। ক্যাকটাস অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক ও বালুকাময় স্থানে জন্মায়। এইরকম পরিবেশে বাস করার জন্য এদের জাঙ্গল উদ্ভিদ (Xerophyte) বলে। ক্যাকটাসের উল্লেখযোগ্য অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল

|
| ক্যাকটাস জাতীয় |
1. মূল : (i) ক্যাকটাসের মূলতন্ত্র সুগঠিত। মূলের বৃদ্ধির হার অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায় খুব বেশি। মূল মাটির নীচে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। জল সংগ্রহের জন্য মূলগুলি সুদীর্ঘ হয়। (ii) মূলে মূলরোম এবং মূলত্রাণ থাকে।
2. কাণ্ড: (i) কাণ্ড সাধারণত খর্বাকার, কাষ্ঠল এবং পুরু বাকল বা মোমজাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। (ii) ফণিমনসার কাণ্ড রসাল, সবুজ এবং চ্যাপ্টা পাতার মতো। এরকম কাণ্ডকে পর্ণকাণ্ড বলে। পর্ণকাণ্ডে অনেক পর্ব এবং পর্বমধ্য থাকে। কাণ্ডে জল সঞ্চিত থাকে। (iii) কাণ্ডের ত্বকে পুরু কিউটিকল্ থাকে। অনেকক্ষেত্রে রোম বা মোমের আবরণ থাকে। বাষ্পমোচন রোধের জন্য এই রকম অভিযোজন।
3. পাতাঃ (i) ক্যাক্টাসের পাতা আকারে ছোটো এবং সংখ্যায় কম থাকে। (ii) ফণিমনসা গাছের পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। (iii) অন্যান্য ক্যাকটাসের পাতার ত্বক খুব পুরু এবং কিউটিকল্যুক্ত। বাষ্পমোচন রোধ করার জন্য পাতাগুলি অনেক সময় মোম জাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। (iv) পাতায় পত্ররন্ধ্র খুব কম সংখ্যায় থাকে। পত্ররন্দ্রগুলি পাতার নিম্নত্বকের ভিতরের দিকে উৎপন্ন হয়। পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ দুটো আকারে খুব ছোটো হয়।
সুন্দরী গাছের অভিযোজন (Adaptation of Sundari) :
সুন্দরী একরকমের লম্বণাম্বু (Halophyte) উদ্ভিদ। এরা সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকার কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত মাটিতে জন্মায়। এর অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

|
সুন্দরী গাছের অভিযোজন |
1. মূল : (i) মাটি লবণাক্ত থাকায় মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করে না, মূল মাটির অল্প নীচে বিস্তৃত থাকে। (ii) মাটি কর্দমাক্ত ও রন্ধ্রবিহিন হওয়ায় ওই মাটিতে অক্সিজেন সরবরাহ খুব কম। তাছাড়া এসব এলাকা বেশিরভাগ সময়ই জলপ্লাবিত থাকে। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে অজৈব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাই উদ্ভিদের কিছু শাখা-মূল অভিকর্ষের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়ে মাটির ওপরে উঠে আসে। এইসব মূলের উপরিভাগে অসংখ্য সূক্ষ্ম শ্বাস ছিদ্র বা 'নিউম্যাটোফোর’থাকে, এই ছিদ্রের মাধ্যমে মূলগুলি বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন শোষণ করে। এই রকম মূলকে শ্বাসমূল বলে। (iii) গাছগুলি নরম ও কর্দমাক্ত মাটিতে জন্মানোর ফলে, যাতে গাছগুলো সহজে না পড়ে যায়, তার জন্য কাণ্ডের গোড়ার দিক থেকে এক রকমের অস্থানিক মূল বেরিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে—এই মূলগুলিকে ঠেস মূল বলে। (iv) সুন্দরী গাছের গুঁড়ির নীচের দিকের চারপাশ থেকে কতকগুলি চ্যাপ্টা এবং তক্তার মতো অংশ বের হয়ে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। তক্তার মতো এই অংশগুলিকে অধিমূল বলে। অধিমূল সুন্দরীর গুঁড়িকে খাড়াভাবে থাকতে সাহায্য করে।
2. কাণ্ড : (i) সুন্দরী গাছ খর্বাকার এবং গম্বুজাকার, কাণ্ড সাধারণত দৃঢ় এবং শাখাপ্রশাখাযুক্ত। (ii) কাণ্ডে যান্ত্রিক কলা ও সংবহন কলা সুগঠিত। (iii) কাণ্ডের ত্বকে পুরু কিউটিকল থাকে। ত্বক অনেক সময় মোমযুক্ত পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে।
3. পাতা : (i) পাতাগুলি স্থূল, রসালো এবং খস্থসে। (ii) পাতার ত্বক পুরু এবং কিউটিকল্যুক্ত, পাতার ফলকে মোমের আবরণ থাকায় পাতা চকচকে হয়। বাষ্পমোচন রোধের জন্য পাতার এমন অভিযোজন হয়েছে। (iii) পাতার প্যালিসেড কলা সুগঠিত এবং কোশান্তর-রন্ধ্র সাধারণত থাকে না। (iv) পত্ররন্দ্রগুলি নিম্নত্বকের ভিতরের দিকে অবস্থিত।
রুই মাছের অভিযোজন (Adaptation of Rohufish) :
রুই মাছ মুখ্য জলজ প্রাণী। জলে বসবাস করার জন্য এদের দেহে নিম্নলিখিত অভিযোজনগুলি দেখা যায় :
1. দেহাকৃতি (Body contour): রুই মাছের দেহ বেম বা মাকুর মত। দেহ দু'পাশ থেকে চ্যাপ্টা এবং দেহ থেকে কোনো প্রবর্ধক বেরিয়ে থাকে না। জলে সাঁতার কাটার সময় জলের গতি রোধ করার জন্য দেহের গঠন এইরকম হয়েছে।
2. দেহাবরণ (Body covering) : রুই মাছের সারাদেহ সাইক্লয়েড আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। আঁশের পিচ্ছিল আবরণ রুই মাছকে আত্মরক্ষা করতে এবং চলনের সময় ঘর্ষণজনিত বাধা দূর করতে সাহায্য করে।
3. পাখনা (Fins) : পাখনা হল রুই মাছের প্রধান গমন অঙ্গ। রুই মাছের দেহে রশ্মিযুক্ত জোড়- সংখ্যক বক্ষ পাখনা ও শ্রোণি পাখনা এবং বিজোড় সংখ্যক পৃষ্ঠ পাখনা, পায়ু পাখনা এবং পুচ্ছ পাখনা থাকে। পাখনাগুলি রশ্মিবিশিষ্ট হওয়ায় জলের চাপে ছিঁড়ে যায় না। এই সব পাখনাগুলি রুই মাছের চলন, গমন, দিক পরিবর্তন করতে এবং জলের মধ্যে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
4. পার্শ্ব বা স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা (Lateral line) : রুই মাছের দেহের দু'পাশে কানকোর পেছন থেকে লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত দুটি পার্শ্ব বা স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা থাকে। স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করে। এর সাহায্যে মাছ জলের চাপ, তাপ, গভীরতা, pH-মাত্রা বুঝতে পারে; জলের স্রোতের দিক নির্ণয় করতে পারে; শব্দ গ্রহণ করতে এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।
5. বায়ুথলি বা পটকা (Air-bladder) রুই এবং অন্যান্য অস্থিবিশিষ্ট মাছদের (অটিকথিস্ শ্রেণিভুক্ত) উদরগহ্বরে মেরুদণ্ডের নীচে অবস্থিত একটি বায়ুপূর্ণ থলি বা পটকা থাকে। পটকা মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে যথাক্রমে মাছকে জলের ওপরে ভাসতে বা জলের গভীরে নামতে অথবা যে কোনও স্থানে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে।
6. শ্বসন অঙ্ক (Respiratory organ): রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ হল ফুলকা (gills)। গলবিলের উভয়দিকে ফুলকা গহ্বরের মধ্যে মাছের ফুলকা অবস্থিত। রুই মাছের ফুলকা, কানকো (operculum) দিয়ে ঢাকা থাকে। ফুলকাগুলোতে রক্তজালক থাকে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তজালকের রক্তে প্রবেশ করে এবং একই প্রক্রিয়ায় জালক থেকে কার্বন ডাই- অক্সাইড (CO2) নির্গত হয়।
7. হূৎপিণ্ড (Heart) : মাছেদের হূৎপিণ্ড হল ভেনাস অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়। এদের হূৎপিণ্ড একটি অলিন্দ ও একটি নিলয় নিয়ে গঠিত।
8. চোখ (Eye) : রুই মাছের চোখ দুটি পল্লবহীন এবং গোলাকার। প্রতিটি চোখে একটি করে পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, যা জলের ঘর্ষণ থেকে চোখকে রক্ষা করে।
9. নাসরিঞ্জ (Nostrils) : মাছের বহিঃনাসারন্ধ্র আছে, কিন্তু অন্তঃনাসারন্ধ্র থাকে না। নাসারন্ধ্র কেবল ঘ্রাণকার্যে সাহায্য করে।
■ 10. মায়োটোম পেশি (Myotome muscles) : রুই মাছের মেরুদণ্ডের দু'পাশে 'V' আকৃতিবিশিষ্ট মায়োটোম পেশি থাকে। এই পেশির সঙ্কোচনের মাধ্যমে রুই মাছ সাঁতার কাটার সময় মেরুদণ্ডকে দেহের দু'পাশে আন্দোলিত করতে পারে।
পায়রার অভিযোজন (Adaptation of Pigeon) :
পায়রা খেচর প্রাণী। আকাশে ওড়ার জন্য পায়রার নীচের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়

|
| পায়রার দেহ মাকুর মতো |
1. দেহাকৃতি (Body contour) : পায়রার দেহ মাকুর মতো। দেহটি
সামনে ও পিছনে সরু হওয়ায় ওড়ার সময় বায়ুর প্রতিরোধ কম হয়।
2. গ্রীবা (Neck) :
পায়রার গ্রীবা নমনীয়, সরু এবং দীর্ঘ হওয়ায় এরা সহজেই মাথা ঘুরিয়ে চঙ্গুর
সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
3.(Beak) : পায়রার চোয়াল
দুটি চঙ্গুতে রূপান্তরিত হয়েছে, ফলে মাটি থেকে খাদ্য মুখে তোলা সহজ হয়।
• গাছের ডালে বসার জন্য পায়রার অভিযোজন (Adaptation for perching) :
পশ্চাদ পায়ের চারটি আঙুলের মধ্যে তিনটি সামনের দিকে এবং একটি পিছনের দিকে
থাকে।।পায়রার পায়ের পেশি সংলগ্ন কন্ডরাগুলি বিশেষভাবে অভিযোজিত। এই কারণে
পায়রা গাছের ডালে ঘুমন্ত অবস্থায়ও স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে।
5. পৌষ্টিক তন্ত্র (Alimentary system)
ওড়বার জন্য পায়রার অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়, তাই এদের পৌষ্টিক তন্ত্র
অত্যন্ত উন্নত ধরনের। পৌষ্টিক তন্ত্রে গিজার্ড থাকে; অন্যদিকে ওজন
কমাবার জন্য দাঁত, পাকস্থলী, পিত্তাশয়, মলাশয় ইত্যাদি থাকে না।
6. শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system) :
বেশি শক্তির প্রয়োজনে দেহে অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পায়রার ফুসফুসে
কতকগুলি বায়ুথলি বা এয়ার স্যাক (air sacs) থাকে, যা প্রয়োজন মতো
অক্সিজেন জমা করে রাখে এবং দেহের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়ে উড়তে সাহায্য করে।
বায়ুথলি দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণেও কিছুটা সাহায্য করে।
৪. চক্ষু (Eye)
পায়রার চোখ দুটি বেশ উন্নত। চোখে 'পেকটিন' থাকায় এরা তীক্ষ্ণ
দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।
9. মূত্র-জনন তত্ত্ব (Urinogenital system)
ওজন কমাবার জন্য ডান ডিম্বাশয়, ডান ডিম্বনালী, মুত্রথলি এবং শিশ্ন থাকে না।
• হাঁটার জন্য পায়রার অভিযোজন (Adaptation for walking) :
ওড়ার জন্য অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত হওয়ায় পায়রা কেবল পশ্চাদ পদদ্বয়ের
সাহায্যে মাটিতে হাঁটাচলা করে। হাঁটার সময় দেহের ভার শ্রোণিচক্র ও
পশ্চাদ-পায়ের উপর ন্যস্ত হয়। ফলে এই অঞ্চলের অস্থিগুলি দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে।
শ্রোণিদেশের কশেরুকাগুলি পরস্পর যুক্ত ও অনড়। অপরপক্ষে শ্রোণিচক্র উক্ত
কশেরুকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পায়ের অস্থিগুলি অনেকটা 'Z' আকারে বিন্যস্ত।
পায়রার দেহের এই রকম অস্থিবিন্যাস এদেরকে হাঁটাচলা করতে, ওড়ার সময় লাফিয়ে
উঠতে এবং উড়তে উড়তে হঠাৎ মাটিতে দাঁড়াবার সময় দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে
সহায়তা করে।



.jpg)

.png)