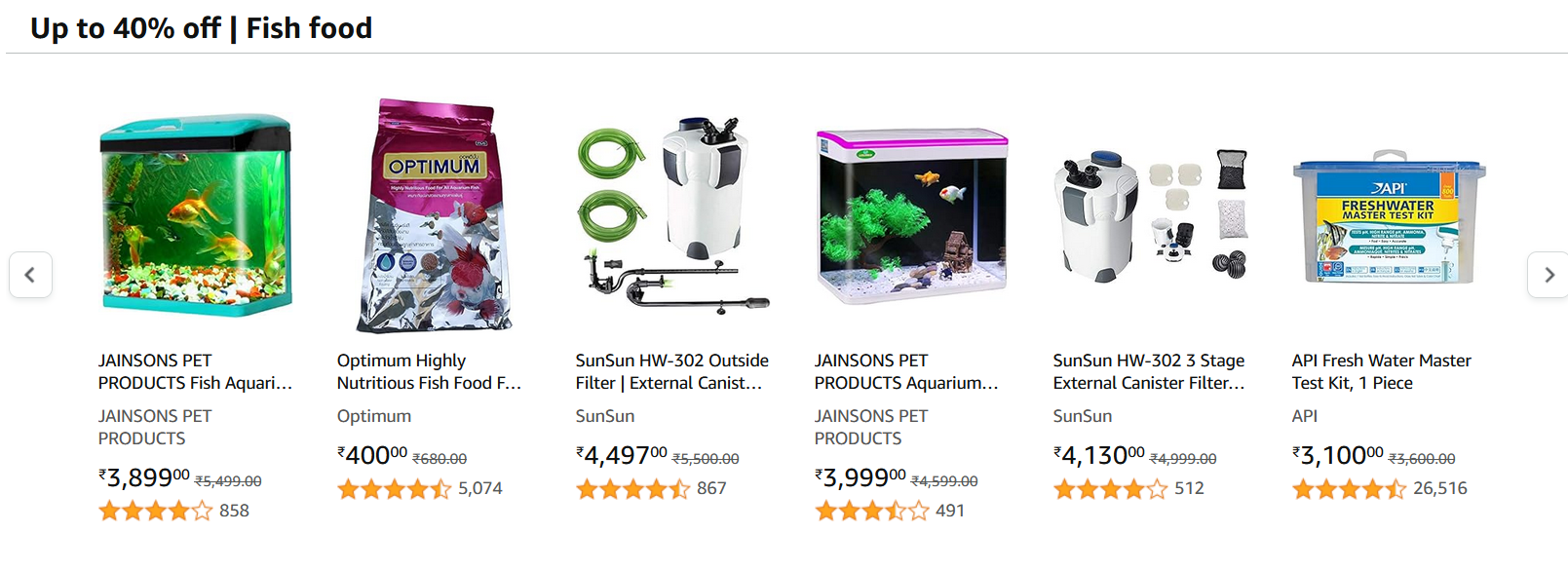চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
শুধু বাংলা ভাষা কেন, সমস্ত পূর্ব-ভারতের নব্যভাষার প্রথম গ্রন্থ এই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। সম্প্রতি জানা গেছে, পুঁথিটির প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ'। এটি আবিষ্কারের আগে সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকেরা মনে করতেন, ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন, রূপকথা—এইগুলি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। কিন্তু বর্তমানকালের আবিষ্কারে এবং গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, উল্লিখিত গ্রন্থ বা কাহিনী প্রাচীন যুগের নয়, অনেক পরবর্তিকালের রচনা। বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত হিসেবে ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদসংকলনকেই উপস্থাপিত করতে পারা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পুঁথি আবিষ্কার ও সম্পাদনা করে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের হারানো দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেন। প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিপত্রাদি সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর ধারণা হয়, প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ বাংলা ভাষায় বোধ হয় কিছু লিখে থাকবেন। নেপাল রাজদরবারে পুঁথির সন্ধানে গিয়ে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি অনেকগুলি সমধর্মী পুঁথির সঙ্গে বাংলা ভাষায় লেখা 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে’র পুঁথি আবিষ্কার করেন। পুঁথিটি প্রাচীন বাংলা ও নেপালি অক্ষরে লিখিত। তিনি পড়ে দেখলেন—এ ভাষা বাংলা, যদিও অতিপ্রাচীন, এবং বৌদ্ধ সহজিয়া গুরুদের রহস্যময় ভাষায় লেখা বলে এর গূঢ় অর্থ উদ্ধার সহজ ব্যাপার নয়। এই পুঁথির সঙ্গে একটি সংস্কৃত টীকা দেওয়া ছিল বলে শাস্ত্রী মহাশয় এর কথঞ্চিৎ অর্থ উদ্ধার করেন এবং এখন আমরা চর্যাগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে যে মোটামুটি অবহিত হয়েছি, তার কারণ ঐ সংস্কৃত টীকার সহায়তা। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। বৌদ্ধতন্ত্রে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন বলে চর্যাপদের ব্যাখ্যা হিসেবে ঐ সংস্কৃত টাকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে। পরে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় চর্যার একটি তিব্বতি অনুবাদও আবিষ্কার করেন। মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা এবং ড. বাগচী আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদের সাহায্যে চর্যার আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা এখন অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছে। অনেক দেশিবিদেশি পণ্ডিত চর্যাপদ নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন, এখনও সে গবেষণার বিরাম হয়নি। প্রয়াত ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১ ৬৪) মহাশয় নেপাল ও তরাই-ভূমি থেকে চর্যার আরও কিছু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছিলেন (১৯৬৩)। এর ফলে চর্যা-গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। তাঁর সংগৃহীত পদ ও তার কয়েকটি শব্দের টীকাটিপ্পনীসহ আমার সম্পাদনায় 'নব চর্যাপদ' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে যে সমস্ত পুঁথি আবিষ্কার করেন, তার মধ্যে যেগুলি তাঁর মতে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত মনে হয়েছিল, সেগুলিকে একত্র করে বাংলা ১৩২৩ সনে (১৯১৬ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে “হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা” এই নামে সুসম্পাদিত করে তিনি প্রকাশ করেন। এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরহ ও কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং 'ডাকার্ণব'। তিনি সব প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত মনে করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালের গবেষণায় নকেই দেখা গেছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-ই শুধু প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় লেখা, অন্য তিনখানির ভাষা বাংলা নয়, শৌরসেনী অপভ্রংশের ভগ্নাবশেষ ঐ ভাষার মেরুদণ্ড। পরে এই গ্রন্থ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে এর ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সমাজদর্শন অতীর কৌতূহলপ্রদ। অবাঙালি পণ্ডিতেরাও (যথা—রাহুল সাংকৃত্যায়ন) এই গ্রন্থ নিয়ে সমান উৎসাহে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। সংকলনটির যথার্থ কি নাম ছিল তা নিয়েও কিছু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী একে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বলে গ্রহণ করতে চাননি। তাঁদের যুক্তিও ফেলে দেওয়া যায় না। যাই হোক, ইদানীং এই সংকলন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (সংক্ষেপে 'চর্যাপদ') নামে অভিহিত হয়েছে বলে আমরা একে শাস্ত্রী মহাশয়-পরিকল্পিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামেই উল্লেখ করব, যদিও এর প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ'।
চর্যাপদের পুঁথিটি চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে নকল হতে পারে। এতে মোট পঞ্চাশটি পদ ছিল, কিন্তু তিনটি পুরো এবং আর একটি পদের শেষাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। উক্ত পুঁথিতে মোট সাড়ে-ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে—অবশ্য চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদে বাকি সাড়ে তিনটির পরে হদিশ মিলেছে। প্রত্যেক পদের অন্তে বৌদ্ধপণ্ডিত মুনিদত্ত সংস্কৃতে তার টীকা সংযোজিত করেছেন। চব্বিশ জন পদকর্তা বা সিদ্ধাচার্য এই সমস্ত সাধনভজন-বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। প্রত্যেক পদের শেষে পদকর্তার নাম দেওয়া আছে বলে কোন পদটি কার রচিত, তা নির্ধারণ করা যায়। প্রধান পদকর্তাদের মধ্যে সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, শান্তিপাদ ও শবরপাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের একাধিক পদ এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে। তিব্বতি গ্রন্থ থেকে এই পদকর্তাদের কিছু কিছু পরিচয় উদ্ধার করা যায়—এঁদের অনেকেই বাংলা, মিথিলা, ওড়িশা ও কামরূপের অধিবাসী ছিলেন—তাই তাঁদের পদে পূর্ব-ভারতের জীবনচিত্র অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। শৈব নাথধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে যে চৌরাশি সিদ্ধা বা ধর্মগুরুর উল্লেখ আছে, এঁদের কেউ কেউ তারই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য এঁদের নামগুলি সবই ছদ্মনাম—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বা সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এঁরা নিজ নিজ কুলপরিচয়, নামধাম প্রভৃতি পরিত্যাগ করে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন।
চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন, এর রচনাকাল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে হওয়াই সম্ভব। সংকলনের প্রথম পদকর্তা লুইপাদ (যিনি আদি পদকর্তা বলে সম্মানিত) দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলে দশম শতাব্দী থেকেই এই পদসমূহের রচনা ও সংকলন কার্য চলতে থাকে। ভাষা দেখেও মনে হয়, খ্রীঃ দশম শতাব্দীর দিকে বা তার সামান্য পূর্বে, যখন মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে বাংলা ভাষা সবেমাত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তখন সেই অপরিণত ভাষায় সিদ্ধাচার্যগণ উক্ত সম্প্রদায়ের জন্য পদগুলি লিখেছিলেন। এ ভাষার মূল বুনিয়াদ মাগধী অপভ্রংশ থেকে জাত প্রাচীনতম বাংলা ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত; অবশ্য তখনও আদি বাংলা ভাষায় শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব রয়ে গিয়েছিল। তবে এতে বেশির ভাগ শব্দই মাগধী অপভ্রংশজাত। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেরও আদিম নিদর্শন এই চর্যাপদে দুর্লভ নয়। এইজন্য ভাষা ও ছন্দের দিক দিয়ে চর্যাপদ বাংলার নিকটতম— যদিও এতে দু-চারটি প্রত্যন্ত প্রদেশের শব্দও আছে। একটু দুর্বোধ্য রহস্যময় ভাষায় এই পদগুলি রচিত হয়েছে। এই হেঁয়ালি ভাষার নাম ‘সন্ধ্যাভাষা'—যার অর্থ, যে-ভাষা রহস্যময় এবং যা বুঝতে বিলম্ব হয় অথবা, যার অর্থ সম্যক ধ্যানের (সম্-ধৈ ধাতু) দ্বারা বুঝতে হয়, তা সন্ধ্যাভাষা' বা 'সন্ধাভাষা"। এই পথের পথিক ভিন্ন চর্যাপদের তাৎপর্য আবিষ্কার সহজ নয়। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে সংযুক্ত মুনিদত্তকৃত সংস্কৃত টীকাটি না থাকলে এর তাৎপর্য চিরদিন দুর্বোধ্যই রয়ে যেত। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিকূল ব্যক্তি বা গোঁড়া ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, যাঁরা সহজিয়া বৌদ্ধদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাঁদের শ্যোনচক্ষু থেকে এই গূঢ় ধর্মাচারকে আড়াল করে রাখার জন্যই বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যেরা এই রকম ‘সন্ধ্যাভাষা’র ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন।
চর্যাপদে বজ্রযান ও সহজযানের গূঢ় ধর্ম, সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানা ধরনের রূপক প্রতীক ও চিত্রকল্পের দ্বারা আভাস-ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত কালক্রমে নানা উপধর্মে (যেমন—বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সাধনতত্ত্বে এঁদের নানা মতপার্থক্য থাকলেও নির্বাণ সম্বন্ধে এঁরা সকলেই একলক্ষ্য ছিলেন। বাস্তব জীবনের জরামরণ ও পুনর্জন্মের বিষচক্র পার নির্বাণলাভই বৌদ্ধধর্মের মন্ত্র। এঁরাও সেই পথের যাত্রী। তবে সেই পথে পৌঁছাতে গিয়ে পদকর্তারা নানাপ্রকার গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের উল্লেখ করেছেন, যা অবলম্বন করলে সাধক অতি সহজে নির্বাণে পৌঁছে যেতে পারেন। এঁরা সাধনভজনের তত্ত্বকথা বললেও অল্পবিস্তর কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভাষা, ছন্দ ও রূপনিমিতিতে এঁদের যে বেশ দক্ষতা ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধিগ্রাহ্য দার্শনিকতা ও রহস্যময় আচার-আচরণকে অনেক স্থলেই এঁরা কাব্যলোকে উন্নীত করেছেন। নির্বাণতত্ত্বকে কোনো কোনো পদকর্তা নিজের দয়িতারূপে বর্ণনা করেছেন; তাই নির্বাণলাভের আকাঙ্ক্ষা কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে প্রিয়সঙ্গকামনায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি এই সমস্ত পদগুচ্ছে তৎকালীন সাধারণ (সময়ে সময়ে হীন অভ্যজ) বাঙালির প্রতিদিনের ধূলিমলিন জীবনচিত্র, সুখদুঃখ হাসিকান্নার টুকরো টুকরো রেখাচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দার্শনিকতা এবং আদিম বাংলা সাহিত্যের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় একখানি স্মরণীয় সংকলন। এটি আবিষ্কৃত না হলে আদিমযুগের বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষা অজ্ঞাতই রয়ে যেত। সে দিক থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে নমুনাস্বরূপ একটি চর্যাপদ উদ্ধৃত হল :
কাহেরে ঘিনি মেলি আছহ কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ল চৌদীস ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরি ॥
তিন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী ॥
হরিণী বোলাঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন ছাড়ী হোছ ভাঙো ॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভনই মৃঢ় হিঅহি ন পইসই ॥ (৬ চর্যা)
অনুবাদ : কাকে গ্রহণ করি, কাকেই বা ত্যাগ করে থাকি? চারিদিক বেড়ে হাঁক পড়ল। এক মুহূর্তও রেহাই দেয় না। হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না। হরিণটা হরিণীর নিলয়ও জানে না। হরিণী বলে, ওরে হরিণ, শোন্ তুই। এ বন ছেড়ে পালা। (শুনে) হরিণ এত দ্রুত ছুটল যে, তার ক্ষুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলেন, মূঢ়ের হৃদয়ে (এ সব) প্রবেশ করে না।
এখানে সিদ্ধাচার্য ভুসুকুপাদ হরিণশিকারের চিত্রকল্প ব্যবহার করে সহজিয়া নির্বাণলাভের তত্ত্বদর্শন হেঁয়ালির ভঙ্গিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন। অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তহরিণ নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে নিয়ে আসে, তার চারদিকে তখন জরামৃত্যু শিকারীর দল মার-মার করে তেড়ে আসে। পরে চিত্ত নিজের বিপদ বুঝতে পেরে, জাগতিক ভোগ-সুখ থেকে বিরত হয়ে নির্বাণ-হরিণীকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই ব্যাকুলতার বশেই স্বয়ং নির্বাণ যেন হরিণীর বেশে এসে নির্বাণলুব্ধ চিত্তহরিণকে ঠিক পথ বাতলে দেয়। এখানে এই তত্ত্বকথাটিকে পদকর্তা অতি চমৎকার বাস্তব হরিণ শিকারের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র পদগুলির মুখ্য আবেদন মুমুক্ষু চিত্তের নিকট হলেও এর মধ্যে কোনো কোনো স্থলে যে গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। আর একটি হেঁয়ালিভরা পদ উল্লেখ করি :
টালত ঘর মোর নাহি পড়িবেবী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল যায়।
দুহিল দধু কি বেল্টে যামায় ৷
বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।
জো সো বুধী শোই নিবুধী।
জো সো চোর সোই সাধী ॥
নিতি নিতি যিআলা যিহে সম জুঝা।
ঢেণ্ঢনপায়ের গীত বিরলে বুঝঅ (৩৩ চর্যা)
অনুবাদ: পাহাড়ের টিলায় আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, কিন্তু নিত্যই অতিথি আসে। দিন দিন ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলে। কী দুঃখ, দোয়া দুধও বাঁটের মধ্যে চলে যায়। বলদের বাচ্চা হল, গাভী রইল বন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যা পালান (গোমহিষের স্তন, Udder) থেকে দোহন করি। যে বুদ্ধিমান, সেই নির্বুদ্ধি। যে চোর, সে-ই সাধু। রোজ রোজ শিয়াল সিংহের সঙ্গে যুজছে। ঢেণ্টনপাদের (পদকর্তা) এই পদের তাৎপর্য অল্প লোকেই বুঝতে পারে।
এখানে দরিদ্র গৃহিণীর দুরবস্থার প্রতীকে ও পরস্পরবিরোধী ইঙ্গিতের সাহায্যে গূঢ়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কীভাবে মোক্ষ-নির্বাণ ও শূন্যতত্ত্বে পৌঁছানো যায়, এবং কীভাবে এই মায়ার জগৎ পরিত্যাগ করে চেতনার শীর্ষদেশে ওঠা যায়, এখানে তাই উপমা-রূপক ও ব্যঞ্জনার সাহায্যে ইঙ্গিতে ইশারায় বলা হয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করা যাক—টিলার উপরে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই—অর্থাৎ চেতনার শীর্ষদেশে উঠেছি, এখন আমার চারিদিকের মায়ার জগৎ লুপ্ত হয়ে গেছে, সংসারচেতনাও বিনাশ পেয়েছে। সংসার যে শূন্যস্বভাব, অর্থাৎ অস্তিত্বহীন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। মনই সবকিছু সৃষ্টি করে, তাই তাকে বলদ বলা হয়েছে, কিন্তু মোক্ষ-নির্বাণ (সহজিয়ারা মোক্ষ-নির্বাণ-শূন্যকে স্ত্রীভাবে কল্পনা করেছেন) কিছুই সৃষ্টি করে না, তাই সে হচ্ছে বন্ধ্যা। এই পদে সাধনা-সংক্রান্ত আরও অনেক গূঢ় ইঙ্গিত আছে যা টীকাকার মুনিদত্ত সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।
কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে শৈব নাথধর্মের কয়েকখানি গ্রন্থ ও ছড়াপাঁচালি বৌদ্ধ শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন, রূপকথা (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঠাকুরমায়ের ঝুলি'তে “এর অনেকগুলি সংগ্রহ করেছিলেন) প্রভৃতি সাহিত্যের নিদর্শন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আদিম-যুগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। খ্রীঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শৈব নাথসম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথের মহিমাবিষয়ক অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মারাঠা সাহিত্যে ঐ ধরনের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, হিন্দি সাহিত্যের প্রাচীন
পর্বে গোরক্ষমহিমাব্যঞ্জক কাব্য-কাহিনীর অভাব নেই। সুতরাং অনুমান খ্রীঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে নাথধর্মের অন্যতম কেন্দ্র গৌড়-বঙ্গেও গোরক্ষনাথ, ময়নামতী ও তাঁর ছেলে গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল। কিন্তু গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের গান-সংক্রান্ত পুঁথি ও লোকগাথাগুলি (ব্যালাড), যা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং লোকমুখ থেকে শুনে লিখে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি আদৌ প্রাচীন নয়। সুতরাং এই সমস্ত পুঁথিপত্রকে চর্যাপদের সমকালীন বলে গ্রহণ করা যায় না। রামাই (রমাই) পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’ও বিশেষ প্রাচীন নয়, বড়ো জোর সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। ডাক ও খনার বচনের ঐতিহাসিক কালক্রম নির্ধারণ করা অসম্ভব—সুতরাং এর প্রাচীনতাও তর্কসংকুল। রূপকথাগুলি বাংলার চিরকালের সম্পদ, সন-তারিখ দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। তাই সবদিক চিন্তা করে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'কেই আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায়।
কেউ কেউ এই প্রাচীন যুগকে যুগ’ বলতে চান। কারণ এই সময়ে রচিত গ্রন্থাদিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়প্রকার মতাদর্শ স্থান পেয়েছে। অবশ্য শুধু চর্যাপদ ধরলে এই অভিধা আরও সংকুচিত হয়ে আসবে। নাথসাহিত্য ও শূন্যপুরাণ বাদ চলে গেলে এই যুগকে এককথায় হিন্দু-বৌদ্ধযুগ বলা যাবে না। কারণ চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধ সহজিয়ামতের পদসংগ্রহ। অবশ্য এতে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, যোগ ও নাথধর্মেরও প্রভাব আছে। তাই বলে একমাত্র চর্যাপদের ওপর ভিত্তি করে সমস্ত যুগটাকে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ নাম দেওয়া সমীচীন নয়।




.png)