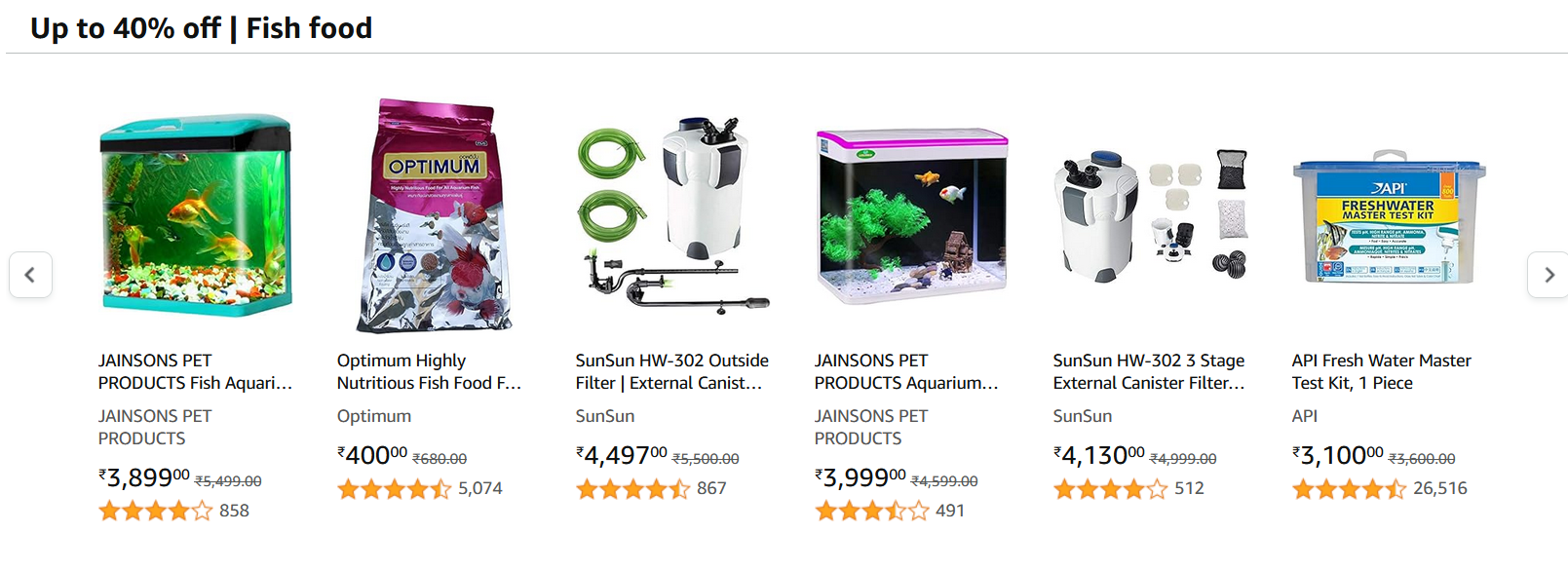প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ
ভারতবর্ষের ইতিহাস : প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ
ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ইংরাজী 'হিস্ট্রি' শব্দটির প্রসঙ্গ ওঠা স্বাভাবিক। সাধারণভাবে আমরা ইংরাজী শব্দ 'হিস্ট্রি' অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। উল্লেখ্য, গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস 'হিস্ট্রি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপর থেকে ধীরে ধীরে এর বহুল ব্যবহার শুরু হয়।
ইংরাজী 'হিস্ট্রি' শব্দটির ন্যায় 'ইতিহাস' শব্দটিও অতি প্রাচীন। ঐ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। সেখানে ইতিহাসকে অথর্ববেদের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে— 'অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ”। সুতরাং ‘ইতিহাস’ শব্দটি প্রথম পাই সংস্কৃত ভাষায়। এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার সেই সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস সংক্রান্ত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বর্তমানকালের 'হিস্ট্রি' বা ইতিহাসের সাদৃশ্য খুব বেশি নেই। কারণ তখন ইতিহাস ছিল অনেকটাই পুরাণ নির্ভর। রোমিলা থাপারের ধারণা অনুযায়ী তখন ইতিহাস ছিল 'পুরাণ-আশ্রয়ী'। একে বলা হয়ে থাকে ইতিহাস- পুরাণ'। এই ইতিহাস-পুরাণকে অনুসরণ করেই মানব সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত প্রাচীন ভারতীয় ধারণার কিছুটা আভাস মেলে। প্রসঙ্গত বলা যায় অথর্ববেদেই পুরাণ ও গাথার সঙ্গে ইতিহাস একত্রে উল্লেখিত হয়েছে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বৈদিক যুগে 'ইতিহাস' নামক বিদ্যাটি তৎকালীন ধারা অনুযায়ী অধ্যয়ন করা হত।
এখন আসা যাক ইংরাজী 'হিস্ট্রি' এবং আমাদের বহুল ব্যবহৃত 'ইতিহাস' শব্দ ও বিদ্যাগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে অতীতের কোনো বিষয় বা ঘটনা তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক যাইহোক না কেন, সে সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চার জন্য যে বিদ্যা আমরা অধ্যয়ন করি তা ভারতবর্ষে বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় ইতিহাস নামে পরিচিত। ‘ইতিহাস' নামক এই বিদ্যাটি ইংরাজী ‘হিস্ট্রি' নামক বিদ্যাটির সঙ্গে অভিন্ন বলেই ধরা হয়। কারণ এই দুটি বিদ্যার উদ্দেশ্য ও চর্চার ধারা প্রায় এক। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইংরাজী 'হিস্ট্রি' শব্দটির নিছক অনুবাদ ইতিহাস নয়।
এতদ্সত্ত্বেও আধুনিককালে 'হিস্ট্রি' ও 'ইতিহাস'-এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এখানে যেটা জোর দিয়ে বলা দরকার তা হল প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অতীত তথা ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল; তবে সেই ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিককালের ইতিহাস বা হিস্ট্রির সঙ্গে অভিন্ন নয়। এখানে প্রাচীনকালের পুরাণ নির্ভর ইতিহাস অধ্যয়ন (ওপরে আলোচিত)-এর সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে শুরু হওয়া পাশ্চাত্য ধারায় অতীত ঘটনার বিচার ও রীতিনীতির পার্থক্যকে বুঝতে হবে। বস্তুত, আধুনিককালের হিস্ট্রি বা ইতিহাস তথা অতীত চর্চার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের অতীত তথা ইতিহাস সংক্রান্ত চিন্তাধারার মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কেননা, বর্তমান যুগে অতীতকে অনুধাবন করার জন্য যেসব পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয় যেমন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা, কালানুক্রম, নির্ভরযোগ্য তথ্য বা আকর উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ প্রভৃতি সেগুলি প্রাচীন ভারতে অতীত তথা ইতিহাস চিন্তায় ছিল প্রায় অনুপস্থিত।
'ইতিহাস' শব্দটি ভাঙলে দাঁড়ায় 'ইতি-হ-আস'। এর অর্থ হল এইরূপই ছিল বা ঘটেছিল। অর্থাৎ ইতিহাসের কারবার অতীতকে নিয়ে। সেই অতীত বহুকাল আগের হতে পারে। আবার কিছুকাল আগের অতীত ঘটনাও হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার সব অতীত ঘটনাই ইতিহাস নয়। বস্তুত, অতীত ও ইতিহাস বিষয়ক অতীতের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়। আসলে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনাকে ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ (Historical Fact) হতে হয়।
অতীত ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় বর্তমানকালে। বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় অতীতের আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিকে বোঝা ও ব্যাখ্যার জন্য। এডওয়ার্ড হ্যালেট কার যথার্থই বলেছেন, ইতিহাস হল অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অন্তহীন কথোপকথন'। অতীত ও বর্তমানের বিশ্লেষণ থেকে কিছুটা হলেও ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যেতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমানকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের ধ্রুব সত্য সব ক্ষেত্রে উদ্ঘাটিত হয়, এমন কথা জোর করে বলা অসম্ভব। এক কথায় অতীতের সার্বিক নয়, আংশিক পুনরুদ্ধার ঘটানো সম্ভব বর্তমানকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রে।
ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহাসিকের যোগ নিবিড়। যেমন মানুষকে বাদ দিয়ে ইতিহাস হয় না তেমনি ঐতিহাসিকও এক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকেন। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা ঐতিহাসিক ছাড়া অতীত ঘটনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা বিচার বিশ্লেষণ আদৌ সম্ভব নয়। অতীত ঘটনার পর্যবেক্ষণের জন্য ঐতিহাসিকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল আকর তথ্য। তথ্যকে যাচাই করে ইতিহাসের নির্মাণের জন্য অপরিহার্য হল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা। এই কারণেই দেখা যায় অতীতচর্চা করতে গিয়ে একই ঘটনার ওপর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, এটাই স্বাভাবিক। এরই ফলে সেই সংশ্লিষ্ট অতীত বিষয় বা ঘটনা প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই (বিশেষ করে প্রাচীন ভারত প্রসঙ্গে) অতীত চর্চার কাজের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিক নিজে সেই ঘটনার সাক্ষী হন না। ফলে অতীতের যে বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে তিনি চর্চা করেন। সেজন্য তাঁকে যেমন আবার তথ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় তেমনি তাঁর পরীক্ষা- নিরীক্ষা কতকাংশে তাঁর সমকালের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে। অশীন দাশগুপ্তর বক্তব্য হল 'ঐতিহাসিক বর্তমানকে সঙ্গে নিয়ে চলেন'। ইতিহাসচর্চা প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হবে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক যুগে বিশেষ করে ঊনবিংশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসচর্চার ধারা ও পদ্ধতিতে বারে বারেই পরিবর্তন ঘটেছে। এটাই বাস্তব ও স্বাভাবিক। এর ফলে অতীত ঘটনার যেমন পুনর্মূল্যায়ন ঘটে তেমনি অভিনব ব্যাখ্যাও বেরিয়ে আসে। ইতিহাস তথা অতীতচর্চা তখন হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয়।
অতি সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চা বিষয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের সুচিন্তিত মতামত এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। এ তাঁর মতে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে এখনও ইতিহাস পড়ানো হয়ে থাকে সাবেক ও বস্তাপচা পদ্ধতিতে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও ইতিহাসের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি হল, ইতিহাস কেবলমাত্র অতীত ঘটনার খবর দেয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার সাম্প্রতিককালের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তা যথার্থ নয়। এখন যেটার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে তা কেবল অতীত সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করাই নয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অতীতকে বোঝা ও অতীতের ব্যাখ্যা দেওয়াই ইতিহাসচর্চার প্রধান লক্ষ্য। এককথায় অতীতকে অনুধাবন করা এবং অতীত ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া—এই দুই বিষয়ের আধার হল ‘ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি' (‘হিস্টরিক্যাল মেথড')। এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক—সকলেরই ধারণা থাকা অপরিহার্য। ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম পদক্ষেপ হল তথ্য সংগ্রহ করা। এর পরবর্তী ধাপ হল প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা এবং নিশ্চিত হওয়া যে ঐ বিশেষ তথ্যসূত্রটির যথার্থতা সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। তৃতীয় পদক্ষেপ হল অতীতের ঘটনাবলীর মধ্যে এর সম্পর্ক আছে কিনা তা যাচাই করা, বিশেষ করে যদি কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়ে গবেষক/বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করে তার যথাযথ উত্তর খুঁজতে হবে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কল্পনা বিলাসের কোনো জায়গা নেই। অতীত ও ইতিহাস বিষয়ক একটি সুপরিচিত বক্তব্য হল—ইতিহাস কেবল রাজা
রাজড়ার গল্প নয়—তা হল মানুষের কাহিনি। কিন্তু মনে রাখা দরকার মানুষ যখন একা তখন তার কোনো ইতিহাস নেই। অর্থাৎ অনির্দেশ্য আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে যাঁরা একা চলেন ইতিহাস তাঁদের ছুঁতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ হলে তবেই তা ইতিহাসের আওতায় আসে। এ প্রসঙ্গে দুই দশক আগে ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, “সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতাশ্রয়ী তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস'। একলা মানুষ ও সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে তিনি যে একটি সুন্দর উপমা টেনেছেন তাও এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করেছিলেন ব'লে ইতিহাসে স্থান পাননি, তিনি নিজের মোক্ষ উপেক্ষা করে অন্যের মুক্তির জন্য সংসারে ফিরেছিলেন তাই তিনি ইতিহাসের বুদ্ধ।
অতি সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চায় একটি নতুন ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে এবং তা হল জিজ্ঞাসু মনোভাবে উদ্বুদ্ধ না হয়ে ও স্বাধীনভাবে ভাবনা চিন্তা না করে ইন্টারনেটের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হওয়া। ইন্টারনেটে যা জানা যাচ্ছে তাকে অবধারিত সত্য বলে মেনে নেওয়ার একটা অভ্যাস অনেকের মধ্যেই বর্তমানে বেশ ভালোভাবেই বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে রোমিলা থাপার এক জায়গায় লিখছেন যে, ইন্টারনেটে যেমন যথেষ্ট চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ বহু লেখা থাকে, তেমনি আবার অসংখ্য লেখাকে মূর্খামি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে যেমন ইচ্ছে বক্তব্য আপলোড করে দিতে পারে। কিন্তু তাকে অবধারিত সত্য বলে মেনে না নিয়ে যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণের পর তাকে গ্রহণ বা বর্জন করা বাঞ্ছনীয় হবে।
ইতিহাস তথা ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যুগবিভাজন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের সমস্ত দেশের ইতিহাস রচনা ও পাঠের ক্ষেত্রে যুগবিভাজন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, একটি নির্দিষ্ট সময়কালের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সময়কালের মৌলিক কিছু পার্থক্য থাকে। সেই পার্থক্য বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে হাজার হাজার বছরের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্যায় বা ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। ইতিহাসের যুগ বা পর্যায় বিভাজন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোনো কোনো পণ্ডিত রাজনৈতিক, কেউ আর্থ-সামাজিক, কেউ আবার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ বিভাজন করে থাকেন।
আধুনিক রীতি অবলম্বন করে ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চায় যুগবিভাগের ধারণাটির জন্ম ঊনবিংশ শতকের গোড়ায়। এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য ধারার। যুগবিভাগের ব্যাপারে অগ্রণী হন উপযোগিতাবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী জেমস মিল। উল্লেখ্য, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে জেমস মিলই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ—এই তিনটি পর্বে ভাগ করেন। এই বিভাজন যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা ‘হিন্দু' ও 'মুসলমান' পর্ব দুটির সঙ্গে ‘খ্রিস্টান্’-এর পরিবর্তে ‘ব্রিটিশ'-এর প্রয়োগের মধ্যে সুস্পষ্ট। বলা বাহুল্য, মিলের এই ধরনের পর্ব বিভাজনের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রথম দুটি পর্বের তুলনায় শেষ পর্ব অর্থাৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারতের সার্বিক অগ্রগতিকে তুলে ধরা। জেমস মিল প্রদত্ত ঐ পর্ব বিভাজন যথেষ্ট সমালোচিত। বস্তুত, 'হিন্দু', মুসলমান—এই দুটি সুপরিচিত ধর্মের সঙ্গে যুগবিভাগের বিষয়টি যুক্ত করার প্রচেষ্টার মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধির পরিচয় ফুটে ওঠে।
পরবর্তীকালে ভারত ইতিহাস চর্চায় হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগের ধারণার পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। তবে খুব বেশি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ঐ তিনটি ধারার পরিবর্তে যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দকে প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্য যুগের সূচনা হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। আবার মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দকে। বলা বাহুল্য, কেবল রাজনৈতিক পালাবদলকে পর্যায়ক্রমের মাপকাঠি হিসাবে এক্ষেত্রে বিচার করা হয়েছে। কেননা, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবকের নেতৃত্বে দিল্লিতে সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। অপরদিকে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে অধিষ্ঠিত মুঘল শাসনের ক্রমিক অবক্ষয়ের সুযোগে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থানের সূত্রপাত ঘটে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে।
প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক—এই তিনটি পর্বে ইতিহাসের পর্যায়ক্রম নির্ধারণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক মানসিকতা জড়িত, এমন ধারণা কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিককালে। কারণ ইতিহাসচর্চায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ইউরোপীয় ত্রিস্তর ছকের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এর মধ্যে। যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় যুগবিভাজনের ক্ষেত্রে তিন না ততোধিক পর্বের প্রয়োগ ঘটানো বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় ঔপনিবেশিক আমলে ঊনবিংশ শতকে ইতিহাসচর্চায় যুগবিভাগের ক্ষেত্রে ত্রিধারা প্রচলনের আগে দীর্ঘকাল ধরে চতুর্যুগের ধারণা বলবৎ ছিল। উল্লেখ্য, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগের কল্পনা করা হয়েছে ইতিহাস-পুরাণ নামক রচনাবলীতে। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সনাতন ভারতীয় এই চতুর্যুগের ধারণায় কালের গতি চক্রাকার। কারণ সত্য থেকে ক্রমশ কলিযুগে গমন এবং তারপর আবার সত্যযুগে প্রত্যাবর্তনের ধারণা এতে উপস্থিত। অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধারণার ন্যায় সনাতন ভারতীয় চিন্তাধারায় কালের গতি ক্রমশ অগ্রবর্তী বা সম্মুখমান বা প্রবহমান নয়— সেখানে পরিবর্তনশীলতা বিরাজমান, তবে তা চক্রাকারে পুনরাবর্তনের ধারায়।
সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক—এই প্রচলিত ত্রিধারার সঙ্গে আদি মধ্যযুগ (Early Medieval) নামে একটি যুগের সংযোজন লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় সুপ্রাচীনকাল থেকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ এমন কি ত্রয়োদশ শতকের শেষ (১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সময়কালকে প্রাচীন যুগ হিসাবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ঐ চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়েছে বিগত কয়েক দশক থেকেই। এই সমগ্র সময়কালটিকে (অর্থাৎ ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) প্রাচীন না বলে 'আদিপর্ব' বলার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে সাধারণভাবে সুপ্রাচীন কাল থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কিছুকাল অর্থাৎ ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালকে প্রাচীন যুগ বলেই এখনও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোনো কোনো পণ্ডিত আবার ঐ একই সময়কাল, (৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)-কে আদি ঐতিহাসিক পর্ব (Early Historical Phase) বলার পক্ষপাতী। আর আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দ তথা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল সাম্প্রতিককালে কিছু ঐতিহাসিক কর্তৃক আদি মধ্যযুগ (Early Medieval) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। একথা সঠিক যে আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্বতন সময়কালের তুলনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। তাই সাধারণভাবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কাল একটি স্বতন্ত্র কালগত পরিচিতির দাবিদার। তবে আলোচ্য সময়কালটিকে ‘আদি মধ্যযুগ’ ছাড়াও ‘বিকাশোন্মুখ মধ্যযুগ’, ‘আদি মধ্য যুগাভিমুখী' প্রভৃতি নামকরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে এই বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে।
সূত্র নির্দেশ
১. লাতিন শব্দ 'হিস্টর’ থেকে ‘হিস্ট্রি' শব্দটি এসেছে। ‘হিস্টর' কথার অর্থ জ্ঞান। ১৩. অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার ও অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর মধ্যে কথোপকথন, (প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট) দ্রষ্টব্য ফ্রন্টলাইন, সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ১-৪০; দ্বিরালাপে রোমিলা থাপার ও আলাপে রণবীর চক্রবর্তী (ফ্রন্টলাইনের বঙ্গানুবাদ), অনুষ্টুপ, শারদ সংখ্যা, ১৪২২ (সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা), পৃ. ৪৩০-৩১।
২. অশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, পৃ. ১৭। ২৩. সূত্রনির্দেশ ১-এর অনুরূপ, অনুষ্টুপ, শারদ সংখ্যা, ১৪২২, পৃ. ৪৫৫।
৩. এই নামকরণ ভারত ইতিহাস প্রসঙ্গে একেবারে সাম্প্রতিক হলেও আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ঘটেছে বহুকাল আগে। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের নাম উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ তাঁর প্রণীত বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে। ৪. বি. ডি. চট্টোপাধ্যায়, দ্য মেকিং অফ আর্লি মিডেইভ্যাল ইন্ডিয়া, পৃ. ৫-১৩ দ্রষ্টব্য।
Tags
History



.png)