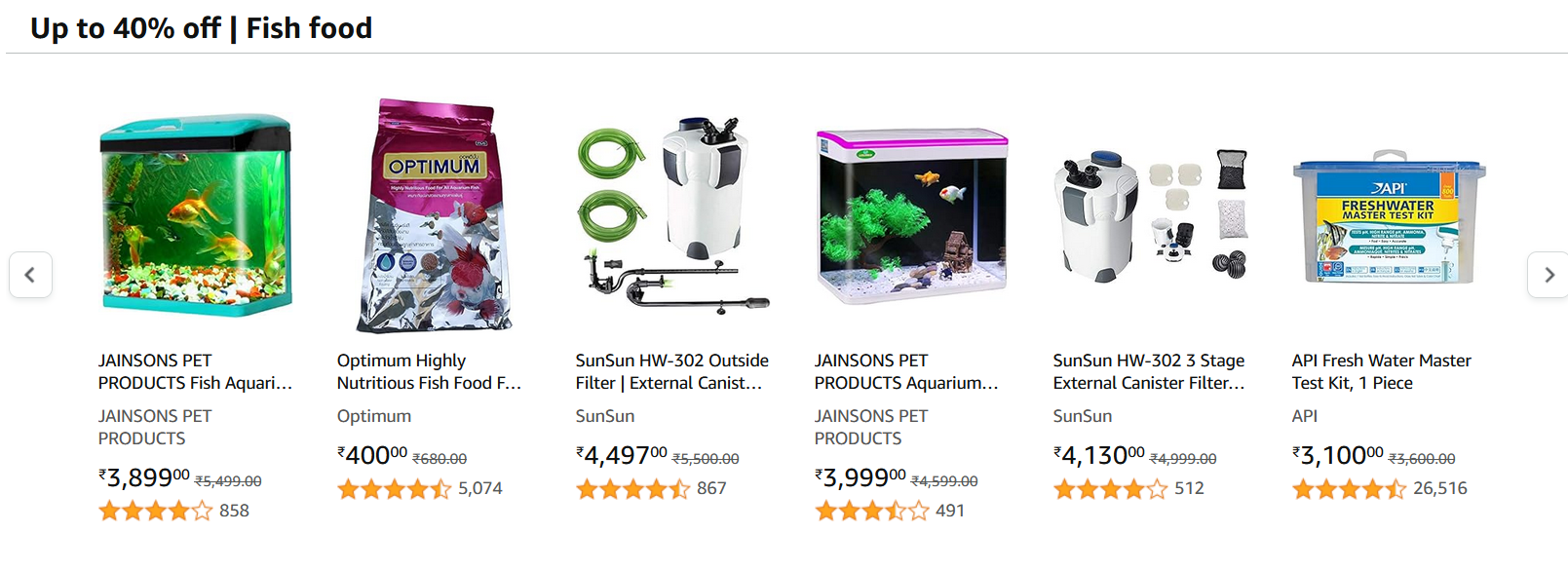|
| হরপ্পা সভ্যতা |
হরপ্পা সভ্যতার মতো জটিল নগরাশ্রয়ী সমাজজীবন হঠাৎ করে রাতারাতি গজিয়ে ওঠেনি। সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে এই সভ্যতা তিনটি পর্যায়ে বিন্যাস্ত। এগুলি হল যথাক্রমে হরপ্পা সংস্কৃতির আদিপর্ব (Early Harappan), বিকশিত বা পরিণত পর্ব (Mature Harappan) অর্থাৎ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পর্ব এবং হরপ্পা-পরবর্তী (Late Harappan) পর্ব। আগের অধ্যায় (চতুর্থ)-এ রাভি নদীর তীরে অবস্থিত হরপ্পা প্রত্নকেন্দ্রের প্রাচীনতম পর্ব (রাভি পর্ব নামেও পরিচিত)-র সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ অব্দ এবং ঐ প্রত্নকেন্দ্রের কোটডিজি পর্ব খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জে. এম. কিনোয়ার ও আর. জি. মিডোর সাম্প্রতিক উৎখননের ওপর ভিত্তি করে ঐ কাল নির্ধারিত হয়েছে। বস্তুত, হরপ্পার প্রত্নকেন্দ্রে রাভি পর্ব থেকে কোটডিজি পর্ব অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ পর্যন্ত সমগ্র সময়কাল ধরে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং ঐ সমগ্র সময়কালটি (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দ) হরপ্পা সংস্কৃতির আদি পর্ব বলে বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর পরিণত পর্ব (Mature Harappan)-র সময়কাল সম্পর্কে আলোকপাত করা সমীচীন হবে।
হরপ্পা সভ্যতার কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে পুরাতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য আছে। খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুগুলির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁদের অনলস প্রয়াস সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কোনো স্থির ঐকমত্যে আসতে পারেননি। হরপ্পা সভ্যতার তারিখ নির্ণয়ের ব্যাপারে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ও মধ্যভাগে যে ধারণা করা হয়েছিল এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদ নানা তত্ত্ব খাড়া করেছেন, যার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা কতকগুলি সুচিন্তিত মতামত পেয়েছি।
হরপ্পা সভ্যতা (Harappan Civilisation) :
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাইরেক্টর স্যার জন মার্শাল-এর তত্ত্বাবধানে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেন-জো-দারোতে এবং দয়ারাম সাহানী পাঞ্জাবের মন্টেগোমারী জেলাতে খননকার্য চালিয়ে এক উন্নত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। প্রথমে খননকার্য চালিয়ে সাতটি স্তর আবিষ্কৃত হয়। সর্বনিম্ন স্তরটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ ফুট গভীরে পাওয়া গেছে। তবে সাম্প্রতিককালে 'রেডিয়ো কার্বন-১৪' এবং 'ডেনড্রোক্রোনোলজি' পদ্ধতির সাহায্যে হরপ্পার কালনির্ণয় বা প্রাচীনত্ব নিরূপণ অনেক সহজ হয়েছে।
ড. ফ্রাঙ্কফুট বলেন সুপ্ত অবস্থায় এই সভ্যতা প্রায় ৫০০ বছর ছিল। তাই হরপ্পার সভ্যতার আসল বয়ঃসীমা ২,৮০০ + ৫০০ = ৩,৩০০ খ্রিঃ পূঃ বলে গণ্য করাই প্রাচীনত্ব বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ঐতিহাসিক মার্টিমার হুইলার হরপ্পার বয়স ধরেছেন ২,৫০০ খ্রিঃ পূঃ। হরপ্পা ও চান-হু-দারোর ইগল ছাপযুক্ত শিলমোহর সুসা নগরীতে মিলেছে। তবে স্যার জন মার্শালের মতে, হরপ্পা সভ্যতার সময়সীমা হল ৩,২৫০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ২,৭৫০ খ্রিঃ পূঃ-এর মধ্যে।
হরপ্পা সভ্যতা সিন্ধুর নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল। এই নদী উপত্যকাটি লম্বায় প্রায় ১,৩৫০ কি.মি. এবং চওড়ায় ১,০৫০ কি.মি.। সিন্ধু ও তার শাখানদীগুলি, বিশেষত মরুভূমির বুকে হারিয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীর পূর্বপ্রান্ত বরাবর হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠায় বিস্তৃতি উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বদিকের প্রায় ১২.৯৯,৬০০ বর্গ কি.মি. ত্রিভুজাকৃতির এলাকায় এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। মূলকেন্দ্র মহেন-জো-দারো (বা মৃতের স্তূপ) ও হরপ্পার দূরত্ব ৬৪০ কি.মি.। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এই সভ্যতা পূর্ব-পশ্চিমে ১,১০০ কি.মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ১,৬০০ কি.মি. বিস্তৃত। হরপ্পা সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। ঐতিহাসিক এ. এল. ব্যাশানের মতে, মধ্যবিও বণিকগন এই নগরিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল।
হরপ্পা সভ্যতার নির্মাতা কারা তা নিয়ে ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা এক মতে আসতে পারেননি। অনেকের ধারণা বেলুচিস্তানের মেহেরগড় সভ্যতার নির্মাতা যারা তারাই হরপ্পা সভ্যতার নির্মাতা। পণ্ডিত মাটিমার হুইলার, গর্ডন চাইল্ড প্রমুখ মনে করেন মেসোপটেমিয়া বা সুমেরের নগর নির্মাতারাই হরপ্পা সভ্যতা গড়ে তোলেন। কিন্তু এই বিদেশী প্রভাবকে অনেকে মানতে রাজি নন। ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রাক্-বৈদিক যুগের দ্রাবিড়-ভাষী মানুষ হরপ্পার নির্মাতা। শেষের মতকে অনেকে স্বীকার করেছেন।
• নগর পরিকল্পনা : সিন্ধু সভ্যতা একটি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, হরপ্পা এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। কারণ এবং পথঘাট, গৃহনির্মাণ কৌশল, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার, শস্যাগার ইত্যাদির গঠনশৈলী থেকে জানা যায়, হরপ্পার নগর পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে প্রাচীন মানুষের দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও উন্নত রুচিবোধের পরিচয়। মনে হয় হরপ্পা সভ্যতা ইতিহাসের এক বিপন্ন বিস্ময়। সভ্যতার চরম উৎকর্য হরপ্পাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। তাই সিন্ধু সভ্যতাকে 'হরপ্পা সভ্যতা' বলা হয়।
হরপ্পা সভ্যতার রাজপথগুলি ছিল সোজা, প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। মহেন-জো-দারোর প্রধান রাজপথটি ৩৪ ফুট চওড়া। ৩ ফুট থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া রাস্তা আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁকা রাস্তা ছিল না। রাস্তার দুধারে বাঁধানো ফুটপাথ, ল্যাম্প- পোস্টের আলো ও ডাস্টবিন ছিল। রাস্তা তৈরি করতে চুন, সুরকি জাতীয় জিনিস ও পাথর ব্যবহৃত হত।
* ঘরবাড়ি ছিল দু-ধরনের সাধারণ মানুষের বাসগৃহ ও অভিজাতদের বাসগৃহ। কোথাও দু-তিন তলার বেশি উঁচু বাড়ি পাওয়া যায়নি। বড়ো মাপের একটি হলঘর' (Assembly Hall) খননকার্যের থেকে পাওয়া গেছে। বাড়িগুলি পাথরের পরিবর্তে ইট ছিল। “গ্রিড পদ্ধতিতে শহরের বাড়িঘরগুলি তৈরি হত। প্রতি বাড়ি প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। জানালা রাখা হত না। দু-একটি জানালা ও দরজা থাকলেও তা গলির পথের দিকেই ছিল।
শস্যাগার স্থাপন হরপ্পার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। (হরপ্পা নগরীতে ১২টি শস্যাগার যুক্তভাবে তৈরি হয়েছিল। যার আয়তন ৮৩৮-১০২৫ ঘন মিটার। প্রধান শস্যাগারটি ১৫০ x ২০০ বর্গফুট উঁচু একটি মঞ্চর উপর অবস্থিত ছিল। কালিবঙ্গানে একটি শস্যাগার পাওয়া গেছে। হরপ্পার শস্যাগারের সংলগ্ন শ্রমিকদের 'ব্যারাক'-এর নিদর্শন মিলেছে। ঐতিহাসিক এ. এল. ব্যাশাম একে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করেছেন।
* সমাজে তিন শ্রেণির মানুষ ছিল-
(ক) শাসকশ্রেণি ,
(খ) ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণি এবং
(গ) শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ।
সিন্ধুর সমাজ রক্ষণশীল হলেও কেউ কাউকে বঞ্চিত করেনি। সেদিক থেকে সাম্যবাদের ধারণা সম্পর্কে তাদের যে পরিষ্কার ধারণা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সিন্ধুর অধিবাসীরা নিরামিষ ও আমিষ উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ করত। গম ও যব তাদের প্রধান খাদ্যশস্য হলেও খেজুর, বার্লি, চাল নানা প্রকার শাকসবজি, ফলমূল, ঘি-দুধ ইত্যাদিকে তারা খাদ্য তালিকায় স্থান দিয়েছিল সাধারণত সুতি ও পশমের বস্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল। নিম্নাকা ও ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢাকার জন্য তারা দু-খণ্ড বস্ত্র পরিধান করত। নারী- পুরুষ উভয়েই মাথায় লম্বা চুল রাখত। তবে মেয়েরা সুসজ্জিত কবরীবন্ধন করে আধুনিককালের মতো মাথার কাঁটা ব্যবহার করত। তাছাড়া চোখে কাজল ব্যবহারও এই যুগের মেয়েদের অজানা ছিল না। ড. ডি. ডি. কোশাম্বীর মতে, এই অঞ্চলের কৃষকরা তখন লাওলের ব্যবহার জানত না। নদীতে জল সঞিত নর্তকী মূর্তি থাকলেও সেচের দ্বারা কৃষির প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ ছিল না। তথাপি খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হত। বিভিন্ন কৃষিপণ্যের মধ্যে গম, যব, বার্লি, রাই, তিল, তুলা, সরিষা, শাকসবজি, ধান ইত্যাদি হল প্রধান।
* পশুপালন : কৃষির ন্যায় পশু- পালনও বহু মানুষের জীবিকা ছিল। খাদের প্রয়োজনে পালিত পশুর মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি ছিল। পরিবহনের জন্য পোষ মানানো হয়েছিল গাধা, উট, হাতি, ষাঁড়, বলদ ইত্যাদি পশু।
* হরপ্পা সভ্যতার আর্থিক সমৃদ্ধির আর একটি দিক হল, ব্যাবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও যুক্ত বণিকদের বলা হত 'পণি। জলপথ ও স্থলপথে অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দুইই চলত। হরপ্পার বণিকদের সঙ্গে মিশর, সুমের, ব্যাবিলন, পারস্য, বেলুচিস্তান, আফগানিস্থান, রাজস্থান, দক্ষিণ ভারতের মহীশুর প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। ভারতের প্রাচীনতম বন্দর লোথালের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সমুদ্র বাণিজ্য চলত। মুদ্রার অভাবে মূলত পণ্য বিনিময়ের দ্বারাই বাণিজ্য হত।
মাতৃরূপিণী শক্তিপূজা, ধরিত্রী পূজা, লিঙ্গপূজা, যোগীরাজ পশুপতি শিবের পূজা ধর্মজীবনের অঙ্গ ছিল। স্যার জন মার্শাল এই পশুপতি শিবকে 'আদি শির' ("Proto Shiva") বলেছেন। তাঁর ভাষায় "The later concept of Shiva.... এছাড়া ষাঁড়, হস্তী, হরিণ, মহিষ, গন্ডার, বাঘ ও সাপকে পুজো করা হত। একইভাবে পিপ্পলি বৃক্ষ (বটগাছ), আগুন ও নদীকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হত। সিন্ধুর মানুষ সূর্য পূজার প্রতীক রূপে “স্বস্তিক চিহ্ন” (Si) ব্যবহার করত।
মহেন-জো-দারোতে খননকার্য চালিয়ে একটি বিশাল স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বাইরের পরিমাপ ১৮০ ফুট x ১০৮ ফুট। এর ভিতরের পরিমাপ হল ৩১ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর।
■ হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য।
- (১) সমসাময়িক যুগে মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে যে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল। প্যাপিরাস, পোড়ামাটি ও পাথরের বুকে তার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা সেগুলি পাঠ করে তার ইতিহাস রচনা করেছেন। সিন্ধু উপত্যকার সিলমোহর ও বিভিন্ন পাত্রের প্রাগৈতিহাসিক ও তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা গায়ে বেশ কিছু লিপি খোদাই করা আছে। সেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পণ্ডিতরা তাই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যথা—ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং মানুষ, পশুপক্ষী ও দেবদেবীর মূর্তির ওপর ভিত্তি করে হরপ্পা সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই কারণে এই সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলা হয়।
- (২) এই যুগে মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না। এ সময় পাথরের ব্যবহার কমে আসতে থাকে এবং ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। পাথরের হাতিয়ার ও সরঞ্জামের পাশাপাশি ব্রোঞ্জ ও তামার ব্যবহার চলতে থাকে।
- (৩) সিন্ধুনদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠে। কেবলমাত্র সিন্ধু উপত্যকাই নয়——সিন্ধুতট অতিক্রম করে পাল্লাব, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদা উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ স্থানে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপতাকা এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকরাণ মুক্ত-উপকূল থেকে উত্তর-পূর্বে মীরাট পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল। পুরো এলাকাটি ছিল একটি ত্রিভুজের মত এবং এর আয়তন হল প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে এলাকাটি প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বড়।
- (৪) বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতার প্রায় ২০০টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র শহর নামের অধিকারী। নগর-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো। এই নগরী- দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার। এছাড়া, চাহুদড়ো, কোটদিজি, রূপার, আলমগীরপুর, লোখাল, রংপুর, রোজদি, সুরকোটরা, কালিবঙ্গান, বনওয়ালি প্রভৃতি স্থানে উন্নত নগর জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।
- (৫) প্রায় তের লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকাটিতে সর্বত্রই একই ধরনের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতার সর্বত্রই একই ধরনের নগরীগুলির অবস্থানগত দূরত্ব যথেষ্ট, কিন্তু এ সত্বেও নগরীগুলির পরিকল্পনা, গঠন-রীতি ও জীবনযাত্রার উপকরণে যথেষ্ট মিল আছে। সুতরাং একটি নগর সম্পর্কে আলোচনা করলেই অন্যান্য নগর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায়। এখানে মহেঞ্জোদরো শহরটি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।
নগর পরিকল্পনা : মহেঞ্জোদরো শহরটির পশ্চিমদিকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশালায়তন টিপির ওপর একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে হয়, সেগুলি শাসকদের বাসস্থান। দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। তার আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। এর চারদিক ঘিরে আছে ৮ ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল। এর কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয়, যা ৩৯ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর। জলাশয়ের নোংরা জল নিকাশ ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল। ঋতুভেদে জল গরম বা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থার ছিল। এরই পাশে ছিল একটি কেন্দ্রীয় শস্যাগার। এর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট এবং প্রস্থে ১৫০ ফুট। ডঃ এ. এল. ব্যাসাম এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্যার মাটিমার হুইলার বলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে এ ধরনের বিশাল শস্যাগার পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায়নি। এই অঞ্চলের অন্যান্য বড় বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষকে পণ্ডিতরা সভাকক্ষ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমিতিগৃহ বলে চিহ্নিত করেছেন।
দুর্গ অঞ্চলের এই উঁচু ঢিপির পূর্বদিকে নিচু জমিতে মূল শহরটি গড়ে উঠেছে। নগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে সমান্তরালভাবে কয়েকটি রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাগুলি ন'ফুট থেকে ত্রিশ ফুট চওড়া। এই রাস্তাগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য গলি পথ। গলিগুলির দু'পাশে নাগরিকদের ঘরবাড়ি। বাড়িগুলি পোড়া-ইটের তৈরি এবং অনেক বাড়িই দোতলা বা তিন-তলা। প্রত্যেক বাড়িতে প্রশস্ত উঠোন, স্নানাগার, কুয়ো ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। অনেক বাড়িতে আবার 'সোকপিট' ছিল। বাড়ির নোংরা জল নর্দমা দিয়ে এসে রাস্তার ঢাকা দেওয়া বাঁধানো। নর্দমায় পড়ত। নর্দমাগুলি পরিষ্কারের জন্য ইট দিয়ে তৈরি ঢাকা ম্যানহোল'-এর ব্যবস্থা ছিল। ডঃ এ. এল. ব্যাসাম বলেন যে, রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোন প্রাচীন সভ্যতায় এত পরিণত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাঁধানো ডাস্টবিন ' ছিল।
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন :
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শহরের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ দেখে মনে হয় যে, সমাজে শাসক সম্প্রদায়, ধনী ও ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরেরা বাস করত। দুর্গ অঞ্চলেই ছিল শাসকদের বাসগৃহ। শহরের দ্বিতল ত্রিতল গৃহগুলিতে বাস করত ধনী ও মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় এবং খুপরি জাতীয় ঘরগুলি ছিল শ্রমজীবী দরিদ্রদের বাসস্থান। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, এই শহরগুলিতে ক্রীতদাসরাও ছিল। তারা দীনহীন কুটিরে বাস করত এবং ফসল মাড়াই, ভারী বোঝা বহন, শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা উভয় শহরেরই উত্তর- পূর্ব কোণ, দুর্গপ্রাকার ও শস্যাগারের কাছাকাছি স্থানসমূহে খুপরি-জাতীয় ঘরগুলির অস্তিত্ব শহরে ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে। কালিবঙ্গান ও লোথালে এ ধরনের কোন খুপরি মেলেনি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই শহরদু টির শাসকরা হরপ্পা-মহেঞ্জোদরোর শাসকবর্গ অপেক্ষা উদার ছিলেন।
এই সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও তার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। এখানকার অধিবাসীরা গম, যব, বার্লি, ধান, ফলমূল, তিল, মটর, রাই খেজুর, বাদাম, দুধ, মুরগি ও পশুর মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। বেলুচিস্তানে মাটির নিচে অতি গভীরে ঘোড়া চিহ্ন মিললেও ঘোড়া কিন্ত সেদিন পোষ মানেনি। সিন্ধুবাসী সুতি পোশাক ও পশমের বস্ত্র ব্যবহার করত। তারা দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও নিম্নাঙ্গ দুই কাপড়ের দ্বারা আবৃত করত। নারী-পুরুষ উভয়েই লম্বা চুল রাখত। মেয়েরা সোনা ও রুপোর ফিতে দিয়ে নানা ধরনের খোঁপা করত। তারা নানা ধরনের সুগন্ধী, প্রসাধন সামগ্রী এবং তামা, ও ব্রোঞ্জের রূপা ও পাথরের তৈরি নানা ধরনের ও নানা আকারের হার, কানের দুল, চুড়ি, মল, কোমরবন্ধ ও মালা ব্যবহার করত। সিন্ধুবাসীরা বিভিন্ন শিল্পকর্মে দক্ষ ছিল। এখানে পাথর, মাটি, তামা, সিসা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র ও গৃহস্থালির নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে। তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরি গৃহস্থালির সংগ্রাম, অসু- কুঠার, বর্শা, তির, ধনুক, মুষল প্রভৃতি অস্ত্রও তারা ব্যবহার করত। এ শত্রু এবং বিভিন্ন শিল্প প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সিন্ধু উপত্যকায় ঢাল, বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের কোন সন্ধান মেলেনি। বস্ত্রবয়ন, হাতির দাঁত, পাথরের কাজ এবং মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ উন্নতি করে। শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরি নানা জীবজন্তুর মূর্তি ও চীনামাটির পাত্রে নানা অলংকরণ তাদের শিল্পদক্ষতার পরিচয় বহন করে। নৃত্য-গীত, পশুশিকার, পাশাখেলা ও রথচালনা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের উপায়। এ ছাড়া, এখানে অলংকার-শিল্পী, ইট-শিল্পী, ছুতোর মিস্ত্রিরাও বাস করত। ভারত ও ভারতের বাইরে নানা স্থানের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দাক্ষিণাত্য থেকে দামি পাথর, রাজপুতনা থেকে তামা, কাথিয়াবাড় থেকে শব্দ। এবং বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান থেকে সোনা, রূপা, সিসা ও টিন আমদানি হত। সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি হত তুলো, সূতিবস্ত্র, তামা, হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র। সুতিবস্ত্র ও তুলো ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ক্রিট, সুমের ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। যানবাহন হিসেবে সিন্ধুবাসী উট, গাধা, দু-চাকা বিশিষ্ট গরু ও ষাঁড়ের গাড়ি ব্যবহার করত। তাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রাও প্রচলিত ছিল। লোখাল ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর।
সিন্ধু উপত্যকায় পোড়ামাটি, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর সিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই ঐসব সিলমোহর ও লিপি সিলমোহর তৈরি হয়েছিল। এইসব সিলমোহরে বিভিন্ন জীবজন্তু ও জলযানের চিত্র অঙ্কিত আছে। এ থেকে মনে হয় যে, এইসব জীবজন্তু ও জলযানগুলি তাদের সুপরিচিত ছিল। আবার কিছু সিলমোহরে চিত্রলিপি উৎকীর্ণ আছে। এগুলিই হল, 'সিন্ধু লিপি' বা 'হরমা লিপি। সিন্ধু লিপির পক্ষে চিত্রলিপির স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। এইসব লিপি এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি—তবে একথা ঠিক যে, এই লিপি ডানদিক থেকে বাঁদিকে পড়া হত।
হরপ্পা সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকাকে অনেকে মন্দির বলে মনে করেন। সেগুলি মন্দির হলেও পুজোর রীতি প্রচলিত ছিল না। সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি মিলেছে। পণ্ডিতরা এই মূর্তিগুলিকে মাতৃমূর্তি বা ভূমাতৃকা বলেছেন। একটি সিলে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, মোষ ও হরিণ—এই পাঁচটি পশু দ্বারা পরিবৃত ও ত্রিমুখবিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন এক যোগীমূর্তি দেখা যায়। মূর্তিটির মাথায় দুটি শিং আছে। অনেকের ধারণায় এটি শিব-মূর্তি। অধ্যাপক ব্যাসাম এটিকে 'আদি শিব' বলে অভিহিত করেছেন কারণ শিবের বাহন ষাঁড়, কিন্তু এই মূর্তিতে ষাঁড় নেই। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে বৃক্ষ, আগুন, জল, সাপ বিভিন্ন জীবজন্ত, লিঙ্গ ও যোনি পূজা এবং সম্ভবত সূর্য উপাসনাও প্রচলিত ছিল। কয়েকটি সিলে সূর্যের প্রতীক স্বস্তিকা ও চক্র পাওয়া গেছে। একটি সিলে একটি অর্ধ- নর অর্থ-বৃষ মূর্তিকে একটি বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে। এই মূর্তিটি হল সুমেরের গিলগমেশ নামক বীরের সাহায্যকারী অর্ধ-নর অর্ধ-বৃত্ত আকৃতি বিশিষ্ট ‘ইঅবনি' মূর্তির অনুরূপ। সিন্ধু উপত্যকার এই মূর্তি সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার ঐক্য প্রমাণ করে। এছাড়া, এই মূর্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপু নিধনকারী নৃসিংহ মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় যে, সিন্ধুবাসীরা এই নর-বুধ মূর্তিকে দেবতা- জ্ঞানে পূজা করত।
হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড-এর মতে হরপ্পার বণিকরা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উপকূলে অবস্থিত বাজারে যেত। পশ্চিম এশিয়ার আক্কাদ নামক স্থানে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকার বেশ কিছু সিল সুমেরে এবং সুমেরেরও কিছু সিল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে। এই তিনটি অঞ্চলে যে-সব সিল, পোড়ামাটির বেহির্বিশ্বের সঙ্গে কাজ ও ধাতুনির্মিত তৈজসপত্রাদি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। উন্নত জীবনযাত্রা, নগর জীবন, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, চিত্রলিপি, মাতৃদেবীর উপাসনা, কেশবিন্যাস পদ্ধতি এবং তিনটি অঞ্চলেই পারস্পরিক স্থানের দ্রব্যাদির অবস্থিতি তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ
আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ধ্বংসের কারণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।
- (ক) অনেকে মনে করেন যে, পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হত এবং এই অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। কালক্রমে এই অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পায় ও ভূগর্ভস্থ লবণ ওপরে উঠে এসে স্থানটিকে মরুভূমিতে পরিণত করে।
- (খ) স্যার মাটিমার হুইলার ও অনেকে মনে করেন যে, পোড়া ইটের ব্যাপক ব্যবহার ও অন্যান্য কারণে এখানে ব্যাপকভাবে বৃক্ষচ্ছেদন শুরু হয় এবং অঞ্চলটি বনশূন্য হয়ে পড়ে। এর ফলে বৃষ্টিপাতের অভাবে এই অঞ্চলের কৃষিকার্য বিপর্যন্ত হয়ে যায় এবং জনসাধারণ স্থানত্যাগে বাধা হয়।
- (গ) ডঃ এম. আর. সাহানী ও অনেকে বলেন যে, বারংবার সিন্ধুনদের বন্যার ফলে সভ্যতাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহেঞ্জোদরো নগরীটি যে একাধিকবার বন্যা কবলিত হয়েছিল এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।
- (ঘ) এই সভ্যতাটি ধ্বংসের জন্য ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড—এমনকি সিন্ধুনদের গতিপথ পরিবর্তনকেও দায়ী করা হয়েছে। (ঙ) এই সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে আবার নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা ও নাগরিক আদর্শের অবনতির কথা বলেন। মহেঞ্জোদরোর নিচের স্তরে নগর পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যত সুন্দর, পরের স্তরগুলিতে তা নয়। ওপরের স্তরগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, রাস্তা দখল করে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, নর্দমা বুজে আসছে, গলির মধ্যে ইটের পাঁজা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এইভাবে ঐ সভ্যতা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- (চ) বলা হয় যে, বিদেশি আর্যদের আক্রমণেই এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মহেঞ্জোদারোতে প্রকাশ্য রাস্তায়, কুয়োর ধারে, বাড়ির মধ্যে পলায়নপর বহু মানুষের স্তূপীকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এই মৃতদেহগুলি প্রকাশ্য স্থানে পড়ে আছে, কোন সংকার হয়নি এবং তাদের মাথার পেছনে ধারাল অস্ত্রের আঘাত। বলা হয় যে, বিদেশিদের অতর্কিত আক্রমণের ফলেই এই অবস্থা হয়েছে এবং দেবরাজ ইন্দ্রই এই সভ্যতার ধ্বংসকারী। ঋগ্বেদে তাঁকে 'পুরন্দর' বা 'দুর্গ ধ্বংসকারী' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কোন কারণই ত্রুটিমুক্ত নয়। আপাতত মনে করা যেতে পারে যে, আর্য আক্রমণই সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ—যদিও সকলে এ সম্পর্কে একমত নন।
→ গুরুত্ব ও অভিনবত্ব : সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে, ভারতীয় সভ্যতা সুমের, আক্কাদ , মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার সমসাময়িক। প্রাচীন বিশ্বে আয়তন ও ব্যাপ্তির দিক থেকে হরপ্পা সভ্যতা অদ্বিতীয়। পোড়া ইট, ডাস্টবিন, সোকপিট পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহারে হরপ্পা সভ্যতা অতুলনীয়। ধানের চাষ ও মুরগী পালনের সুত্রপাত সিন্ধু উপত্যকাতেই। উৎকৃষ্ট মানের তুলোর চাষ ও সুতিবস্ত্র উৎপাদনে সিন্ধুবাসীদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।
■ স্মরণীয় কালপঞ্জি
আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৫০০০০০ – ভারতে মনুষ্য বসতির সূচনা।
5000000 – ৮০০০ ভারতে প্রাচীন প্রস্তর যুগ।
৮000 --8000 ভারতে মধ্যপ্রস্তর যুগ।
৬০০০— ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা।
৩০০০-১৫০০ – সিন্ধু সভ্যতা।



.png)