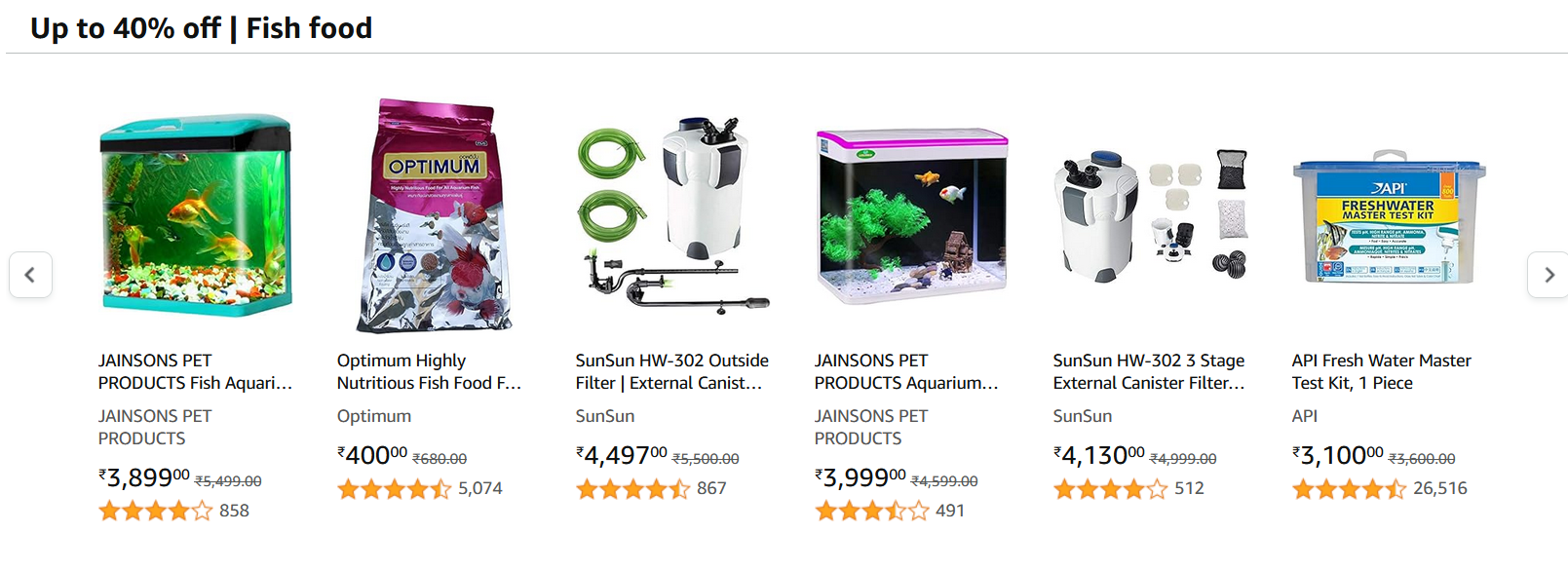|
| বৈদিক সভ্যতা |
বৈদিক সভ্যতা
বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত মনে করা হত বৈদিক সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা ,যার উৎস ঋগ্বেদ। এমনকি ১৯২০-র দশকে হরপ্পা সভ্যতা (সেই সময় সিন্ধু সভ্যতা নামে প্রচলিত)-র আবিষ্কারের পরেও পণ্ডিতমহলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে হরপ্পা সভ্যতা আসলে আর্য সভ্যতারই অংশবিশেষ। আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও ভারতের কিছু প্রান্তে আর্য সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার আভিন্নতার বিষয়টি সমৃদ্ধতর করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালোরে মিথিক সোসাইটি আয়োজিত “আর্য সমস্যা" শীর্ষক আলোচনাচক্রে এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এককথায়, মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে হরপ্পা ও আর্য সভ্যতার অভিন্নতার বিয়েটি তার সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে প্রাচীনতম না হলেও ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসে আর্য সংস্কৃতির স্থান অনন্য। ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদের জন্য আমরা আর্যদের কাছে চিরঋণী। কেননা, চারটি বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য থেকেই কেবল সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি তথা জীবনযাত্রার সামগ্রিক দিক সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকি। সর্বোপরি, আমাদের বর্তমান বহুমুখী জীবনযাত্রায় আর্য সংস্ক্রৃতির প্রভাব আপরিসিম।
আর্য তথা বৈদিক সভ্যতাকে জানতে বেদ হল অন্যতম প্রধান আকর গ্রন্থ। হিন্দুদের কাছে এই বেদ একটি পবিত্র গ্রন্থ। বেদ চার প্রকার — ঋক্, সাম, যজু, ও অথর্ব। প্রতিটি বেদের আবার চারটি বিভাগ আছে—সংহিতা, ব্রাক্ষ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।
এই সাহিত্যকে সংক্ষেপে সম্যকভাবে বুঝতে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাকে ‘সূত্র সাহিত্য' বলা হয়। এই সূত্র সাহিত্য বেদাঙ্গ এবং ষড়দর্শন নিয়েই গঠিত।
সামাজিক জীবন : ‘পরিবার' (Family) বা 'কুল' হল আর্য সমাজের মূল ভিত্তি। তবে ঋগবেদে ‘কুল’ অপেক্ষা ‘গৃহ' কথাটির বেশি ব্যবহার রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক' (Patriarchal) একান্নবর্তী পরিবার আর্য পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য বেশি ছিল। তাই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধান ব্যক্তিকে বলা হত 'কর্তা' বা 'কুলপতি’ বা ‘গৃহকত্’। যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারে কর্তার আদেশকে আইন মনে করে সবাই তা মেনে চলত।
ঋগ্বৈদিক আর্যদের সমাজের চারটি বর্ণ হল –
(১) ব্রাক্ষ্মণ (পুরোহিত), (২) ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা বা দেশরক্ষী), (৩) বৈশ্য (বণিক ও কৃষক) এবং (৪) শূদ্র (পশুপালক)।
এই সময় ‘জাতি' ও 'বর্ণ' শব্দদুটির আলাদা অর্থ ছিল। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ঋগ্বৈদিক যুগের একেবারে শেষের দিকে আর্য-সমাজে চতুরাশ্রম প্রথা গড়ে ওঠে। এই প্রথা অনুসারে একমাত্র শূদ্র ছাড়া ব্রাক্ষ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সমগ্র জীবন চারটি আশ্রম বা পর্বে বিভক্ত ছিল। এগুলি হল ব্রক্ষ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম।
ঋগ্বৈদিক আর্য-সমাজ পুরুষ শাসিত হলেও নারীদের যথেষ্ট সম্মান, স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। এই যুগে নারীদের উপনয়ন বা পৈতা হত। সমাজে বিষপলা ও মুদ্গলানীর মতো রণকুশলী নারী যেমন ছিল, তেমনি বিদুষী রমণীদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, মমতা, অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা ও বিশাখার নাম বিশেষ স্মরণীয়।
অর্থনৈতিক জীবন : প্রথমে নদী উপত্যকার উর্বর পলি মৃত্তিকা অঞ্চলে আর্যরা বসবাস গড়ে তোলায়, স্বভাবতই কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে। ব্যাশামের মতে তখন জমির ব্যক্তিমালিকানা ছিল না। জমির মালিকানা থাকত এক-একজন 'গ্রামণী' বা গ্রাম প্রধানের হাতে। কিন্তু ঐতিহাসিক ড. এইচ. সি. রায়চৌধুরীর মতে, চারণভূমি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হলেও বাস্তু ও আবাদি জমির ব্যক্তিমালিকানা ছিল। কৃষির মতো পশুপালন ছিল আর একটি প্রধান জীবিকা। গৃহপালিত প্রধান পশু গোরুকে ‘গোধন', 'গারিস্টি' (যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ হত) ও 'অগ্ন্য' (যা হত্যা করা নিষেধ) বলা হয়েছে। গোরু ছিল মূল্যবান সম্পদ ও সম্পত্তির মাপকাঠি।
ঋগ্বৈদিক যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে দু-ধরনের স্বর্ণখণ্ড ‘মনা” ও ‘নিষ্ক’-এর প্রচলন থাকলেও উন্নত মুদ্রাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাই ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য পণ্য 'বিনিময় প্রথা' (barter system) গড়ে ওঠে। তবে গোরু ছিল এই বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম।
বাণিজ্যের পাশাপাশি কিছু ছোটোখাটো শিল্পের কথা ঋগবেদ থেকে জানা যায়। তবে বড়ো শিল্পের পরিবর্তে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পই ছিল বেশি। এইসব শিল্পের মধ্যে লৌহশিল্প, স্বর্ণশিল্প, সুতিবস্ত্র শিল্প, পশম শিল্প, রজ্জুনির্মাণ শিল্প, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প, নৌকা ও রথ নির্মাণ শিল্প প্রধান।
রাজনৈতিক জীবন : কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন 'বিশ' বা 'জন', যার প্রধান শাসনকর্তাকে বলা হত বিশপতি' বা 'রাজন' বা 'রাজা'। এইভাবে রাজপদের উত্থানের মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ধারণা বিকশিত হয়। সার্বভৌম শক্তির প্রতীক রূপে রাজা 'অশ্বমেধ', 'বাজপেয়', 'রাজসূয়' প্রভৃতি যজ্ঞ শেষে ‘সম্রাট', ‘একরাট', 'বিরাট', 'রাজচক্রবর্তী', 'রাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। রাজার স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সভা ও সমিতির মতো দুটি জনপ্রতিনিধিমূলক সংস্থার উন্মেষ ঘটে। আর. সি. মজুমদার একে 'Popular assembly' বলে উল্লেখ করেছেন। লুডউইগের মতে, উপজাতির বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধানদের নিয়ে নির্বাচিত হত 'সভা' বা পরিষদ। আর সমিতি হল, সর্বসাধারণের পরিষদ'। সভার চেয়ে সমিতি অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। কারণ সমিতি রাজার কর্তব্য নির্ধারণ করে তাঁকে প্রজাতন্ত্রের দিকে চালিত করতে পারত।
ধর্মীয় জীবন : আর্যরা বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। তাই বহু দেবদেবীর উপাসনা আর্যদের ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার সেই জন্য বৈদিক যুগের ধর্মে 'বহু ঈশ্বরবাদের' অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আগুনের দেবতা 'অগ্নি'র উদ্দেশ্যে ২০০টি স্তোত্র রচিত হয়েছে। এছাড়া বাতাসের ‘মরুত’, জলের দেবতা 'বরুণ', মৃত্যুর দেবতা 'যমরাজ' প্রভৃতির উল্লেখ ঋগবেদে আছে। তবে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নাম ঋগবেদে না থাকলেও প্রজাপতি বিধাতৃ ও হিরণ্যগর্ভের নাম আছে। এই যুগের বিভিন্ন দেবীর মধ্যে 'ঊষা', 'অদিতি', 'অরুন্ধতী', 'সরস্বতী', 'সাবিত্রী' ইত্যাদি প্রধান।
হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক সম্পর্ক (Comparison and relations between the Harappan Civilisation and Vedic Civilisation):
- হরপ্পার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য চোখে পড়ে।
- (১) হরপ্পা সভ্যতা ছিল প্রাচীনতম (৩৫০০ খ্রিঃ পূঃ) কিন্তু বৈদিক সভ্যতা তুলনামূলক বিচারে নবীন (১৫০০ খ্রিঃ পূঃ)। (২) হরপ্পা সভ্যতা তাম্র-ব্রোঞ্জ বা নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতা। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা লৌহযুগের সভ্যতা।
- (৩) হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। কিন্তু আর্য সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা। কারণ সিন্ধু সভ্যতার মতো ইটের তৈরি উন্নত বাড়ি আর্যদের ছিল না।
- (৪) সিন্ধু লিপি ও ভাষা দুর্বোধ। এর পাঠোদ্ধার আজও হয়নি। কিন্তু আর্যসভ্যতায় আর্যদের ভাষা সংস্কৃত ও তা অনেকের বোধগম্য।
- (৫) সিন্ধু যুগে ঘোড়ার ব্যবহার ছিল না। আর্যরা ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার করত।
- (৬) সিন্ধু যুগে মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু আর্যরা মন্দির নির্মাণ করে মূর্তিপূজা শুরু করেছিল।
- (৭) হরপ্পার মানুষ সংস্কৃতি সচেতন ছিল। কিন্তু বৈদিক আর্যরা অর্ধযাযাবর বলে সংস্কৃতিকে ততটা সমাদর করেনি।
- (৮) হরপ্পার মানুষ সাধারণত মৃতদেহ কবর দিত। কিন্তু আর্যরা মৃতদেহ দাহ করত।
- (৯) হরপ্পা যুগে নারীদেবতার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আর্যযুগে সেই প্রাধান্য ততটা ছিল না।



.png)