ধর্মীয় প্রতিবাদ আন্দোলন
ধর্মবিপ্লবের যুগ : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতে ধর্মীয় আলোড়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারতে ধর্মীয় আলোড়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত।বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে এই যুগে ভারতে তেষট্টি-টি প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান ঘটে। জৈনগ্রন্থে এর সংখ্যা আরও বেশি বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই সব ধর্মমতের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
→ ধর্মীয় কারণ : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বহু পূর্বেই বৈদিক ধর্ম তার সরলতা ও পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ, পশুবলি, দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান- সর্বস্বতা, ধর্মীয় কার্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অপরিহার্যতা এবং এর ফলে সমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি ও ক্রমবর্ধমান দক্ষিণার চাহিদা প্রভৃতির ফলে ধর্ম প্রাণহীন হয়ে পড়ে এবং সমাজে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বৈদিক সমাজের চতুরাশ্রম প্রথার ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্যাশ্রমে মানুষের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের আদর্শ সবার কাছে গ্রহণীয় ছিল না। অপরদিকে, উপনিষদে যাগযজ্ঞ অপেক্ষা আত্মার মুক্তি, কর্মফল ও স্বাধীন চিন্তার আদর্শ প্রচারিত হতে থাকে। উপনিষদের ঋষিরা যাগযজ্ঞ ও দেবদেবীর উপাসনার নিন্দা করতে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, মানুষের জীবন জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বাঁধা এবং কর্মফলই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানসর্বস্ব যাগযজ্ঞ নয়—সৎ কর্ম ও শুদ্ধ জীবনচর্যাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। ধর্মীয়কার্যে পুরোহিতও অপরিহার্য নয়—মানুষই নিজের ভাগ্য নিয়ামক। বলা বাহুল্য, এই সব কারণে সমাজে নতুন ধর্মীয় চিন্তা ও আদর্শের পথ প্রস্তুত হয় এবং সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মে আস্থাহীন হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ওল্ডেনবার্গ বলেন যে, “বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর পূর্বেই ভারতীয় চিন্তাজগতে এমন এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, যা বৌদ্ধধর্মের পথ প্রস্তুত করে।
→ সামাজিক কারণ : বৈদিক সমাজের মধ্যেই ধর্মবিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। বৈদিক সমাজ স্পষ্টতই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁরা বহু সুযোগ-সুবিধা পেতেন। তাঁরা রাজার কাছ থেকে নানা উপহার পেতেন, তাঁদের কোন কর দিতে হত না- এমন কি অনেক সময় তাঁরা শাস্তিরও ঊর্ধ্বে ছিলেন। ব্রাহ্মণদের পরেই ছিল ক্ষত্রিয়দের স্থান। তাঁরা ছিলেন যোদ্ধা ও শাসকশ্রেণীর মানুষ। তাঁরা যুদ্ধ করতেন, রাজকার্য পরিচালনা, করতেন ও রাজস্ব আদায় করতেন। এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও বৈশ্যদের মর্যাদা হ্রাস পায় এবং অনেক সময় তাদের শুদ্রদের সঙ্গে এক করে দেখা হত। শুদ্রদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা শোচনীয়—তারা ক্রীতদাস ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না এবং বয়ক্ষেত্রে তাদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হত। স্বাভাবিকভাবেই এই বর্ণবিভক্ত সমাজে কোন শান্তি ছিল না। সমাজ ও ধর্মে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্য রাজনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী ক্ষত্রিয়দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এই কারণে পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দু'জনেই ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আচার- অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধ প্রথম সার্থক প্রতিবাদ জানান এবং ভারতীয় জনজীবন ও চিন্তাজগতে নতুন পথের সন্ধান দেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল না। শহরের উৎপত্তির ফলশ্রুতি হিসেবে পতিতাদের আবির্ভাব হয়। ব্রাহ্মণ্য সমাজে পতিতারা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হত। ধর্মশাস্ত্রকার নারী সমাজ নিম্ন-স্তরের মানুষ গৌতম পতিতাদের সম্পর্কে চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে, বুদ্ধদেব নারীসমাজ, পতিতা, দস্যু – সকলকেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত - করেছেন। ধনী ব্যবসায়ী অনাথপিণ্ডক, দস্যু অঙ্গুলিমাল, ব্রাহ্মণ সন্তান সারিপুত্ত ও মোগল্লায়ন এবং পতিতা আম্রপালি — সকলেরই আধ্যাত্মিক পিপাসা তিনি নিবৃত্ত করেন, সামাজিক সাম্যের বাণী প্রচার করে সকলকে তিনি কাছে টেনে নেন এবং মিঠে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার দেন। এর ফলে বৌদ্ধধর্ম সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
→ অর্থনৈতিক কারণ : খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নতুন ধর্মচিন্তার উন্মেষে উত্তর- পূর্ব ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার নতুন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উত্তর - উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বিহারসহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে লোহার হাতিয়ারের সাহায্যে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে এই অঞ্চলে কৃষিকার্য শুরু হয় এবং নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হতে থাকে। কৃষিকার্যের নতুন পদ্ধতি ও উন্নত সারের ব্যবহারের ফলে কৃষির ফলন খুব বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে 'গহপতি’ নতুন কৃষি অর্থনীতি নামে বৈশ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক বিত্তশালী কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য পশুপালন অপরিহার্য। আবার বৈদিক ধর্মরীতিতেও বলিদান ছিল অপরিহার্য ও স্বাভাবিক। একমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞেই ৬০০ ষাঁড় বধ করা হত। বলা বাহুল্য, এসবই কৃষিকার্যের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া, মগধের দক্ষিণ ও পূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষরা খাদ্যের জন্য নিয়মিতভাবে পশু হত্যা করত। সুতরাং নতুন এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে স্থায়ী করার জন্য নির্বিচারে পশুহত্যা বন্ধ করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কৃষিকার্যের আয়তন ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সমাজে উদ্বৃত্ত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে কৌশাম্বী, কোশল, কুশীনগর, বৈশালী, রাজগৃহ, বারাণসী, চিরান্দ প্রভৃতি বহু নতুন নগর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সব নগরগুলিতে অসংখ্য কারিগর ও ব্যবসায়ী বাস করতো। এ সময় তারা নগরের উন্মেষ মুদ্রার ব্যবহার শুরু করেছিল। মুদ্রা ব্যবহারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং কারিগর ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যথেষ্ট ধনবান হয়ে ওঠে। বৈদিক আদর্শে পরিচালিত সমাজে ধনবান বৈশ্যদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তারা এমন এক ধর্মের অন্বেষণে রত ছিল, যে-ধর্ম তাদের সামাজিক মর্যাদা দিতে সক্ষম। বলা বাহুল্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম তাদের এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এই দুই ধর্মমতে জাতিভেদ প্রথার কোন স্থান বৈশ্যদের মর্যাদার প্রশ্ন নেই। এই কারণে বৈশ্যরা এই দুই ধর্মমতের প্রবল সমর্থক ছিল। এছাড়া, প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অভাব ছিল না। যুদ্ধ কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তরায়। এই দুই নতুন ধর্মমত অহিংসার বাণী প্রচার করে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে টাকা ধার দেওয়া, সুদ গ্রহণ করা ও সমুদ্রযাত্রা নিন্দনীয় ও পাপ বলে চিহ্নিত। বিভিন্ন ধর্মসূত্রগুলিতে টাকা ধার দেওয়া ও সুদ গ্রহণের নিন্দা করা হয়েছে। বৌধায়ন তীব্র ভাষায় সমুদ্রযাত্রার নিন্দা করেছেন—অথচ বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলি অপরিহার্য ছিল। বহু 'শ্রেষ্ঠী' বা মহাজন সুদের কারবার করত এবং এটাই ছিল অনেকের জীবিকা। ব্রাহ্মণ্য সমাজ এগুলি ঘৃণার চোখে দেখত এবং সমাজের চোখে এই সব ব্যক্তিরা অপরাধী বলে বিবেচিত হত। স্বাভাবিকভাবেই বৈশ্যরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী হয়ে ওঠে এবং নতুন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতকে সমর্থন করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়।
এই সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা, উন্নত মানের পোশাক, পরিবহন ও বাসস্থান এক শ্রেণীর মানুষের মনে প্রবল বিতৃষ্ণার সঞ্চার ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি বিরূপতা করেছিল। বিলাসময় এই জীবনযাত্রা ত্যাগ করে তারা পূর্বের সহজ, সরল ও তপশ্চর্যাময় জীবনে ফিরে যেতে চাইছিল। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বিলাসিতার দিক পরিহার ও তপস্বীর জীবনযাত্রার কথা প্রচার করে মানুষের এই চাহিদাও মিটিয়েছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সোনা-রূপা স্পর্শের অধিকার ছিল না। শরীর ও আত্মাকে তৃপ্ত রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাঁরা ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে পারতেন। ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, এই যুগে কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে একশ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয় এবং অপর শ্রেণীর অবস্থা ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে আসে। সমাজের বৃহত্তর অংশের লোকরা ছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য- দরিদ্র, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। ধনবণ্টনের কোন ব্যবস্থা বৈদিক সমাজে ছিল না। এর ফলে ধনী যেমন একদিকে ধনীই হত এবং দরিদ্র তেমনি দিন দিন দরিদ্রতর হত। বলা হত –এ সবই কর্মফল। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে এক গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় বুদ্ধদেব দরিদ্র শ্রেণীকেও সহানুভূতি ও অধিকার দান করে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে দরিদ্রই দুর্নীতি ও সব অপরাধের উৎস। তাই অপরাধ দূর করতে হলে উৎপাদন-ব্যবস্থা কৃষক, শ্রমিক ও বণিকদের হাতে দিতে হবে। কেবলমাত্র ইহকালই নয়—তিনি দরিদ্রদের পরকালের কথাও চিন্তা করেন। তিনি বলেন যে, দরিদ্র ব্যক্তি যদি মঠের সন্ন্যাসীকে মুষ্টিভিক্ষা দান করে, তাহলে পরজন্মে সে ধনী হয়ে জন্মাবে। এইভাবে তিনি সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে দেন। এবং ভোগবিলাস ও সন্ন্যাসের মধ্যবর্তী এক মধ্যপন্থা'-র সন্ধান দিয়ে সমাজকে রক্ষা করেন।
জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা ও তার প্রভাব (Main teachings and impact Jainism) :
মহাবীর হলেন ২৪-তম অর্থাৎ সর্বশেষ জৈন তীর্থঙ্কর। অন্যান্য তীর্থঙ্করের নাম জানা না গেলেও ২২-তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ এবং ২৩-তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ- এর নাম জানা গেছে। মহাবীরের জীবনী : ৫৪০ খ্রিঃ পূঃ জৈনদের ২৪-তম বা শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের জন্ম হয় উত্তর বিহারের বৈশালীর কুন্দপুর (বাসাড়) গ্রামে। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ 'জ্ঞাতৃক গোষ্ঠীর' নেতা ছিলেন এবং মাতা লিচ্ছবিরাজ চেতকের ভগ্নী ত্রিশলাদেবী। অল্প বয়সে বর্ধমানের যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় এবং আনজ্জা বা প্রিয়দর্শনা নামে এক কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে। তিনি ত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন।
মোট ১২ বছর নানা স্থানে কঠিন তপশ্চর্যার মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ষড়রিপুকে জয় করেন। এইভাবে প্রথমে তিনি ‘কৈবল্য' বা সর্বজ্ঞ, তারপর 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয় বা ষড়রিপু বিজেতা ও সবশেষে 'মহাবীর' হন। আনুমানিক ৪৬৮ খ্রিঃ পূঃ বিহারের রাজগীরের পাবাপুরীতে ৭২ বছর বয়সে অনশনে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।
মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত চতুর্যামের নীতিগুলি গ্রহণ করেছিলেন। এগুলি হল—– (১)অহিংসা, (২)অচৌর্য, (৩) অপরিগ্রহ বা কোনো বস্তুর প্রতি মায়া বা আসক্তি না রাখা এবং (৪) সত্যবাদিতা বা মিথ্যা কথা না বলা। এই চতুর্যামের সঙ্গে তিনি 'ব্রহ্মচর্য'-এর আদর্শ যুক্ত করে মোট পাঁচটি উপদেশ তাঁর শিষ্যদের পালনের কথা বলেন। একেই বলে ‘পঞ্চ মহাব্রত’।
মহাবীর ও তার অনুগামীরা কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। নিম্নবর্ণের মানুষ ভালো কর্ম করলে উচ্চবর্ণে উত্তরণ ঘটে। কর্মফল ও জন্মান্তরের ফলে সুখ- দুঃখ, উত্থান-পতন চক্রাকারে মানুষের জীবনে আসে। এর থেকে চিরমুক্তি পেতে সৎ জ্ঞান, সৎ আচরণ ও সৎ বিশ্বাস-ই একমাত্র পথ। এই তিনটি নীতিকে বলে “ত্রিরত্ন"। এই ত্রিরত্নকে বলা হয় “সিদ্ধশিল”। কারণ এর দ্বারা মানুষ পরম আনন্দ লাভ করতে পারে বা আত্মার মুক্তি আসে।
জৈনমতে উত্থান-পতন মানুষের জীবনে আসে। মানুষের পতন শুরু হলে তবেই পরিত্রাণকারী হিসাবে তীর্থংকরদের আবির্ভাব হয়। মহাবীরের মতে, মনকে বিশুদ্ধ রাখতে উপবাস, কঠোর কৃচ্ছসাধন, অহিংসা ও কঠোর তপস্যা খুবই প্রয়োজন। ত্যাগ, সংযম, প্রায়শ্চিত্ত ও আসক্তি বর্জন করলে মুক্তি আসে। সরল ও অনাড়ম্বরহীন জৈনধর্মে অহিংসাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ‘সর্বপ্রাণবাদ’ জৈনধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তাই ইট, কাঠ, পাহাড়, পর্বত, নদনদী প্রভৃতির মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্রতম কীট-পতঙ্গ হত্যাও দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর মহাপাপ। তাই একবস্ত্রে দীর্ঘ বারো বছর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভের পর তিনি বাকি ত্রিশ বছর বিবস্ত্র থেকেছিলেন। মহাবীর বলতেন, অপরিগ্রহ অর্থাৎ প্রয়োজনের বেশি সম্পত্তি যেন না রাখা হয়। অমিতব্যয়িতা ও পবিত্রতা রক্ষা মানবজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। পার্শ্বনাথ শ্বেতবস্ত্র পরিধানের অর্থাৎ ‘শ্বেতাম্বর’- এর কথা বললেও মহাবীর বিবস্ত্র থাকার অর্থাৎ ‘দিগম্বর'-এর কথা বলেছিলেন।
• জৈন ধর্মের প্রভাব : ভারত ইতিহাসের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে জৈনধর্মের প্রভাব অপরিসীম। প্রথমত, জৈনরাই প্রথম বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ গড়ে তুলে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ভারতে প্রথম এই জৈনরাই অহিংসার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। বৈদিক ধর্মের আড়ম্বর অপেক্ষা আত্মার উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, আধুনিক পণ্ডিতদের মতে খ্রিঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচশো বছর ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের “উত্থানের যুগ”। এই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পিছনে জৈনধর্মের অবদান অসীম। এই কারণে পশ্চিম ভারতের বড়ো শিল্পপতি ও বণিকদের একটা বিরাট অংশ আজও তাঁদের সাফল্যের জন্য মহাবীরের আশীর্বাদ আছে বলে মনে করেন। চতুর্থত, জৈনরা উচ্চবর্ণের সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা প্রাকৃত ও অর্ধ-মাগধী ভাষায় ধর্মপ্রচার করায় তামিল, তেলেগু, কানাড়ি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাও সমৃদ্ধিশালী হয়ে। উঠেছিল। মধ্যযুগের শুরুতে মেরুতঙ্গ, হেমচন্দ্র প্রমুখ সংস্কৃত টীকাকার এইসব ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিতে যে উৎসাহ পেয়েছিলেন, তা জৈনদের জন্যই সম্ভব হল। পঞ্চমত, ভারতের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় জৈনদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি উদয়গিরি পাহাড়ের জৈন গুহামন্দির, জুনাগড় ও ইলোরার জৈনমন্দির, রাজস্থানের আধু পাহাড়ের জৈনমন্দির এবং কাগজের উপর প্রথম চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ইত্যাদি সবই জৈনদের অবদান ছিল।
• বৌদ্ধধর্মের মূল শিক্ষা ও তার প্রভাব (Main teachings and impact of Buddhism) :
বুদ্ধকে শাক্যমুনি বলা হয়। কেউ বলেন ৫৬৬ খ্রিঃ পূঃ আবার কারো মতে ৫৬৩ খ্রিঃ পূঃ বুদ্ধের জন্ম হয়। সেই হিসাবে বুদ্ধের মৃত্যু ৪৮৬ খ্রিঃ পূঃ ও ৪৮ খ্রিঃ পূঃ কে অনেকে চিহ্নিত করতে চান। তাঁর পিতা শুদ্ধোদন নেপালের তরাই অঞ্চলের চার কিমি. দক্ষিণে কপিলাবস্তুর নির্বাচিত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি শাক্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মাতা দেবদাহের রাজকন্যা মায়াদেবী কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানের শালকুঞ্জে ভ্রমণের সময় বুদ্ধের জন্ম হয়। 'গৌতম গোত্রে' এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধ মাতৃহারা হন। ফলে মাসি ও বিমাতা প্রজাপতি গৌতমী সিদ্ধার্থ বা বুদ্ধকে মাতৃস্নেহে বড়ো করে তোলেন। পিতা শুদ্ধোদন গৌতমকে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গোপা বা যশোধরা নামে এক সুন্দরী শাক্যরাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ দেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর রাহুল নামে এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। বুদ্ধের গৃহত্যাগের ঘটনাকে তাই বৌদ্ধগ্রন্থে “মহাভিনিষ্ক্রমণ” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে দিব্যজ্ঞানী ভগবান বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের উপলব্ধির কথা প্রচার করবেন কিনা সংশয়ে ছিলেন। পরে ঠিক করলেন মানবসমাজের কল্যাণের জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা জানানো প্রয়োজন।
ভগবান বুদ্ধের ধর্মমত বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ— 'ত্রিপিটক' থেকে জানা যায়। ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ আছে—(ক) সূত্র পিটক (বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ), (খ) বিনয় পিটক (বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ও সংঘের নিয়মাবলি) ও (গ)অভিধর্ম পিটক (বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা)। জাতক থেকে কিছু কথা জানা যায়। বাস্তববাদী ও সাম্যবাদী ধর্মবিপ্লবী বুদ্ধ বলতেন “সমুদ্রের জলের যেমন স্বাদ একটাই তা হল লবণাক্ত, আমার ধর্মের তেমনি একটি লক্ষ্য, তা হল মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত করা।” এই দুঃখের কারণ অবিদ্যা এবং আসক্তি। ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী বলেন, যেহেতু সব মানুষ দুঃখের অধীন, তাই আর্যসত্য সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই আর্যসত্য চারটি—(১) জগতে দুঃখ-কষ্ট আছে, (২) দুঃখ-কষ্টের কারণও আছে, (৩) এই দুঃখ নিবারণ করা সম্ভব এবং (৪) দুঃখ-কষ্ট থেকে নিবৃত্তির পথ বা মার্গ আছে। এই দুঃখ নিবৃত্তির মোট আটটি পথের কথা ভগবান বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন, যা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' (Eight fold Path) নামে পরিচিত। এই পথ বা মার্গগুলি হল— (১) সৎ- চিন্তা, (২) সৎ-কর্ম, (৩) সং-বাক্য, ৪) সৎ-জীবিকা,(৫) সৎ-চেষ্টা,(৬) সৎ-দৃষ্টি, (৭) সৎ-সংকল্প এবং (৮) সৎ বা সম্যক সমাধি। এই আটটি পথ ঠিকভাবে কেউ অনুসরণ করে চললে পরম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ হয়। ড. কোশাম্বী বলেন এই পথগুলি সামাজিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বুদ্ধ-প্রচারিত 'পঞ্চশীল' হল ব্যাভিচার, মদ্যপান, মিথ্যাভাষণ, পরস্বপহরণ ও হিংসা থেকে দূরে থাকা। বুদ্ধ সর্বদা মধ্যম পন্থা (Middle Path) অনুসরণের কথা বলতেন। তাই জৈনদের কঠোর কৃচ্ছসাধন ও তপস্যা এবং লোকায়ত চার্বাকদের অতিরিক্ত ভোগলিপ্সাকে তিনি মঝিম্ বা মধ্যপন্থা পছন্দ করতেন না। এই দুই-এর মাঝামাঝি পথ ছিল অষ্টমার্গ, যা পালনের জন্য কঠিন তপস্যা বা ভোগ-বিলাসিতার দরকার ছিল না। এই আটটি পথকে তাই মধ্যপন্থা বা পালি ভাষায় 'মঝঝিম্' বলা হত।
সমস্ত জাগতিক আসক্তি ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আত্মার চরম মুক্তিই হল 'নির্বাণ'। নির্বাণ আত্মার চরম মুক্তি অর্থ নিভে যাওয়া। এই তত্ত্বটি জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদের এক অনিবার্য কার্য-কারণসূত্রে বাঁধা। কারণ জন্মালেই কর্ম করতে হয় এবং তার ফল ভোগ এক জন্মে না হলে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়।
• বৌদ্ধধর্মের প্রভাব : বৌদ্ধধর্মের প্রভাববিস্তারের ও জনপ্রিয়তার পিছনে বহু কারণ বিদ্যমান।
- (১) বৌদ্ধধর্মে ব্যয়বহুল যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র, উপনিষদের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ছিল না। তাই সাধারণ মানুষ এই ধর্মের বিশেষ অনুগামী হয়ে ওঠে।
- (২) ভগবান বুদ্ধের সহজ সরল উপদেশ, সৌম্য ভাবমূর্তি, চারিত্রিক শুচিতা ও গভীর আত্মপ্রত্যয় মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল।*
- (৩) সব জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম যে নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য পালনের কথা তুলে ধরেছে, এককথায় তা অনবদ্য ঘটনা। গবেষক রিজ ডেভিডস, কোশাম্বী প্রমুখ এই সামাজিকতাকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ বলে মনে করেন।
- (৪) এই ধর্মে মধ্যপন্থার অস্তিত্বের কারণে সংসারী মানুষ ও সাধু-সন্ন্যাসী সকলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।
- (৫) তাছাড়া বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ভাষা সাধারণ মানুষের কথ্যভাষা—পালি ও প্রাকৃত হওয়ায়, মানুষের মধ্যে সহজেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
- (৬) বণিকরা (শেরঠী) বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। (৭) রাজানুকূল্য লাভও বৌদ্ধধর্মের স্বদেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তার আর একটি বড়ো কারণ। অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্ধন, বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের জন্য সক্রিয় চেষ্টা করেছিলেন।
আরও পড়ুন অশোকের ধর্মের বৈশিষ্ট্য
বৌদ্ধধর্মের সাফল্য ও অবলুপ্তির কারণ : বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের কয়ের শতাব্দীর মধ্যেই ভারত ও ভারতের বাইরে নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয় এবং মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে তা বিশ্বধর্মে রূপান্তরিত হয়। বৌদ্ধধর্মের এই সাফল্যের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। বুদ্ধদেবের মহানুভবতা, সহজ, সরল ও বিনম্র ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতের পরিবর্তে সাধারণের বোধগম্য পালি ভাষায় প্রচারকার্য এবং বৌদ্ধধর্মের জাতিভেদ, যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা-বিরোধী মনোভাব বহু মানুষকে এই নতুন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। এছাড়া, সুশৃঙ্খল সঙ্ঘের অস্তিত্ব ও রাজানুগ্রহ বৌদ্ধধর্মের সাফল্যে নানাভাবে সাহায্য করে।
ভারতের বাইরে নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম বিদ্যমান থাকলেও বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে আজ তা প্রায় বিলুপ্ত। বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে পণ্ডিতরা রাজানুগ্রহ অবলুপ্তির কারণ থেকে বৌদ্ধধর্মের বঞ্চনা, শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকদের উত্থান, বৌদ্ধধর্মে ক্রমশ হিন্দু আচার ও মূর্তিপূজা গ্রহণের ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য বিলুপ্তি, বৌদ্ধসঙ্ঘে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ এবং ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার প্রভৃতি কারণের উল্লেখ করেছেন।
* ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট লিখেছেন— "In controversy he (Buddha) was more patient and considerate than any other of the great teachers of mankind".
সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য : ১. বিবর্তনই ভারতীয় সভ্যতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ২. হরপ্পা সভ্যতা হল মেহেরগড় সভ্যতার এক উন্নত ও পরিণত রূপ। ৩. হরপ্পার সঙ্গে মিশর, মেসাপটেমিয়ার সম্পর্ক ছিল। ৪. হরপ্পা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে বহু বিষয়ে মিল ও অমিল রয়েছে। ৫. পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যসভ্যতায় জটিলতা ও বিবর্তন আসে। ৬. প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের ফলে নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে বহু শহর গড়ে ওঠে। ৭. বৈদিক ব্রাক্ষ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামী ও জটিলতার জন্য মহাবীর, বুদ্ধদেব প্রমুখ প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে মানবতার জয়গান করেছিলেন।
স্মরণীয় কালপঞ্জি খ্রিঃ পূঃ (আনুমানিক)
- ৫৬৬—বুদ্ধদেবের জন্ম
- ৫৪০ – মহাবীরের জন্ম
- ৪৮৬—বুদ্ধদেবের মৃত্যু
- ৪৬০— মহাবীরের মৃত্যু
- "For hundred of years before Buddha's time, movements were in progress in Indian thought which prepared the way for Buddhism."-Oldenburg
- "It was Gautam Buddha who rose in open protest against the power and ritual of the Brahmanas and thus introduced a new force into Indian life and thought." - Dr. D. C. Sircar
- "Thus the social equality preached by Buddhism would naturally have made a strong appeal to those that were considered socially inferior. Buddhism certainly made its appeal to the lower orders of society"-Asoka and the Decline of the Maurys, Dr. Romila Thaper,
- "In the earlier stages Buddhism was supported largely by the commercial I the decline of the Mauryas, Romila Thaper,




.png)
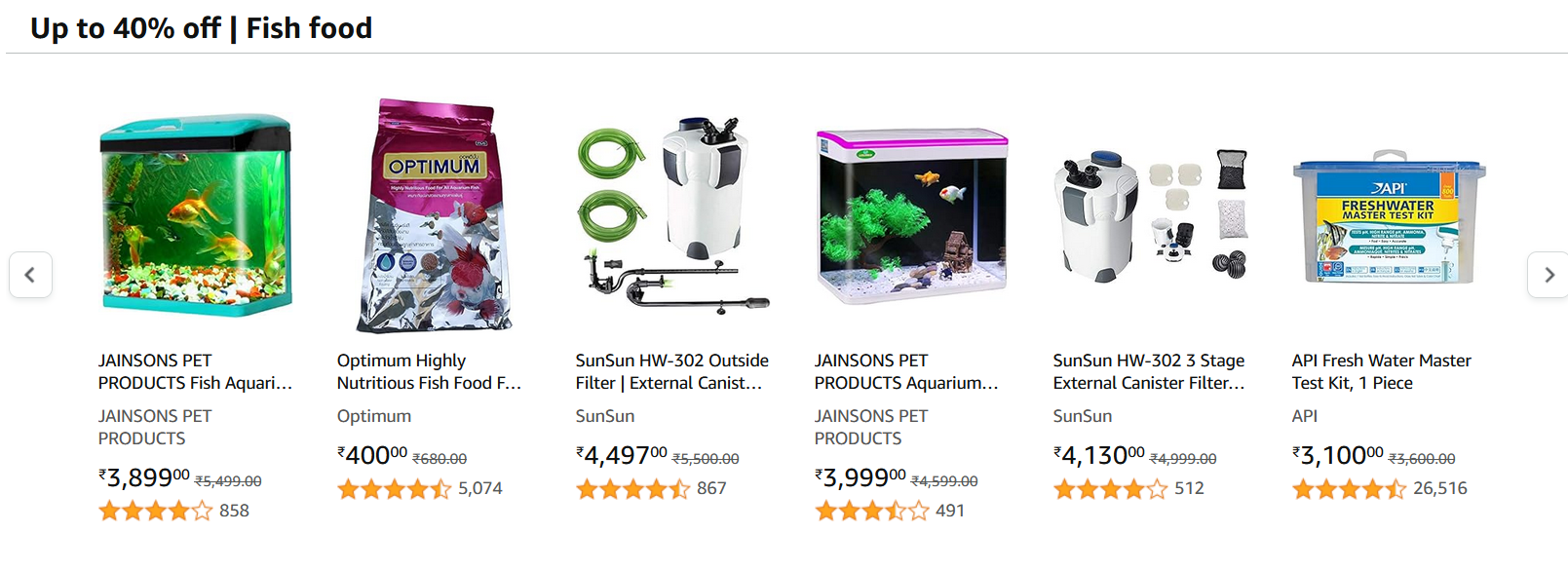
khub shundor
উত্তরমুছুন