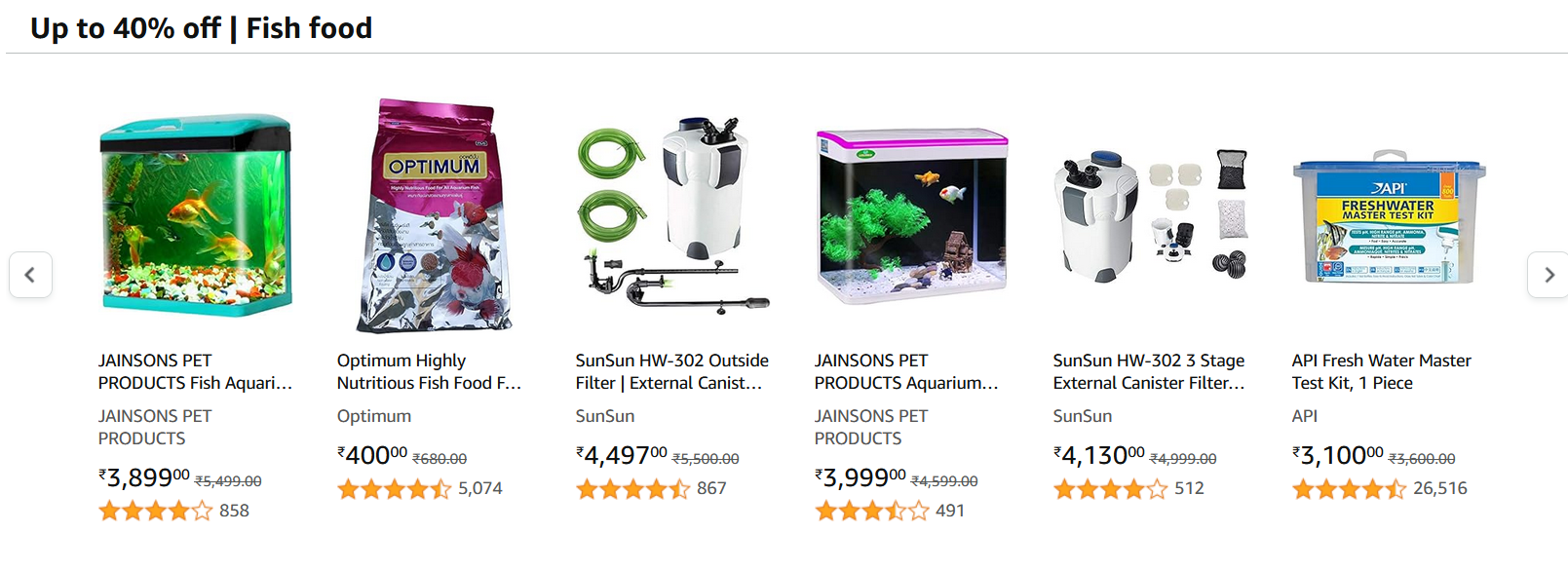ভারত ইতিহাসে মধ্যযুগ

ভারত ইতিহাসে মধ্যযুগ
'মুসলিম যুগ' নয়—'মধ্যযুগ'
(সুলতানি শাসন)
সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়। এই তিনটি যুগের নামকরণ সম্পর্কে পণ্ডিতরা কিন্তু একমত নন। সুপ্রাচীন অতীত থেকে শুরু করে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত যুগকে 'হিন্দু যুগ, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে 'মুসলিম যুগ এবং ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী কালকে 'ব্রিটিশ যুগ' বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকে আবার এ ধরনের যুগ-বিভাজনের বিরোধিতা করে ভারত ইতিহাসকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ— এই তিনটি যুগে বিভক্ত করেন। বলা বাহুল্য, ইতিহাসে এ ধরনের যুগ-বিভাজন যুক্তিসম্মত নয় বা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ ইতিহাস কখনই থেমে থাকে না— ইতিহাস অখণ্ড, অবিভক্ত ও অবিভাজ্য এবং তার ধারা চিরপ্রবহমান।
এ সত্ত্বেও মানুষের ধ্যান-ধারণা বা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাসে যুগ-বিভাজন করা হয়। তবে ভারত ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ বা ব্রিটিশ যুগ বলে চিহ্নিতকরণ করা ঠিক নয়। তথাকথিত 'হিন্দু যুগ'-এ ভারতে কেবল বৈদিক হিন্দুধর্মই প্রচলিত ছিল না বা কেবলমাত্র হিন্দুরাজারাই রাজত্ব করতেন না। এই যুগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মত জৈন শাসক এবং অশোক ও কণিষ্কের মত বৌদ্ধ নরপতিও সগৌরবে রাজত্ব করে ভারত ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন। যুগ যুগ ধরে বৈদিক হিন্দুধর্ম নানাভাবে ও নানারূপে পরিবর্তিত হয়, বহু বিদেশি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজা ভারতে রাজত্ব করেন এবং এক সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সুতরাং 'হিন্দু যুগ' নয়-ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায়কে 'প্রাচীন যুগ' বলাই বিধেয়। অনুরূপভাবে 'মুসলিম যুগ' কথাটিও যুক্তিসম্মত নয়। তথাকথিত এই 'মুসলিম যুগ'-এ মুসলিম শাসকদের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং এর মধ্যে কিছু রাজ্য কেবলমাত্র মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রতিরোধই গড়ে তোলেনি — শত্রুরাজ্যের ওপর বলিষ্ঠ আক্রমণও হেনেছিল। উড়িষ্যা, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ছোটনাগপুর ও কেরালার বহু অঞ্চল এবং দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্য দীর্ঘকাল মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে সগৌরবে রাজত্ব করেছিল।
তথাকথিত মুসলিম যুগে মুসলিম শক্তি ভারতে তার প্রাধান্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। গজনীর ঘুর-বংশীয় নরপতিদের অধীনে ভারতে ইসলামের যে জয়যাত্রা শুরু হয়, তুঘলক বংশীয় সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালের কিছুকাল পর্যন্ত (১৩৩৯ খ্রিঃ) তা অব্যাহত ছিল। এর পরের দুইশ' বছরে ভারতে ইসলামের আধিপত্য যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব হয়। এই সময় দিল্লি সুলতানির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়, উত্তর ভারতে রাজপুত শক্তির পুনরুত্থান ঘটে, দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৈমুর লঙের আক্রমণে সুলতান-শাহির প্রাণশক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে। ১৫৫৬খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহণে মুসলিম শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের কিছুকাল পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ পর্বে মোগল আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়ে, ভারতের বহু অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও মারাঠারা প্রবল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র মুসলিমদের কৃতিত্বই নয়— রাজপুত, শিখ, মারাঠা ও অন্যান্য হিন্দু রাজন্যবর্গের গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় এই যুগ উদ্ভাসিত।
ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও শাসনকার্যে হিন্দুরাজ্য ও হিন্দু রাজকর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শেরশাহ বা আকবর-প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা অভূতপূর্ব হলেও প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের কাছে তা অচিন্তনীয় ছিল না এবং তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তথাকথিত মুসলিম শাসনে প্রাচীন হিন্দুযুগে দেশের সব মানুষ যেমন হিন্দু হয়ে যায়নি, তেমনি এই যুগেও সব মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেনি। মুসলিম শাসকের সঙ্গে হিন্দুপ্রজার বিরোধ থাকলেও সমাজে নিচু তলার হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে এক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। হিন্দুদের শাঁখা-সিঁদুর যেমন মুসলিমরা গ্রহণ করেছিল, তেমনি মুসলিমদের সত্যপীর হিন্দুদের সত্যনারায়ণে পরিবর্তিত হয়েছিল।
এ সত্ত্বেও বলতে হয়, মুসলিম শাসনে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও শাসনব্যবস্থায় নানা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বহু বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে বিদেশি মুসলিমরাও ভারতীয় দেহে লীন হয়ে যায়। ৭১১-১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু জয়ে যে বীজ রোপিত হয়, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবকের সিংহাসনারোহণে তা অঙ্কুরিত হয়ে ভারতে মধ্যযুগের সূচনা করে। এ যুগের ইতিহাস কেবলমাত্র মুসলিম আধিপত্য, সংস্কৃতি বা ধর্ম বিস্তারের ইতিহাস নয়—হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ইতিহাস। ইংরেজের আগমনে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সংস্পর্শে এসে ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা হয় এবং নতুন চেতনায় ভারতীয় জনজীবন সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।
সুলতানি যুগের ইতিহাসের উপাদান
১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরির অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর কুতুব উদ্দিন আইবক কর্তৃক দিল্লিতে স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রবর্তন থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে ভারত ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলবংশীয় বাবরের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সময় 'সুলতানি শাসন' বা “সুলতানি- যুগ' বলে পরিচিত। এই যুগে একমাত্র সৈয়দ বংশীয় খিজির খাঁ ব্যতীত- দিল্লির সকল স্বাধীন নরপতিই 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেছিলেন। 'সুলতান' শব্দটি কোরানে 'শক্তি' বা 'সামর্থ্য'-র প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'সুলতান' অর্থে সাধারণভাবে স্বাধীন নরপতিই বোঝায়।
সুলতানি শাসনাধীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলিকে
- (১) সরকারি দলিলপত্র,
- (২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা,
- (৩) বিদেশি পর্যটক ও বণিকদের বিবরণ এবং
- (৪) মুদ্রা ও শিল্প-নিদর্শন প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।
→ ঐতিহাসিকদের রচনা : সমকালীন বহু ঐতিহাসিকই এই যুগের ইতিহাস রচনা করেছেন। রাজানুগ্রহপুষ্ট এইসব ঐতিহাসিকদের রচনা পক্ষপাতদুষ্ট ও অতিরঞ্জিত হলেও, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। মির মহম্মদ মাসুদ রচিত 'তারিখ- ই-সিন্ধ গ্রন্থ থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আরবি ভাষায় রচিত 'চাচনামা' গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আলবেরুনি রচিত 'তহরুক- ই-হিন্দ'বা কিতাব-উল-হিন্দ গ্রন্থে দশম শতকের সমাপ্তি ও একাদশ শতকের সূচনায় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। হাসান নিজামি রচিত 'তাজ উল-মাসির' এবং মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবাকাত- ই-নাসিরি গ্রন্থে মহম্মদ ঘুরির রাজ্যজয় থেকে ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের সভাসদ জিয়াউদ্দিন বরনি রচিত 'তারিখ-ই ফিরোজশাহি গ্রন্থে গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল থেকে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের কয়েক বছরের বিবরণ পাওয়া যায়। কাইকোবাদ থেকে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমল পর্যন্ত দিল্লি দরবারের সভাকবি পদে নিযুক্ত বিশিষ্ট কবি ও ঐতিহাসিক আমির খসরু রচিত 'কিরান-উস-সাদিন, মুফতা-উল-ফ: 'আসিক', 'তুঘলকনামা' প্রভৃতি গ্রন্থে সমকালীন ইতিহাসের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁকে 'ভারতের তোতাপাখি' বলা হয়। এ ছাড়া, ফিরোজ তুঘলক রচিত 'ফতোয়ার-ই-ফিরোজশাহি, ইসামি রচিত 'ফতা উথ-সালাতিন' সামস-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহি ' প্রভৃতি গ্রন্থ অতি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।
বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ : সুলতানি আমলে যে-সব বিদেশি পর্যটক ভারতে আসেন তাদের রচনা থেকেও ইতিহাসের নানা তথ্যাদি জানা যায়। বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আলবেরুনির 'তহকক-ই-হিন্দ' বা 'কিতাব-উল-হিন্দ' গ্রন্থে সমকালীন ভারতের সুন্দর বিবরণ আছে। আফ্রিকাবাসী ইবন বতুতা চোদ্দ বছর ভারতে ছিলেন এবং এর মধ্যে আট বছর তিনি দিল্লিতে বাস করে সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা 'কিতাব-উল-রাহলা' মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ। ইটালির মার্কোপোলো, নিকোলো কণ্টি, পর্তুগিজ প্যায়েস, বরবোসা, নুনিজ, পারস্যের আবদুর রজ্জাক, রাশিয়ার নিকিতিন প্রমুখের রচনাও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত।
মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন : মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিও এই যুগের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। ঐতিহাসিক লেনপুল-এর মতে, এই যুগের মুদ্রাগুলি ইতিহাসের এই অধ্যায়ের প্রধান ও নিশ্চিত ভিত্তি-স্বরূপ। তাঁর মতে এই মুদ্রাগুলি থেকে রাজাদের রাজবংশ, রাজত্বকাল, রাজ্যের আয়তন, রাজার সিংহাসনারোহণের সময়, ধর্মমত, ধাতুশিল্পের অবস্থা প্রভৃতি বহু বিষয়ের কথা জানা যায়। এছাড়া এই যুগের মসজিদ, স্মৃতিসৌধ, প্রাসাদ এবং ললিতকলার বিভিন্ন নিদর্শন থেকেও ইতিহাসের তথ্যাদি জানা যায়।
ভারতে ইসলামের আবির্ভাব
হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্মের নবী ছিলেন। বহু দল-উপদলে বিভক্ত আরবদেশকে এক ধর্মসূত্রে আবদ্ধ করে আরববাসীকে তিনি এক জাতিতে পরিণত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রিঃ) আরবরা পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ক্রিট, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি স্থান দখল করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে।
আরবদের সিন্ধজয় : আরবের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতি প্রাচীন। আরবে ইসলামধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব থেকেই আরবের বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূল ও দক্ষিণাত্যে বাণিজ্য করতে আসত। আরবে ইসলামধর্ম প্রসারিত হওয়ার পরেও এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল এবং এ সময় থেকেই আরবরা ভারতে রাজ্যবিস্তারে আগ্রহী হয়। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর-এর শাসনকালে আরবরা পশ্চিম উপকূলে বোম্বাইয়ের থানা, ভারুচ এবং সিন্ধুর দেবল বন্দরে আক্রমণ হানে। এই সব আক্রমণ প্রতিহত হয়। এরপর তারা উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে আরব সেনাপতি আবদুল্লাহ মাকরণ দখল করেন। ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বোলান গিরিপথ দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়।
৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবরা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সিন্ধুদেশ জয় করে। আরবি 'চাচনামা' মির মহম্মদ মাসুদ রচিত 'তারিখ-ই- সিদ্ধ গ্রন্থ এবং আল বিলাদুরি-র রচনা থেকে সিন্ধুদেশে আরব আক্রমণ ও আরব শাসনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এ সময় দাহির নামে ব্রাহ্মণবংশীয় জনৈক রাজা সিন্ধুদেশে রাজত্ব করতেন। আরবদের সিন্ধু আক্রমণের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন যে, ইসলামধর্মের বিস্তারের উদ্দেশ্যেই আরবরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য, এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সিন্ধুদেশ জয়ের পর আরব সেনাপতি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিজ নিজ অধিকার ভোগ করার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন এবং এ সময় ব্যাপক ধর্মান্তকরণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অনেকে আবার মনে করেন যে, ধর্মবিস্তার নয়—ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যাই হোক, একটি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে তারা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ৭০৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহলের রাজা ইরাক ও খোরাসনের আরব শাসনকর্তা অল্-হজ্জাজ-এর জন্য উপঢৌকনসহ কয়েকটি জাহাজ পাঠান। সিন্ধুদেশের অন্তর্ভুক্ত দেবল (করাচী) বন্দরে জাহাজগুলি জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হলে অল্-হজ্জাজ দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃত হলে অল্-হজ্জাজ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। ওবেদুল্লা ও বুদাইল নামক দু'জন সেনাপতির নেতৃত্বে পর পর দু'টি অভিযানের ব্যর্থতার পর ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিম-এর নেতৃত্বে আরবরা রাও-এর যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়। দাহির নিহত হন এবং আরবরা দেবল ও রাওর-সহ সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করে। ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুলতান জয় করেন। অষ্টম শতকের শেষ দিকে সিন্ধুদেশে আরব শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দ্বাদশ শতকের শেষ পর্বে মহম্মদ ঘোরির আক্রমণে তা বিলুপ্ত হয়।
ইংরেজ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল-এর মতে, আরবদের সিন্ধুজয় ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে ফলাফলহীন একটি ঘটনামাত্র। ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসে সিন্ধুজয় প্রথম পদক্ষেপ হলেও ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা কোন স্থায়ী রেখাপাত করেনি। আরব আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং তা একমাত্র সিন্ধুতেই সীমাবদ্ধ ছিল সিন্ধুদেশকে কেন্দ্র করে কখনই তা ভারতের অন্তর্দেশে বিস্তৃত হতে পারেনি। ভারতের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম শক্তিকে কেবলমাত্র সিন্ধুদেশেই প্রায় তিনশ' বছর আবদ্ধ থাকতে হয়। সিন্ধুদেশে কিছু মানুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, শাসন-পদ্ধতি বা সামাজিক রীতিনীতির ওপর আরব শাসনের কোন প্রভাবই পড়েনি। বিপরীতভাবে, আরবরা ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা যথেষ্টভাবে প্রভাবিত হয়। সিন্ধু অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে
আরবরা ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে এবং তাদের মাধ্যমে তা ইওরোপে সম্প্রসারিত হয়। খলিফা মনসুর-এর আমলে ভারত থেকে বেশ কিছু হিন্দু পণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও রাজনিধি আরবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। খালিফা মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত' ও 'খাদ্য-খাগুক নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীর ভাষায় অনূদিত হয়। আমির খসরু-র রচনা থেকে জানা যায় যে, আরব জ্যোতির্বিদ আবু মাশার বারাণসীতে দশ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। আরবদের সিন্ধুজয়ের অর্থনৈতিক ফলাফল ও উপেক্ষণীয় নয়। আরব-অধিকৃত সিন্ধুর মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরও পড়ুন
ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা
→ মুসলিম আক্রমণের কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা : আরবদের সিন্ধু জয়ের পর (৭১২ খ্রিঃ) প্রায় তিনশ' বছর পর্যন্ত মুসলিম শক্তি ভারতে কোন রাজ্যবিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভারতে মুসলিম রাজত্ব স্থাপন তুর্কি-দের কীর্তি এবং এ কাজ শুরু করেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনি রাজ্য-র তুর্কি সুলতানরা।
দশম শতকের সমাপ্তি ও একাদশ শতকের সূচনায় তুর্কি আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবদমান কয়েকটি স্থানীয় শক্তি তখন দেশ শাসন করত। হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে পাঞ্জাবের চেনাব নদ পর্যন্ত অঞ্চলে রাজপুত শাহি বংশ রাজত্ব করত। প্রায় তিনশ' বছর ধরে শাহি বংশ সাফল্যের সঙ্গে আরব আক্রমণ প্রতিরোধ করে। ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্য এই রাজবংশকেই সর্বপ্রথম গজনি থেকে আগত তুর্কিদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য কাশ্মীর-এর অবস্থা তখন সন্তোষজনক ছিল না। উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান রাজা কনৌজের প্রতিহার শক্তির দুর্বলতার সুযোগে দিল্লি- আজমিরে চৌহান, গুজরাটে চৌলুক্য, মালবে পারমার, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেশ, বিলাসপুর- জব্বলপুর অঞ্চলে কলচুরি প্রভৃতি রাজপুত বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার পাল বংশীয় রাজন্যবর্গ তখন দুর্বল ছিলেন। এইসব পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত এবং দেশের সামগ্রিক স্বার্থ উপেক্ষা করে নিজ নিজ রাজ্য ও বংশের গৌরববৃদ্ধি করাই এই সব রাজন্যবর্গের লক্ষ্য ছিল।
ভারতীয় সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডও সেদিন ভেঙে পড়েছিল। ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এই নৈতিক অধঃপতনের চিত্র সুপরিস্ফুট। জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, নারীর প্রতি চরম অবহেলা, আচারের আতিশয়া এবং ধর্মের নামে প্রচণ্ড গোঁড়ামি, দেবদাসী প্রথা ও রুচির বিকৃতি সমাজের প্রাণশক্তিকে সেদিন নিস্তেজ করে দেয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী দেশ ছিল এবং অভিজাত সম্প্রদায়, বিলাস-ব্যসনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতেন। সাধারণ পাল্লিবাসী কৃষক ও কারিগর ও চরম অবহেলিত। সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাবে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।জাতীয় জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে গজনির সুলতান মামুন ভারত আক্রমণ করেন।
→ সুলতান মামুদ : ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলপ্তগিন নামে জনৈক ভাগজ্যাম্বেশী আফগানিস্তানে গজনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগিন গজনির সিংহাসনে বসেন। তুর্কি সুলতানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং এর ফলে পাঞ্জাবের শাহি বংশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। শাহিরাজ জয়পালকে পরাজিত করে তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিম ভূভাগ পর্যন্ত অঞ্চল দখল করেন। তাঁর পুত্র সুলতান মাসুদ-এর রাজত্বকাল (৯৯৮-১০৩০ খ্রিঃ)-এ ভারতে প্রথম তুর্কি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
সুলতান মামুদ মোট কতবার ভারত আক্রমণ করেন এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ঐতিহাসিক হেনরি এলিয়ট-এর মতে, ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক বর্তমানে এই মতটিই মেনে নিয়েছেন। তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ঐতিহাসিকরা একমত নন।
(১) ঐতিহাসিক স্মিথ-এর মতে, ভারত আক্রমণের “সুলতান মামুদ ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী লুণ্ঠনকারী দস্যু।” ভারতে তিনি নির্বিচারে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে গেছেন। ধনরত্ন লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে এসেছিলেন—এখানে কোন স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি।
(২) তাঁর দরবারের ঐতিহাসিক উৎবি মন্তব্য করেন যে “ভারত অভিযানের দ্বারা মামুদ নিজ বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি মহৎ কর্তব্য পালন করেন।” উৎবি-র এই উক্তির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা বলতে শুরু করেন যে, ধর্মীয় উন্মাদনার জন্যই তিনি ভারত অভিযানে আসেন এবং এজনাই তিনি হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করতেন। বলা বাহুল্য, এই মত গ্রহণযোগা নয়। তিনি হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করতেন, কারণ এই যুগে মন্দিরগুলি প্রভূত ধনরত্ন পূর্ণ ছিল। হিন্দুমন্দিরগুলি লুণ্ঠন করলেও তিনি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার কোন চেষ্টা করেননি—এমনকি তাঁর অধিকৃত সিন্ধু ও পাঞ্জাবে হিন্দুদের ধর্মেও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। অধ্যাপক জাফর বলেন, তিনি যদি কোন হিন্দুমন্দির ভেঙে থাকেন তবে তা ধন-রত্নের লোভে। অধ্যাপক হ্যাভেল বলেন যে, তিনি যেভাবে কনৌজ বা মথুরা লুণ্ঠন করেছিলেন, প্রয়োজন হলে অনুরূপভাবেই তিনি বাগদাদ বা যে-কোন মুসলিম নগর লুণ্ঠন করতেন।
(৩) বলা হয় যে, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মধ্য এশিয়ার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ইরানি সংস্কৃতির নবযুগের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। এজন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ ও সম্পদ। এই কারণেই তিনি ভারত অভিযানে অগ্রসর হন। বারংবার ভারত আক্রমণ ও হিন্দু দেব-দেবী মূর্তি ভঙ্গ করার ফলে ইসলাম জগতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি 'বাথ -সিকান বা মূর্তিভঙ্গকারী রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। সুতরাং কেবলমাত্র সম্পন-সংগ্রহই নয়- ইসলাম জগতে নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নটিও তাঁর ভারত আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ছিল। ঐতিহাসিক ডঃ মহম্মদ হাবিব মন্তব্য করেছেন যে, ভারত আক্রমণে সুলতান মামুদ "সোনা ও সম্মান ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেননি।" পাঞ্জাবের শাহি-রাজ্য জয় তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ভারতের প্রধান প্রধান নগর ও মন্দিরগুলিই ছিল তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য এবং এর ফলে তিনি কনৌজ, মথুরা, থানেশ্বর কালিঞ্জর প্রভৃতি স্থানগুলি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করেন। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন এবং প্রায় দুই কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও প্রচুর অলংকার-সহ গজনিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে কোন স্থায়ী রাজ্যবিস্তার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে স্থায়ীভাবে কোন সাম্রাজ্য স্থাপন করা সুলতান মামুদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং তা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও মুলতান তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন এবং এর ফলে ভারতে মুসলিম প্রভুত্ব স্থাপনের পথ সুগম হয়। তাঁকে নিঃসন্দেহে মহম্মদ ঘুরির পথপ্রদর্শক বলা যায়। তাঁর বারংবার আক্রমণের ফলে ভারতের অপরিমিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং সবই দেশের বাইরে চলে যায়—যা আর কখনও ফিরে আসেনি। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। যুদ্ধে ভারতীয় যোদ্ধাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। এইভাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয়ের ফলে পরবর্তীকালে হিন্দুদের পক্ষে তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি হ্রাস পায় এবং মহম্মদ ঘুরির আগমন সহজতর হয়ে ওঠে। তাঁর আক্রমণের ফলে ভারতে অনেক মুসলিম বণিক ও ব্যবসায়ীর আগমন হয় এবং তাদের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়, যা উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। তুর্কি আক্রমণের সূত্রেই এদেশে সুফি সাধকদের আগমন ঘটে – যাঁরা হিন্দু-মুসলিম উভয়ের মধ্যে প্রেম, ভক্তি ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচার করে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের পথ তৈরি করেন।
→ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলবেরুনি : সুলতান মামুদের অন্যতম সভাসদ, অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত আলবেরুনি ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খোয়ারিজাম রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আৰু রিহান। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকালে তিনি তাঁর সঙ্গে ভারতে আসেন এবং একাধিক্রনে দশ বছর ভারতে বসবাস করেন। ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রাচীন ভারতের বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবীয় ভাষায় রচিত 'কিতাব-উল-হিন্দ'বা 'তহকক-ই-হিন্দ নামে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত ভারত-সম্পর্কিত গ্রন্থে দশম শতাব্দীর শেষভাগ ও একাদশ শতকের সূচনায় ভারতীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় পণ্ডিতদের বিজ্ঞানবিমুখতা, কুপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণতা ও দাম্ভিকতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের সত্যনিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদাবোধের কথা বলতেও ভোলেননি। তাঁর মতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং অন্যান্য জাতির মানুষকে তাঁরা অপাংক্তেয় বলে মনে করতেন। ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথা, বর্ণব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বৈধব্য যন্ত্রণা, ধর্মের আচার-সর্বস্বতা প্রভৃতির কথা তিনি বিশদভাবে বলেছেন। ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও রাজন্যবর্গের দূরদর্শিতার অভাব সম্পর্কেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। এককথায়, তাঁর রচিত গ্রন্থটিকে 'ভারত-কোষ’ বলা যায়, কারণ ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিদ্যাচর্চা, রাজনীতি ও আইন-কানুনের সব কিছুই এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।
স্মরণীয় কালপঞ্জি খ্রিস্টাব্দ
- ৭১২ – আরবদেশের সিন্ধুজয়।
- ৭১৩—মহম্মদ-বিন-কাসিমের মুলতান জয়।
- ৯৬২–আলপ্তগিনকর্তৃক গজনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
- ৯৭৩-আলবেরুনির জন্ম।
- ১০০০—সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ।
"We may look upon Muhammadan coins as the surest foundation for an exact history of the dynasties by which they were issued."
“I (আরব আক্রমণ) was an episode in the history of India and of Islam. a triumph without results." - Stanley Lane-poole
"A great many elements of Arban culture which afterwards had such a profound effect upon European civilisation, were borrowed from India"- Dr.. Ishwari Prasad
"Mahmud was simply a bandit operating on a large scale."--Smith
প্রশ্ন উওর পর্ব
1. কোন সময়কে সুলতানী যুগ বলে অভিহিত করা হয়?
উঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল বংশীয় বাবরের সিংহাসন আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত সময় সুলতানী যুগ বলে পরিচিত।
2. সুলতান শব্দের অর্থ কী?
উঃ স্বাধীন নরপতি।
3. ‘তারিখ-ই-সিন্ধু’ গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উঃ মীর মহম্মদ মাসুদ।
4. আলবেরুণী রচিত গ্রন্থটির নাম কী?
উঃ তহকক্-ই–হিন্দ।
5. কিতাব-উল-রাহলা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ ইবন বতুতা।
6. আমীর খসরু রচিত গ্রন্থটির নাম কী?
উঃ তুঘলক নামা।
7. ‘তবাকত-ই-নাসিরি’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ মিনহাজ-উস-সিরাজ।
8. ‘তারিখ-ই-ফিরোজশাহী’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ জিয়াউদ্দীন বরণী।
9. আরবরা কবে সিন্ধুদেশ জয় করে?
উঃ ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে।
10. সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেছিল?
উঃ ১৭ বার।
11. আলবেরুণী কার সভাসদ ছিলেন?
উঃ সুলতান মামুদের।
12. আলবেরুণী কত খ্রীষ্টাব্দে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর প্রকৃত নাম কী? তিনি কার সঙ্গে ভারতে আসেন এবং কত বছর ভারতে ছিলেন?
উঃ ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যএশিয়ার খোয়ারিজাম রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু রিহান। তিনি মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন। তিনি ১০ বছর ভারতে ছিলেন।
13. কবে,কাদের মধ্যে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়?
উঃ ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং মহম্মদ ঘুরীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরী পরাজিত হন।
14. কবে,কাদের মধ্যে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়?
উঃ ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং মহম্মদ ঘুরীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হন।
15. ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল?
উঃ মহম্মদ ঘুরী।
16. দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল?
উঃ কুতুবউদ্দিন আইবক।
17. আইবক কথার অর্থ কী?
উঃ দাস।
18. কুতুবুদ্দিনের পর কে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন?
উঃ ইলতুৎমিস।
19. ‘ইকতা’ ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?
উঃ ইলতুৎমিস।
20. চল্লিশ চক্র বা বন্দেগান-ই-চাহেলগানী কে প্রবর্তন করেন?
উঃ ইলতুৎমিস।
21. ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে বসেন?
উঃ রুক্নউদ্দিন ফিরোজ।
22. ভারতের তোতাপাখি নামে কে পরিচিত?
উঃ আমীর খসরু।
23. খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ ফিরোজ শাহ খলজী।
24. খলজী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন?
উঃ আলাউদ্দিন খলজী।
25. দাগ ও হুলিয়া ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?
উঃ আলাউদ্দিন খলজী।
26. খলজী বংশের শেষ সম্রাট কে ছিলেন?
উঃ কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ।
27. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।
28. দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর কে করেন?
উঃ মহম্মদ বিন তুঘলক।
29. সুলতানী যুগের আকবর নামে কে পরিচিত?
উঃ ফিরোজ শাহ তুঘলক।
30. কোন সুলতানী শাসকের রাজত্বকালে তৈমুরলঙ ভারত আক্রমণ করেন?
উঃ নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহের আমলে।
31. সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
উঃ খিজির খাঁ সৈয়দ। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন আলাউদ্দিন আলম শাহ।
32. লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
উঃ বহলুল লোদী। শেষ রাজা ইব্রাহিম লোদী।
33. কবে,কাদের মধ্যে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়?
উঃ ১৫২৬ খ্রীঃ কাবুলের অধিপতি বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে।
34. কে কবে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
35. কোন রাজার আমলে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও কোতোয়ালি দরওয়ালা তৈরি হয়?
উঃ সিকন্দর শাহের আমলে।
36. কোন চৈনিক দূত গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের দরবারে আসেন?
উঃ চৈনিক দূত মা-হুয়ান।
37. বাংলার আকবর নামে কোন শাসক পরিচিত?
উঃ হোসেন শাহ।
38. ভক্তিবাদী আন্দোলনের একজন নেতার নাম লেখ।
উঃ শ্রীচৈতন্যদেব।
39. ছোট সোনা মসজিদ কোন রাজার আমলে তৈরি হয়?
উঃ হোসেন শাহের আমলে।
40. বড় সোনা মসজিদ কোন রাজার আমলে তৈরি হয়?
উঃ নসরৎ শাহের আমলে।
41. কে কবে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ ১৩৪৭ খ্রী হাসান বা জাফর খাঁ। তাঁর রাজধানী ছিল গুলবর্গায়।
42. তালিকোটার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়? এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয়?
উঃ ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে। একদিকে ছিল বিজাপুর, গলকুণ্ডা, বিদর ও আহম্মদনগর আর অন্যদিকে ছিল বিজয়নগর। এই যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয়।
43. বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ হরিহর ও বুক্কু।
44. বিজয়নগরের সঙ্গম রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন?
উঃ দ্বিতীয় দেবরায়।
45. বিজয়নগরের তুলভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন?
উঃ নরসিংহ। শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়।
46. আমুক্তা মাল্যদা গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ কৃষ্ণদেব রায়।
47. কাকে অন্ধ কবিতার পিতামহ বলা হয়?
উঃ তেলেগু কবি পেদ্দনকে।
48. হাজারা মন্দিরের নির্মাতা কে?
উঃ কৃষ্ণদেব রায়।
49. কবীরের কবিতাগুলি কি নামে পরিচিত?
উঃ দোহা।
50. শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ? তিনি কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উঃ গুরুনানক। তিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের লাহোর জেলার রাভী নদীর তীরে তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
51. শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উঃ গ্রন্থসাহেব।
52. সুফীদের গুরুকে কী বলা হয়?
উঃ পীর বা খাজা বলা হয়।
53. পীরের ধর্মকেন্দ্রকে কি বলা হয়?
উঃ দরগা বলা হয়।
54. সুফী ধর্মের অনুগামীরা কী কি নামে পরিচিত?
উঃ ফকির বা দরবেশ নামে পরিচিত।
55. সুফী সম্প্রদায় কটি ভাগে বিভক্ত? কী কী?
উঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। চিস্তি ও সুহরাবর্দি।
56. চিস্তি সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাধকের নাম লেখ।
উঃ খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি,নিজামউদ্দিন আউলিয়া।
57. সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের কয়েকজন সাধকের নাম উল্লেখ করো।
উঃ শিহাবউদ্দিন সুহরাবর্দি,হামিদউদ্দিন নাগোরী।
58. ‘চিরাগ-ই-দিল্লী বা দিল্লীর আলো’ নামে কে পরিচিত?
উঃ নিজামউদ্দিন আউলিয়া।
59. ‘পৃথ্বিরাজ রাসো’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ চাঁদ বরদৈ।
60. ‘হাম্মির রাসো’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ শাঙ্গঁধর।
61. মালিক মহম্মদ জায়সীর রচিত গ্রন্থটির নাম কী?
উঃ পদুমাবৎ।
62. ‘অলখানন্দা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ জননায়ক।
63. ‘তুজুক-ই-বাবরী’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ বাবর।
64. তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ জাহাঙ্গীর।
65. ‘হুমায়ুন নামা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ গুলবদন বেগম।
66. ‘আইন-ই-আকবরী বা আকবর নামা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ আবুল ফজল।
67. ‘মুন্তাখাব–উল–তারিখ’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ বদাউনী।
68. ‘তবকৎ–ই–আকবরী’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ খোজা নিজামউদ্দিন।
69. ফৈজী রচিত গ্রন্থটির নাম কী?
উঃ আকবর নামা।
70. ‘পাদশাহনামা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ আবদুল হালিম লাহোরী।
71. ‘আলমগীরনামা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ মীর্জা মহম্মদ কাজিম।
72. ‘মুন্তাখাব-উল-লুবাব’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ কাফি খাঁ।
73. ‘তারিখ-ই-বাংলা’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ শলিমউল্লাহ।
74. ‘রিয়াজ-উল-সালাতিন’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উঃ গোলাম হোসেন।
75. আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন?
উঃ দাহির সিন্ধুর রাজা ছিলেন।
76. দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়?
উঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে।
77. সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রথম বংশের নাম কী? এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ দাস বংশ। কুতুবউদ্দিন আইবক।
78. দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
উঃ ইলতুৎমিস।
79. তুর্কি বিজয়ের সময় বাংলার শাসক কে ছিলেন?
উঃ লক্ষ্মণ সেন।
80. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণবিধি কে করেছিলেন?
উঃ আলাউদ্দিন খিলজী।
81. দাক্ষিণাত্যে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিস্তার প্রথম কার সময় হয়েছিল?
উঃ আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে।
82. বলবনের পূর্ব নাম কী ছিল?
উঃ উলুঘ খাঁ।
83. মহম্মদ বিন তুঘলকের পূর্ব নাম কী ছিল?
উঃ জৌনা খাঁ।
84. কে তামার নোট প্রচলন করেছিলেন?
উঃ মহম্মদ বিন তুঘলক।
85. মহম্মদ বিন তুঘলক কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন?
উঃ দিল্লী থেকে দেবগিরিতে।
86. মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে কোন পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন?
উঃ ইবন বতুতা।
87. ‘নব মুসলমান’ কাদের বলা হয়?
উঃ যে সকল মোঙ্গল জালালউদ্দিনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দিল্লীর উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাদের নবমুসলমান বলা হয়।
88. তৈমুর লঙ কোন সময় ভারত আক্রমণ করেন ?
উঃ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।
89. কে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন?
উঃ সুলতান মামুদ।
90. আমীর খসরু কোন সময়ে ভারতে এসেছিলেন?
উঃ খলজী ও তুঘলক শাসনকালে।
91. জিয়াউদ্দীন বরণী কোন সময়ে ভারতে এসেছিলেন?
উঃ মহম্মদ তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের সময়ে।
92. ‘ফুতুহু উস সালাতিন’ গ্রন্থটির লেখক কে?
উঃ খাজা আবদুল্লাহ মালিক।
93. ইবন বতুতার লেখা গ্রন্থটির নাম কী?
উঃ সফর নামা।
94. ‘খামখেয়ালী রাজা’ কাকে বলা হয়?
উঃ মহম্মদ বিন তুঘলককে।
95. চাহেলগান বা চল্লিশ চক্র কে গঠন করেছিলেন?
উঃ ইলতুৎমিস।
96. শিখদের প্রথম গুরু কে?
উঃ গুরু নানক।
97. কবীর কার শিষ্য ছিলেন?
উঃ রামানন্দের।
98. গুরুমুখী কোন অঞ্চলের ভাষা?
উঃ পাঞ্জাবের।
99. ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ গ্রন্থটি কার লেখা?
উঃ মালাধর বসুর লেখা।
100. বিজয়গুপ্তের গ্রন্থের নাম কী?
উঃ মনসামঙ্গল (পদ্মাপুরাণ)।
101. চৈতন্যদেব কবে কোথায় দেহরক্ষা করেন?
উঃ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে।
102. যে বিদেশী পর্যটক বিজয়নগরে এসেছিলেন তাদের দুজনের নাম কর?
উঃ ইতালীয় পর্যটক নিকোলোকন্তি। পারস্যের পর্যটক আবদুর রজ্জাক।



.png)