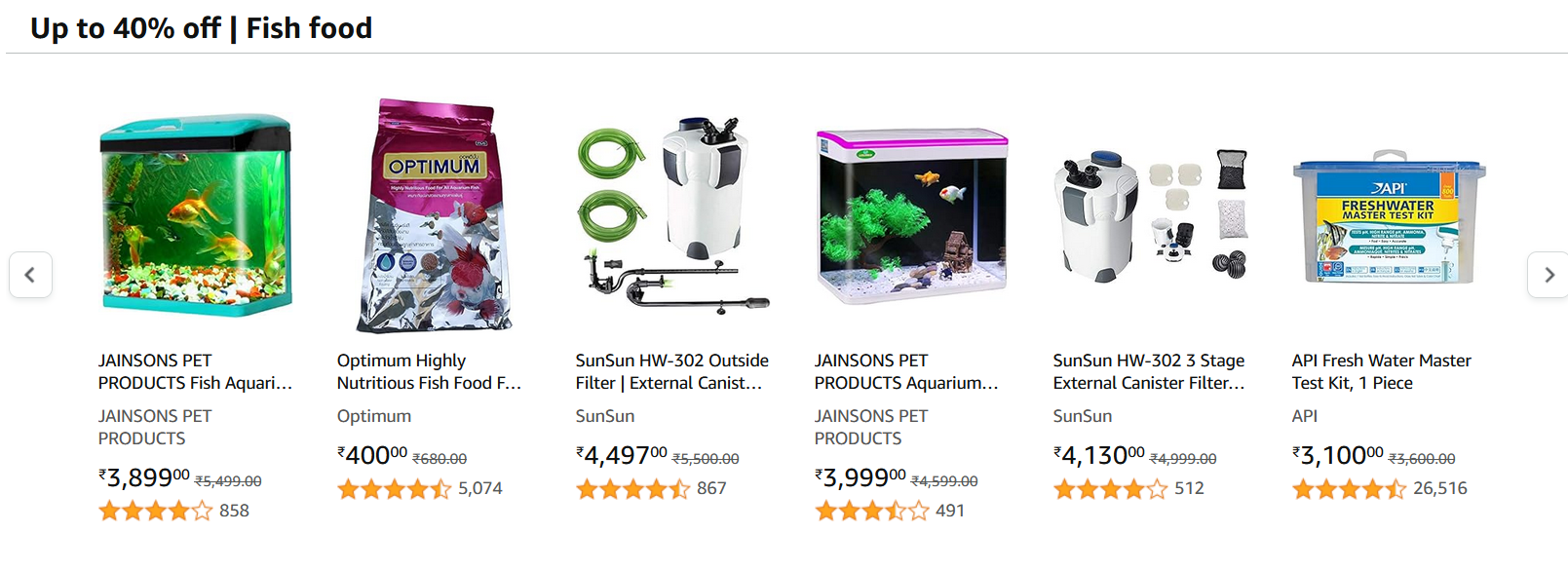কোনো দেশের ভূগোল তথা ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সেই দেশের ইতিহাসের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। বস্তুত, ভূগোল ছাড়া ইতিহাস পাঠ অনেকটা ফ্রেম ছাড়া ছবির মতোই। এখানে আরো মনে রাখা দরকার যে-কোনো দেশ বা জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে সর্বাগ্রে সেই দেশের যথার্থ ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ন্যায় আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। বহু যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ ইতিহাসে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।
ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিচয়
বর্ষং তম্ভারতং নাম ভারতী যত্র সস্তুতিঃ।।
ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বর্তমান। ভূপ্রকৃতিগত দিক থেকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলি হল :
১. হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ;
২. উত্তর ভারতের বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চল ;
৩. উপদ্বীপ অঞ্চল, যা আবার মধ্যভারতের উচ্চভূমি এবং উপদ্বীপীয় মালভূমি
—এই দুটি ভাগে বিভক্ত।
৪. উপকূলবর্তী নিম্নভূমি এবং
৫. প্রান্তদেশীয় সাগর ও দ্বীপসমূহ।
■ ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব (Geographical factors and their impact on Indian History) :
• ভৌগোলিক উপাদান : ভারতবর্ষ একটি বিশাল উপমহাদেশ। এটি রাশিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র ইউরোপের সমান এবং পৃথিবীর মধ্যে আয়তনের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এই উপমহাদেশের পশ্চিমে আরব সাগর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থান করায় এটি উপদ্বীপীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এশিয়ার বৃহত্তম উপমহাদেশ এই ভারতবর্ষকে ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে 'আর্যাবর্ত' ও 'দাক্ষিণাত্য’- এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একইভাবে 'আর্যাবর্তী'কে আবার প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : যেমন – (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমি অঞ্চল ও (৩) মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চল। আর ভারতের প্রাকৃতিক দাক্ষিণাত্যের দুটি প্রাকৃতিক বিভাগ হল— (১) দক্ষিণ ভারতের বিভাগ মালভূমি এবং (২) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ ও উপকূল অঞ্চল। এইভাবে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতবর্ষ পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পুরাণ-এর 'ভুবনকোষে ভারতবর্ষের ন'টি বিভাগের উল্লেখ রয়েছে। এই বিভাগগুলো । হল— কশেরুমান, কুমার (কুমারী), ইন্দ্রদ্বীপ, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব, গভস্তিমান, বারুণ এবং তাম্রবর্ণ। তবে এই বিভাজন অপেক্ষা প্রথমোক্ত পাঁচটি বিভাগকে বর্তমানে অধিকাংশ ঐতিহাসিক গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ মালভূমির দক্ষিণে মাদ্রাজ, কেরল, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ভাগকে “সুদূর দক্ষিণ" (Far— South) বলে চিহ্নিত করেছেন।
• ভৌগোলিক প্রভাব : কোনো দেশের ইতিহাস সেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এই ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক প্রভাব এক চিরন্তন সত্য ঘটনা। ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রার প্রণালী ও জীবনদর্শন সবটাই ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ফরাসি পণ্ডিত জন বোদিন (Bodin) যথার্থই বলেছিলেন, “প্রকৃতির সন্তান মানুষের জাতীয় চরিত্র গঠনে, কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী।" আবার আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক টয়েনবির (Toynbee) কথায় ইতিহাসের নায়ক মানুষ ভৌগোলিক উপাদানকে যেভাবে ব্যবহার করে, সেভাবেই সবকিছু নির্ধারিত হয় ("Geographical facts are the only fact as approached by man")।
* মানব সভ্যতার উত্থানে ভৌগোলিক প্রভাব ইতিহাসের সাথে এক অনিবার্য বন্ধনে আবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, নীলনদ না থাকলে মিশর সাহারা মরুভূমির গর্ভে হারিয়ে যেত। প্রাচীন গ্রিস ইজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগর পরিবৃত হওয়ায় গ্রিসের অধিবাসীরা বাণিজ্য ও নৌবিদ্যায় এত পারদর্শী। আবার অধ্যাপক জে. বি. বিউরি-র মতে, পর্বতসংকুল হওয়ায় প্রাচীন গ্রিসে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের পরিবর্তে অসংখ্য ছোটো ‘পলিশ” বা “নগর-রাষ্ট্র” (City-State) গড়ে ওঠে। অখণ্ড গণতান্ত্রিক চেতনার পরিবর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Self-control) জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে। আবার ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এত উন্নত। এই দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে আয়তনে প্রায় কুড়িগুণ বড়ো হল ভারতবর্ষ।
*হিমালয়ের প্রভাব ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতার উপর হিমালয়ের আশীর্বাদ অপরিমেয়। ঐতিহাসিক * কে. এম. পানিক্কর ('A Survey of Indian History' গ্রন্থে) বলেছেন, মিশরকে যদি “নীলনদের দান” বলা হয়, তবে ভারতবর্ষকে “হিমালয়ের দান" বলে উল্লেখ করলে কোনো অত্যুক্তি হবে না। তার কারণ হিমালয় ভারতকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আবার অন্যদিকে হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট নদীগুলো ভারতকে সুজলা- সুফলা-শস্য-শ্যামলা দেশে পরিণত করেছে। তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিভিন্ন গিরিপথ যেমন- খাইবার, বোলান, বানিহাল, গোমাল, কারাকোরাম, পিরপক্কাল প্রভৃতি বহির্ভারতের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে।
* বিন্ধ্য পর্বতের জন্য উত্তরে আর্যাবর্তের সঙ্গে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ার ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের একটা স্বাভাবিক ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। কিংবদন্তি আছে অগস্ত্য মুনি বিশ্বা পর্বত অতিক্রম করতে গিয়ে আর ফেরেননি। সেই জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে অজ্ঞাত স্থানে যাত্রাকে বলা হত অগস্ত্যযাত্রা বা শেষযাত্রা। তবে ভারতের ইতিহাসে এই পর্বতের সবচেয়ে বড়ো প্রভাব হল, দক্ষিণে 'দ্রাবিড় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এবং সৃষ্টি হয়েছে উন্নত ও মৌলিক শিল্প স্থাপত্য। বিদ্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে প্রথমে আর্যরা এসেছিল দক্ষিণে। তারপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আলাউদ্দিন খলজি, আকবর প্রমুখ বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে এলেও দ্রাবিড় সভ্যতায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থেকেই গেছে।
* ভারতের পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত হওয়ায় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হয়েছে। কারণ দুর্গম ও দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোনো জলদস্যুর আক্রমণ তেমনভাবে ঘটেনি। ড. রোমিলা থাপারের মতে, সমুদ্রসংলগ্ন হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের চোলরা সামুদ্রিক কার্যাবলিতে বিশেষত নৌবিদ্যা ও বাণিজ্যে এত বেশি পারদর্শী। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপনীত হলেও তিনি লুণ্ঠন করতে আসেননি। বরং তাঁর আগমনের পর জলপথ আবিষ্কার হওয়ায় ভারত শিল্প-বাণিজ্যের দিক দিয়ে বহির্বিশ্বের সান্নিধ্য লাভ করে। তারপর একে-একে পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি বণিকরাই জলপথে ভারতে এসেছিলেন।
* উত্তর ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমভূমির মধ্যে গাঙ্গেয় সমভূমিকে "ভারতের হৃৎপিণ্ড" বলা যেতে পারে। এই গাঙ্গেয় সমভূমির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,০০০ কিমি. সমভূমি ও নদনদীর এবং প্রস্থ ২৫০-৩০০ কিমি.। অনুকূল অনুপম এই সমভূমি অঞ্চলে, প্রভাব বিশেষত গঙ্গার তীর ধরে প্রাচীনকাল থেকে যে শহর, নগর, বন্দর, সাম্রাজ্য, ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি গড়ে ওঠে, তার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সভ্যতার জৌলুস বেড়েছে। ভারতমাতার সারা শরীরে অসংখ্য শিরা-উপশিরার মতো যেসব নদী রয়েছে ভারতের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় তারও প্রভাব বর্ণনাতীত।
* ভারতের দক্ষিণে পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম উপকূল মিলিয়ে মোট ৪৮২৭ কিমি. দীর্ঘ উপকূলরেখা রয়েছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকায় পূর্বঘাট পর্বতসংলগ্ন পূর্ব উপকূল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।




.png)