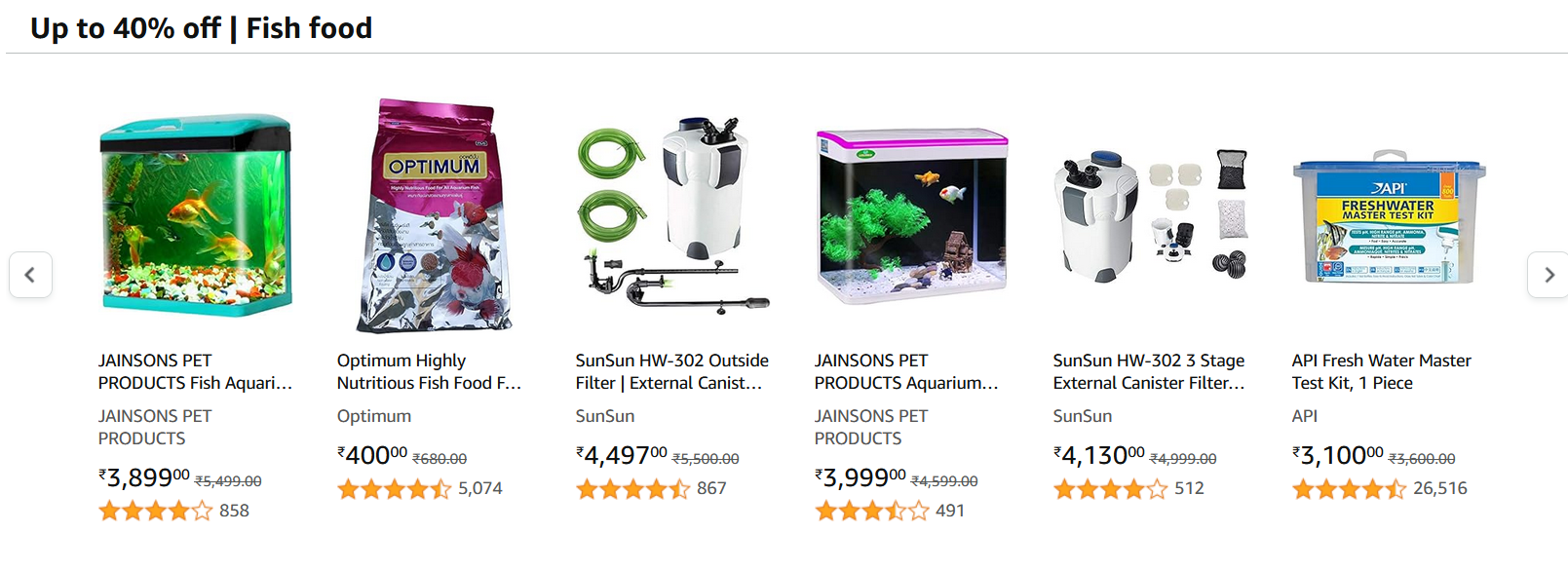চিংড়ি মাছ (Shrimp)
চিংড়ির দেহাকৃতি, আকৃতিক গঠন প্রভৃতি
চিংড়ি কয়েক রকম হয়। আমাদের চোখে যে সব চিংড়ি পড়ে সেগুলি একরকম নয়। এগুলি কয়েক প্রকার। যেমন—গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি। এখানে যে চিংড়ির বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, সেটি কিন্তু জলের বাগদা চিংড়ি এই চিংড়িকেই আমরা আদর্শ চিংড়িরূপে গণ্য করে বর্ণনা করছি।
-
চিংড়ির পরিবেশ (Habit and Habital) এই চিংড়ি যে কোন স্বাদু জলের পুকুরে, খালে, নদীতে পাওয়া যায়। এই সব স্থানেই কুচো চিংড়িও পাওয়া যায়। শুধুমাত্র বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায় নদী ও সমুদ্রের মোহনায় এবং লোনা ও স্বাদু মাঝামাঝি জলে। চিংড়িকে সর্বভূক বলা যায়। কারণ চিংড়ি সবরকম খাদ্যই খায়। বিশেষ করে পচা আবর্জনা, পচা লতা-পাতা। চিংড়ির স্বভাব হলো নিশাচরের মতো কারণ এরা রাতের অন্ধকারেই জলে বিচরণ করে খুব বেশী।
চিংড়িকে মাছ বলা ভুল। কারণ চিংড়ি মাছ নয়। মশা-মাছি, আরশুলা, কাঁকড়া প্রভৃতির মতো এরাও একটি পতঙ্গ জাতীয় (Insects) জলজ প্রাণী। এদের সবগুলিকে একসঙ্গে সন্ধিপদ প্রাণী বলা হয়। অতএব চিংড়ি হলো সন্ধিপদ প্রাণী।
চিংড়ির বহিরাকৃতি (External Structures) — চিংড়ি লম্বাটে ও অর্ধবৃত্তাকার এবং শেষের দিকটা অর্থাৎ ল্যাজের দিক কিছুটা সূচালো বা সূচীমুখ টার্টকা গলদা চিংড়ি কিছুটা নীলচে সাদা।
চিংড়ির বাইরের সারাদেহটা একটা শক্ত খোলসের দ্বারা আবৃত থাকে। এই খোলস চিংড়ির বহিঃকঙ্কাল জাতীয় বস্তু। অর্থাৎ এই খোলসকে চিংড়ির বহিঃকঙ্কাল বলা হয়। ইংরাজীতে বলা হয় Exeskeletan | চিংড়ির দেহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) শিরোবক্ষ (Cephalothorax) এবং (২) উদর (Abdomen)। এই দু'টি অংশ আবার তলার দিকে অনেক উপাঙ্গ বা দাঁড়া (Appandages) আবদ্ধ করে রাখে। এই দাঁড়ার আবার বিভিন্ন কাজ আছে। এই প্রত্যেকটি দাঁড়া আবার দুটি ভাগে বিভক্ত (Biramous)। চিংড়ির দাঁড়ায় বিভিন্ন রকম রূপান্তর দেখা যায়। তবে রূপান্তর দেখা গেলেও ওদের দাঁড়ার রূপান্তর মোটামুটি একই ধরনের। যেমন—(১) নিচের দ্বিধাবিভক্ত প্রোটোপোডাইট্ (Protopedite)-এর আবার ওপরের থাকে কক্সা (coxa), নিচে বেসিস (Basis) । বেসিস আবার দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ অর্থাৎ বাইরের ভাগটা এক্সোপোডাইট (Exepodite) এবং ভেতরের অংশটা এন্ডোপোডাইট (Endopodite) নামে অভিহিত।
শুধুমাত্র দাঁড়াই নয়, এছাড়াও চিংড়ির নিজের দেহের ওপর অনেকগুলি বর্ম বা আবরণী এঁটে বসে থাকে ।
চিংড়ির শিরোবক্ষ (Cephalothorax)
লম্বা নলের মতো দেখতে কিন্তু চওড়া এবং অবিভক্ত হয় সামনের অংশ। এই শিরোবক্ষ অর্থাৎ সিফালোথোরেক্সটি তৈরী হয়েছে মাথা ও বুক নিয়ে। বিবর্তনের পথে-চিংড়ির একটা অবিভক্ত অংশ এবং পরের চোদ্দটা অংশ একসঙ্গে মিশে এই শিরোবক্ষ অর্থাৎ সিফালোথোরেক্স তৈরী হয়েছে। অবিভক্ত অংশটাই বোঁটার ওপর চোখ দুটি আবদ্ধ রাখে। একটা শক্ত খোলস সমস্ত শিরোবক্ষকে ঢেকে রাখে। এই শক্ত খোলসটাকে বলা হয় ক্যারাসে (Carapace)। এই ক্যারাসে ধারের দিকে একেবারে তলার দিকে ঝুলে থাকে। এটি ঝুলে গিয়ে ফুলকো প্রকোষ্ঠকে (gill chamber) আবৃত করে রাখে। সেই সময় ওকে বলা হয় ফুলকো ঢাকনা। ইংরাজীতে বলা হয় gill cover বা branchiostegite। এই ফুলকো ঢাকনাটি একটি পাতলা আবরণ বা পর্দা দ্বারা তোলা বা নামানো যায় ৷ এই আবরণ বা পর্দাটির নাম Branchiostegal membrame। এগুলির তলার দিকটা অর্থাৎ ক্যারাপেস কতকগুলি পেয়ালার মত দেখতে স্টারনাল প্লেট (Sternal plate) দ্বারা ঢাকা থাকে।
শিরোবক্ষ এবং অন্যান্য আর সব যে জিনিসগুলি চিংড়ি মাছে পাওয়া যায়, তা
(ক) রোস্ট্রাম (Rostrum)
এটি হলো ক্যারাপেসেরই একটা অংশ। এটি ওপরে এবং মাঝামাঝি জায়গায় সোজাভাবে খাঁজ কাটার মতো এগিয়ে যায়। এই রোস্ট্রামের কাজ হলো আত্মরক্ষা করা । অর্থাৎ এর কাজ আত্মরক্ষামূলক।
(খ) চোখ (Eye) —
ঠিক রোস্ট্রামের তলার দিকে এবং ক্যারাপেসের দুদিকে একটি করে দুটি চোখ থাকে। চিংড়ির চোখ হলো কালো এবং দেখতে উপবৃত্তাকার। চিংড়ির চোখ দুদিকে দুটি হলেও একটি করে নয়—অনেকগুলি চোখের সমষ্টি। সেজন্য চিংড়ি মাছের চোখ হলো যৌগিক। এই যৌগিক চোখই হলো সন্ধিপদ প্রাণীর, অর্থাৎ Phylum Arthopoda প্রাণীর একটা বৈশিষ্ট্য। দুটি চোখই দুটি বোঁটার (Slak) দ্বারা আবদ্ধ। প্রত্যেকটি বোঁটা আবার ইচ্ছা মতো ঘোরাতে পারে। এই চোখের কাজ হলো অন্ধকারে সব কিছু অনসন্ধান করা।
(গ) কাঁটা (Spines)
চোখের পিছনেই ক্যারাপেসের দুদিকে দু'জোড়া করে এই কাঁটা থাকে। আগে থাকে দু'জোড়া আর পিছনের দু'জোড়া। আগের জোড়া কাঁটার নাম Antennal Spines এবং পিছনের জোড়ার নাম Hepatic Spines.
(ঘ) উপাঙ্গ চিংড়ির দেহের তলার দিকে দাঁড়ার সংখ্যা হলো তেরো জোড়া। এই দাঁড়াগুলির নাম হলো তাদের অবস্থান অনুসারে। যেমন সেফালো কথাটার অর্থ যদি হয় আগের অংশ বা মাথা, তাহলে ঐ অংশের সবগুলি দাঁড়ার নাম সেফালো (Cephalo) অনুসারে। যেমন প্রথম পাঁচ জোড়া হলো- সেফালিক উপাঙ্গ (Cephalic Appendages), First Antenna or Antennual. Second Antenna Manlible, First Maxilla Maxillula এবং Second Maxilla। অবশিষ্ট আট জোড়া দাঁড়ার নাম Thoracic Appendages (দাঁড়া)। এই থোরাসিক অ্যাপেনডেজেস এর আর একটি নাম হলো Periopods। বুকের দাঁড়াগুলির নাম হলো তিন জোড়া ম্যাক্লিনিকোডস (Maxillipeds) এবং পাঁচ জোড়া হাঁটার সাহায্যের জন্য দাঁড়া।
চিংড়ির শিরোবক্ষে বিভিন্ন ধরনের গর্ত (Different Apertures in cephalothorax)
-
(ক) মুখ চিংড়ির মুখ বলতে একটা দাগ চিহ্নের মতো। এটি থাকে সেফালো থোরাক্সের নিচে। এর আরো অবস্থান হলো তৃতীয় এবং চতুর্থ দেহাংশের মাঝখানে। খাবারের কাজে স্বাভাবিক ভাবেই চিংড়ি মুখ ব্যবহার করে থাকে ৷
(খ) রেচন মুখ (Renal Aperture)
খুবই ক্ষুদ্র মুখ থাকে প্ৰতি দ্বিতীয়, শুঁড়ের (Antenna)-র তলায় উঠে থাকা একটা প্যাপিলাতে। এর ভেতর দিয়েই চিংড়ি তার রেচন কাজটি করে থাকে। (গ) যৌন-মুখ (Gonopores) জোড়া জোড়া হিসাবে এই সব মুখগুলির অবস্থান নির্ভর করে চিংড়ি স্ত্রীজাতির বা পুরুষ জাতির ওপর। পুরুষের যৌন মুখ দেখা যায় হাঁটার পঞ্চম দাঁড়ার কবজির ভেতরের দিকে আর স্ত্রীজাতীয় চিংড়ির বেলায় একই জায়গায় দাঁড়াটা হবে তৃতীয় হাঁটবার দাঁড়াতে ৷ (ঘ) ভারসাম্যের মুখ (Statocyts opening) দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে চিংড়ি বাইরের সঙ্গে দুটি খুব ছোট ছোট গর্ত দিয়ে আদান প্রদান করে। এই গর্ত দুটি হল দ্বিতীয় শুঁড়ের (Second Antenna) মাঝে। চিংড়ির উদর (Abdomen) চিংড়ির মাছের উদর দুটি অংশে বিভক্ত। সবার পিছনদিকের অংশটির নাম টেল্সন (Telson)। প্রতিটি উদরের অঙ্গ ধারের দুটি অঙ্গ চাপা, এবং প্রত্যেকটি উদরাঙ্গে একটা করে গোলাকার খোলস (Exeskeleton) আছে, তার নাম হলো স্কেলেরাইট (Sclerite)। প্রত্যেকটি অঙ্গের স্কেলেরাইট পিছনের স্কেলেরাইটকে ঢেকে রাখে। একটি চূর্ণবিহীন অর্থাৎ ক্যালসিয়াম বিহীন আবরণ দ্বারা স্কেলেরাইট আবৃত থাকে। এই আবরণটির নাম হলো আর্থ্রোয়েডাল আবরণী (Arthroidal Membrane)। প্রতিটি স্কেলেরাইটের দুটি অংশ, তলার দিকে প্লেটের মতো স্টারনাম (Sternum) এবং ওপরে খিলানের টারগাম (Tergum) থাকে। টারগাম দুদিকে ঝুলতে থাকে—তাকে বলা হয় প্লেরন। এই প্লেরন (Pleuron) অপর দিকের দাঁড়ার সঙ্গে এপিমেরন (Epimeron) দ্বারা যুক্ত থাকে। প্রতিটি উদরাঙ্গের দুদিকে এক জোড়া করে দাঁড়া থাকে। ঐ দাঁড়া উদরাঙ্গের তলা থেকে বেরিয়ে আসে। এই দাঁড়ার নাম হলো প্লেওপল্ড্স (Pleupods) এবং শেষ জোড়াটি বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন এর নাম হয় ইউরোপড্স (Uropods)। প্রথম দিকের পাঁচটি 1 চিংড়ির সন্তরণের দাঁড়া (Pleupods or Swimes) উদরাঙ্গে এক জোড়া করে দাঁড়া থাকে। একে বলা হয় (Pelupods)। প্রত্যেকটি প্লেওপড় প্রচেষ্টা পোডাইট এর বেসিসকক্সা থেকে লম্বায় বড়। এক্লোপোডাইড এণ্ডোপোডাইটের চেয়ে বড় হয়।দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্লেওপড এর ভেতরে আছে একটি অতিরিক্ত হুকের মতো তার নাম অ্যাপেনডিক্স ইন্টারনা (Appendix Interna)। এইসব হুকগুলি একত্রে মিশে একটা বাড়ির মতো তৈরী করে। এটি স্ত্রী চিংড়ির বেলাতেই হয়। এরই সাহায্যে স্ত্রী-চিংড়ি ডিম বহন করে থাকে। পুরুষ চিংড়ির দ্বিতীয় প্লেওজাড় ছাড়াও অতিরিক্ত অ্যাপেণ্ডিক্স ম্যাসকুলাইন (Appendix Masculine ) থাকে।
-
চিংড়ির ইউরোপড্ (Uropod) চিংড়ির একজোড়া ইউরোপড থাকে একবারে শেষ উদরাঙ্গে ঠিক টেলসনের দুটি ধারে (Telson)। ইউরোপড্ চিংড়িকে দিক পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এরই সাহায্যে চিংড়ি পিছন দিকে লাফায় ।
চিংড়ির পায়ুর অবস্থান হলো ওর দেহের তলার প্রায় টেলসনের গোড়ার দিকে ।
চিংড়ির চলাফেরা (Locomotion )
চিংড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তিনভাবে। গুঁড়ি মেরে, সাঁতার কেটে ও ঝাঁপিয়ে। গুঁড়ি মেরে যখন যায়, তখন চিংড়ি তার দেহকে টান টান করে ফেলে অর্থাৎ একেবারে সোজা করে ফেলে এবং নিজের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে পাঁচ জোড়া হাঁটার দাঁড়ার ওপর। পাগুলি ছন্দোবদ্ধভাবে এগিয়ে যায় এবং অনুভূতির শুঁড় (Feeler) সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। সন্তরণ দাঁড়াগুলি (Swimmereto) ঠিক প্যাডেলের মতো জলের তলায় ঘোরে এবং ঠিক নৌকার
বৈঠার মতো কাজ করে।
চিংড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ হলো বিপদকে এড়িয়ে যাওয়া। এইভাবে ঝাঁপ দিয়ে যাবার সময় চিংড়ি দেহটা বাঁকিয়ে আনে সেফালোথোর্যাক্সের তলায়। তারপরেই চিংড়ি তার ইউরোপড এর ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তার ফলে চিংড়ি পিছনে যায় ধাক্কার সাহায্যে। এই ধাক্কায় বেশ কিছুটা ছিটকে যায় পিছন দিকে। চিংড়ির পরিপাক প্রণালী (Digestive System)
চিংড়ির পরিপাক পদ্ধতিতে দুটো জিনিস দেখা যায়। এই দুটো জিনিসের ওপরেই চিংড়ির পরিপাক পদ্ধতি 'নির্ভর করে। সে দুটো হলো—(ক) পরিপাক নালী এবং (খ) হজম গ্রন্থি ।
(ক) পরিপাকনালী আবার তিনভাগে বিভক্ত। যেমন—অগ্রপরিপাক নালী, মধ্য পরিপাক নালী এবং পশ্চাৎ পরিপাক নালী ।
অগ্র পরিপাক নালী (Fare Gut )
-
এতে যে অংশগুলি থাকে সেই
Tags
ইতিহাস
Bengali
Class 1
Class 10
Class 11
Class 12
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 7
Class 8
Class 9
Class B.A
Class B.ED
Class D.ED
Class M.A
Class P.G
Class PHD
Class U.G



.png)