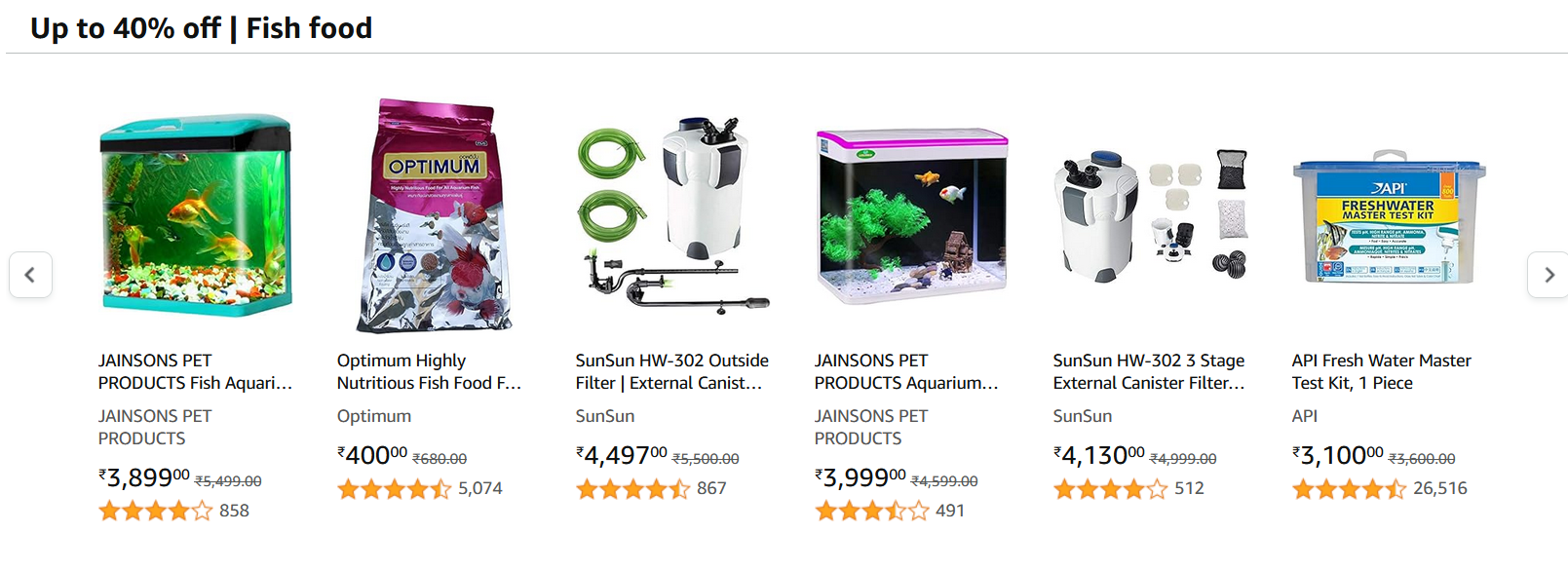বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভবOrigin of Bengali race and Bengali language In Bengali
বঙ্গ নাম
'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'। উত্তরে তার হিমালয়, পূর্বে ও পশ্চিমে কঠিন শৈলভূমি, দক্ষিণে সমুদ্রে মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ শ্যামল সমতলভূমি বঙ্গদেশ নামে খ্যাত । ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও আছে, কিন্তু প্রাচীন যগে সমগ্র বাংলা দেশের নাম বঙ্গ ছিল না; বস্তুত কোনো বিশিষ্ট নামেই বর্তমান ভৌগোলিক সীমাটি পরিচিত ছিল না। বঙ্গ, পাণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ় ইত্যাদি নামে এক একটি জনপদ বা অঞ্চল অভিহিত হত। মাসলমান আমলেই 'সবা বাংলা' অথবা 'বাঙ্গালা' নামে সমগ্র প্রদেশটি পরিচিত হল । পর্তুগীজদের কাছে ফারসী 'বঙ্গালহ' একট, বিকৃত হয়ে দাঁড়াল 'বেঙ্গলা', যার থেকে ইংরেজরা 'বেঙ্গল' নামটি খাঁজে পেল। একাদশ-দ্বাদশ শতক থেকে 'গৌড়' নামেও -অবশ্য দেশটি অভিহিত হত।
জাতি :
কোন সন্দেরে কালে বাংলায় মনষ্য বসতির সচেনা হয় সে সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। বাংলার ইতিহাস চতুর্থ দশকের আগে রচিত হয় নি। ত কিছ, সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, যার থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে সভ্যতার আদিযুগেও বাংলা দেশে জনবসতি ছিল।
আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্র দিয়েই পৃথিবীর সর্বত্র মানষের অস্তিত্ব
প্রমাণিত হয়। আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে আদিযুগে, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের
পরিসমাপ্তি ঘটে। সে-যুগেরও পাথরের তৈরি নানা হাতিয়ার পাওয়া গেছে বাঁকড়া
মেদিনীপর ও বর্ধমানের নানা অঞ্চল থেকে। সুতরাং অনমিত হয়, বাংলায় তখনো ছিল
মানষের বসবাস ।
নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্র পালিশ করা। এযুগের মানষে জানত আগুনের ব্যবহার।
সুতরাং রন্ধনকৌশল যেমন আয়ত্ত ছিল তেমনি মাটি পাড়িয়ে বাসন তৈরির কৌশলও
অজ্ঞাত ছিল না। ক্রমে তারা তামা (তামাযুগে) ও লোহার ব্যবহারও শিখেছিল। এই
যুগের অস্ট্রিক ভাষাভাষী নরগোষ্ঠী যারা নিষাদ' জাতি নামেও পরিচিত, তারাই বাঙালীর পূর্বপুরুষ। কোল শ্রেণীর শবর, মন্ডা, সাঁওতাল এবং হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল এদেরই বংশধর ।
অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা ছিল কৃষিজীবী এবং শিকারোপজীবী। ধান, কলা, লেব,, পাট, বেগুন ইত্যাদি বাঙালীর প্রিয় খাদ্য এবং তুলার চাষ বাংলা দেশে শর করেছিল এরাই।
নিষাদ জাতির পরে আসে দ্রাবিড় ও ব্রহ্মতিবতীয় ভাষাভাষীরা। দ্রাবিড়রা নগরসভ্যতার সৃষ্টিকর্তা এবং বর্শা ছারি ইত্যাদি লৌহ-নির্মিত অস্ত্র ও তামার রকমারি জিনিসের আবিষ্কর্তা। বাঙালীর নরতত্তে এই দুই ভাষা-গোষ্ঠীর প্রভাব আজও পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নি। তবে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অজয় কনের ও কোপাই নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্ভবত, আর্য আগমনের (খত্রীঃ পূঃ ১৫০০ ) আগেই এই সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল। অসম্ভব নয়, এই সভ্যতা দ্রাবিড়দেরই দান।
দ্রাবিড়ভাষীর পর এল আলপীয় আর্যরা। এরা আর্য হলেও বৈদিক আর্য বা নডিক শাখা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণ ভক্ত হিন্দরে পূর্বাপরষে এরাই। ফলত, সমগ্র আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণেরা নর্ডিক শাখার বংশধর বলে দীর্ঘশির হলেও বাঙালী ব্রাহ্মণ প্রশস্ত-শির।
খীস্টীয় প্রথম শতকে অথবা তারও আগে বাঙালী তার স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা করেও যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার ইত্যাদি উপলক্ষে বৈদিক আর্য' অথবা 'নডিক' শাখার সংস্পর্শে আসে। বাংলা ছাড়া সমগ্র আর্যাবর্তে ছিল তাদের বসবাস। বাংলাদেশে তাদের বসবাস নিষিদ্ধ হলেও রুদ্ধ হয় নি। বাংলাদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি হলে ( ৪র্থ শতক ) এই আগমন হল অবাধ। বাংলা ও বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘটল আর্যীভবন, বৈদিক আর্য-প্রভাব বাংলাদেশে দৃঢ়তর হল ।
অস্ট্রিক ভাষাভাষীরা ছিল খর্বাকার। এদের নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রং কাল, মাথার চাল ঢেউ খেলানো। সাঁওতাল, লোধা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড় ভাষী জনসমাজের গড়ন পাতলা, রং ময়লা এবং নাক ছোট। দক্ষিণ ভারতে এই গোষ্ঠীর লোক দেখা যায়। আলপীয় আর্যদের নাক লম্বা, রং ফর্সা, মুখে গোলাকার এবং উচ্চতা মধ্যম। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী এই গোষ্ঠীর লোক। নর্ডিক আর্য দীর্ঘকায়, ফর্সা, সরু ও লম্বা নাকবিশিষ্ট। এরা যথেষ্ট বলিষ্ঠ। খাপ পনেরশ' অব্দের কাছাকাছি সময়ে এদেরই একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম ভারতে পঞ্চনদের তীরে এসে বসবাস করে। রুমে এরা সমগ্র আর্যাবর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ঋগ্বেদ রচনার কৃতিত্ব এদেরই। বাংলাদেশে এরা দীর্ঘকাল প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। একসময়ে এই প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। প্রবেশ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, নতুবা হত সমাজচ্যতে। কারণ, বাংলাদেশে তখন ছিল
অবশেষে গতযুগে আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চল থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।
সেজন্যে
স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র ভাষা। থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এসে
বাংলায় তাঁদের জমিজমাও দান করা হয়েছিল। এভাবে ঘটল বাংলায় আর্যভবন । এর
আগে বাংলা দেশে বৃত্তিভিত্তিক চবর্ণ ছিল না। কিন্তু 'বহদ্ধর্ম পুরাণে'র
সাক্ষ্যে জানা যায়, সেন আমলে বা তারও কিছু আগে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের
সৃষ্টি হয়। তিনভাবে এই জাতপ্রথা গড়ে ওঠে—পেশা, কর্ম ও নৃতাত্ত্বিক
গোষ্ঠীগতভাবে। বর্তমান বাঙালী সমাজের জাতিবিন্যাস গড়ে উঠল এভাবে। সেইসঙ্গে
জাতি ভেঙে বিভিন্ন 'জাতে'রও (কথায় বলে ছত্রিশ জাত) সৃষ্টি হল। অননুসারে
অভিজাত ও অন্ত্যজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হল সমাজ ।
পুরুষান ক্রমিক বৃত্তি
অবশেষে গতযুগে আর্যাবর্তের বিভিন্ন অঞ্চল থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।
সেজন্যে
স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র ভাষা। থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এসে
বাংলায় তাঁদের জমিজমাও দান করা হয়েছিল। এভাবে ঘটল বাংলায় আর্যভবন । এর
আগে বাংলা দেশে বৃত্তিভিত্তিক চবর্ণ ছিল না। কিন্তু 'বহদ্ধর্ম পুরাণে'র
সাক্ষ্যে জানা যায়, সেন আমলে বা তারও কিছু আগে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের
সৃষ্টি হয়। তিনভাবে এই জাতপ্রথা গড়ে ওঠে—পেশা, কর্ম ও নৃতাত্ত্বিক
গোষ্ঠীগতভাবে। বর্তমান বাঙালী সমাজের জাতিবিন্যাস গড়ে উঠল এভাবে। সেইসঙ্গে
জাতি ভেঙে বিভিন্ন 'জাতে'রও (কথায় বলে ছত্রিশ জাত) সৃষ্টি হল। অননুসারে
অভিজাত ও অন্ত্যজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হল সমাজ ।
পুরুষান ক্রমিক বৃত্তি
জাতির পরিচয় নরত, জনতন্ত্র, সমাজতত্তের মতো ভাষাতত্তের সাহায্যেও জানা যায়।
বাঙালীর কৃষি ও তার পদ্ধতি অস্ট্রিকভাষীদের দান। তাই বাঙালীর প্রিয় কষিসম্পদের নাম অস্ট্রিক ভাষা থেকেই আগত। ধান, তুলা, পান, হলদে, নারকেল ও নানা জাতীয় সবজির সঙ্গে লাঙল, কার্পাস কম্বল সব শব্দের মলে অস্ট্রিক শব্দ । কড়ি, গণ্ডা ইত্যাদি সংখ্যাগণনারীতিও অস্ট্রিকভাষীদের কাছ থেকে পাওয়া । দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণরীতি বাংলাভাষায় প্রবেশলাভ করেছে । আর বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দই তো সংস্কৃতমলে। সতরাং ভাষার ক্ষেত্রে বৈদিক আর্যদের দান অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত।
জাতির পরিচয় জানার আর একটি উপায় গ্রন্থাদির নানা উল্লেখ। বৈদিক আর্যরা মনে করতেন বঙ্গভূমি 'দেশোহনাৰ্যনিবাসঃ'-অনার্যদের নিবাসস্থান। বাঙালীদের সম্পর্কে" তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অবজ্ঞার। 'আচারঙ্গসূত্রে' মহাবীরের (খলীঃ পঃ ৬০০) এদেশে এসে বিপত্তিতে পড়ার কথা বলা হয়েছে। বৌধায়নের ধর্মসূত্রে পাণ্ডু ও বঙ্গ জনপদে কিছুকালের জন্য থাকলেও প্রায়শ্চিত্তের ( ব্রাত্যষ্টোম ) বিধান দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি স্বীকৃতি পেল । মনসংহিতার কাল থেকে খীঃ পঃ ২০০ - খীঃ ২০০-এর মধ্যে) বঙ্গদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হল। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে (খীঃ পঃ ৩২৭ ) 'গাঙ্গরিদাই' নামে এক সাহসী জাতির বঙ্গদেশে অবস্থানের কথা বলেছেন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ । 'আর্য'মঞ্জ, শ্রীম, লকল্পে' (অষ্টম শতক) বঙ্গবাসীকে বলা হয়েছে অসার ভাষাভাষী।
‘জনপ্রবাহ তো একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা; তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায় না।' তব্দ প্রত্ন-নর জন-সমাজ ভাষাতত্ত্ব বিচারে ও নানা উল্লেখে জানা যায় গেপ্রবাহের বিভিন্ন তরে অন-আর্য ও আর্যের মিলনে বর্তমান বাঙালী জাতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
আর্যীভবনের পরে তা স্পষ্টত দৃশ্য না হলেও বাঙালীর
উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। সে পরিচয় গোপন থাকেনি।
বাঙালীর মনের ভাব প্রকাশের ভাষা বাংলা ভাষা। বাঙালী জাতির উদ্ভব
যাগপরম্পরায় কয়েকটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকের মিলনে, বাংলা ভাষাতেও স্বভাবতই সেই
ভাষাগুলির প্রভাব বর্তমান। ভবে, আর্য আগমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাচীন
অধিবাসীরা যেমন আর্য' সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই বরণ করে নিয়েছিলেন, তেমনি ভাষার
ক্ষেত্রেও আর্য ভাষাই হয়েছিল বাঙালীর ভাষা; অস্ট্রিক দ্রাবিড় ইত্যাদি
ভাষাগুলি শব্দ ও ব্যাকরণরীতিতে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল মাত্র।
দ্বিতীয় স্তর : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা: পার্লিখনীঃ পঃ ৬০০-খীঃ পঃ ২০০
প্রাকৃত খীঃ পূঃ ২০০-৬০০ অপভ্রংশ — খীঃ ৬০০-১০০০
তৃতীয় স্তর : নব্যভারতীয় আর্যভাষা : বাংলা ও অন্যান্য ভাষা-খা: ১০০০- বাংলা দেশে প্রথমে প্রচলিত ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আলপীয় আর্যশাখার ভাষা। কালক্রমে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির অন প্রবেশের আগেই বণিক ও সাধদের মাধ্যমে বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রবেশলাভ ঘটল। চাও চলল বিশেষ যত্নের সঙ্গে । পরবর্তীকালে আর্যাবর্তোর ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে বাধাহীন আগমনের ফলে (খীস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে) এই চর্চায় আগ্রহ দেখা দিল অনেক বেশি পরিমাণে। বস্তুত, আর্য ভাষাই হল বাঙালীর ভাষা, তা-ই ক্রমপরিবর্তিত হয়ে জন্ম নিল বাংলা ভাষা । আদিতে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষা ছিল অভিন্ন। কালক্রমে তারা আপন বাস্তব্য অর্জন করে।
ভাষাস্তরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :
আর্যীভবনের পরে তা স্পষ্টত দৃশ্য না হলেও বাঙালীর
উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। সে পরিচয় গোপন থাকেনি।
বাংলা ভাষার উদ্ভব
ভাষা :
যাগপরম্পরায় কয়েকটি ভাষাগোষ্ঠীর লোকের মিলনে, বাংলা ভাষাতেও স্বভাবতই সেই
ভাষাগুলির প্রভাব বর্তমান। ভবে, আর্য আগমণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার প্রাচীন
অধিবাসীরা যেমন আর্য' সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই বরণ করে নিয়েছিলেন, তেমনি ভাষার
ক্ষেত্রেও আর্য ভাষাই হয়েছিল বাঙালীর ভাষা; অস্ট্রিক দ্রাবিড় ইত্যাদি
ভাষাগুলি শব্দ ও ব্যাকরণরীতিতে তাকে সমৃদ্ধ করেছিল মাত্র।
আর্যজাতি (নর্ডিক গোষ্ঠী) খীস্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে ইরান ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁদের বসতি ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবে। হাজার বছরের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়া সমগ্র আর্যাবর্তে তাঁদের বসতি বিস্তৃত হয়। এই আর্যরা রচনা করেন বেদ এবং বিভিন্ন উপনিষদ ও পরাণ। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার এ স্তরটিকে বলা হয় আদি-ভারতীয় আর্য ভাষা ( Old Indo Aryan ) । এ ভাষার কালসীমা খীস্টপূর্বে পনের শতক থেকে খীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ।
তখনো লিপি আবিষ্কৃত হয়নি। সবই ছিল শ্রুতিনির্ভর। লিপি আবিষ্কারের পর এগুলি লিপিবদ্ধ হয় বলে এগুলিকে লেখ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
এই লেখ্য বৈদিকের সঙ্গে প্রচলিত ছিল জনসাধারণের মুখের ভাষা 'কথিত বৈদিক'। এই কথিত বৈদিক ভাষা ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে রুমে পরিবর্তিত হতে থাকে। তার ফলে সৃষ্টি হয় কয়েকটি প্রাকৃত ভাষার। মাগধী প্রাকৃত তাদেরই অন্যতম । প্রাকৃত ভাষাও ক্রমরপোত্তরের মধ্য দিয়ে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি করে। প্রাকৃত ভাষার নাম অনুসারে অপভ্রংশ গুলিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, মাগধী প্রাকৃত- মাগবী অপভ্রংশ ইত্যাদি। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই আর্যাবর্তের বিভিন্ন ভাষার জন্ম। বাংলাভাষার জননী মাগধী অপভ্রংশ ।
ভাষার বিবর্তনের তিনটি স্তরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :
প্রথম স্তর : আদি ভারতীয় আর্য ভাষা : খণ্ডীঃ পূঃ ১৫০০ - খীঃ ৬০০ দ্বিতীয় স্তর : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা: পার্লিখনীঃ পঃ ৬০০-খীঃ পঃ ২০০
প্রাকৃত খীঃ পূঃ ২০০-৬০০ অপভ্রংশ — খীঃ ৬০০-১০০০
তৃতীয় স্তর : নব্যভারতীয় আর্যভাষা : বাংলা ও অন্যান্য ভাষা-খা: ১০০০- বাংলা দেশে প্রথমে প্রচলিত ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আলপীয় আর্যশাখার ভাষা। কালক্রমে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির অন প্রবেশের আগেই বণিক ও সাধদের মাধ্যমে বাংলায় সংস্কৃত ভাষার প্রবেশলাভ ঘটল। চাও চলল বিশেষ যত্নের সঙ্গে । পরবর্তীকালে আর্যাবর্তোর ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে বাধাহীন আগমনের ফলে (খীস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে) এই চর্চায় আগ্রহ দেখা দিল অনেক বেশি পরিমাণে। বস্তুত, আর্য ভাষাই হল বাঙালীর ভাষা, তা-ই ক্রমপরিবর্তিত হয়ে জন্ম নিল বাংলা ভাষা । আদিতে বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষা ছিল অভিন্ন। কালক্রমে তারা আপন বাস্তব্য অর্জন করে।
ভাষাস্তরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে :
ইন্দো-ইউরোপীয়
সতেরাং, কথিত বৈদিক ভাষার আদি মধ্য ও নব্য তিনটি স্তরে ক্রমবিবর্তনের ফলেই জন্মলাভ করেছে আর্যাবর্তের অন্য সকল ভাষার মতোই বাঙালীর ভাষা, বাংলা ভাষা।
বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও যুগ-বিভাগ
কথিত বৈদিক ভাষার ক্রম-পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে খনীস্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে। বাঙালীর সৌভাগ্য ভাষার জন্ম লগ্নেই বাংলা- ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার ফলেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে দ্রুত।
বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও যুগ-বিভাগ
কথিত বৈদিক ভাষার ক্রম-পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে খনীস্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়ে। বাঙালীর সৌভাগ্য ভাষার জন্ম লগ্নেই বাংলা- ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। তার ফলেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছে দ্রুত।
ভাষাগত পরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলাভাষাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়- আদি, মধ্য ও আধুনিক যুগ। আদিস্তরের কালসীমা দশম থেকে "বাদশ শতক, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে বিশিষ্ট আসন সংগ্রহ
করে বাঙালীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করল বিশ্বে। স্বাধীনতা লাভের লগ্নে দেশ
বিভাগের ফলে বাংলাদেশ হল দ্বিখণ্ডিত। অভ্রচড় বনপতি বাংলাসাহিত্য তব, তার
শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে উনিশ শতকীয় বাঙালী মনীষীর নির্দেশিত পথেই,
যার ভিত্তি উদার মানবপ্রেম।
বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের সমকালে সামাজিক পটভূমি
বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে রচিত সাহিত্য
করে বাঙালীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করল বিশ্বে। স্বাধীনতা লাভের লগ্নে দেশ
বিভাগের ফলে বাংলাদেশ হল দ্বিখণ্ডিত। অভ্রচড় বনপতি বাংলাসাহিত্য তব, তার
শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে উনিশ শতকীয় বাঙালী মনীষীর নির্দেশিত পথেই,
যার ভিত্তি উদার মানবপ্রেম।
বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের সমকালে সামাজিক পটভূমি
বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব' দশম থেকে দ্বাদশ এই দুই শতক জুড়ে বিস্তৃত। এই কালসীমায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশীয়েরা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজারা বাংলায় রাজত্ব করতেন। পাল যুগে বাংলাদেশে বর্তমান জাতিবিন্যাস দেখা দেয়নি, দেখা দিল সেন আমলে। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মে'র পোষকতা করায় সমাজশাসনে, রীতিনীতিপালনে ব্রাহ্মণদের বিধান অতিরিক্ত মূল্য পেল। কথিত আছে সেনরাজ বল্লাল সেন বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ফলত, ব্রাহ্মণ সমাজ নতেনভাবে সংগঠিত হয়। এইসব কারণে বাংলাদেশে সেন আমলে নানা জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। এই সময়ের কিছন পরে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' তার বিস্তৃত তালিকা আছে। সেন আমলে শখে, কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন-ই হয়নি, সমাজে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির স্থানও নির্দিষ্ট হয়েছে। ফলে উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর, অধমসংকর ইত্যাদি জাতিবিন্যাস দেখা গেল । আমাদের পূর্ববর্তী দান ছিল জাতিবিভাগ, তার সঙ্গে যুক্ত হল জাতপাত-বিচার ।
সমাজের উচ্চবর্ণ অননুরক্ত ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি। তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও অনভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল দুটি অবৈদিক লোকায়ত ধর্মের প্রভাব । তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে'র রূপান্তরিত শাখা সহজযান এবং শৈবপন্থী নাথধর্ম' শখে, সমাজেই স্থান সংগ্রহ করল না, সাহিত্য রচনাতেও কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল ।
বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে রচিত সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে'র একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত গান বা পদাবলী। নিজ ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই গানগুলি রচনা করেননি, কারণ ধর্মমতকে গোপন রাখাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সেজন্য গানগুলি রচনা করেছিলেন একটি সাংকেতিক ভাষায়, যার নাম সন্ধ্যা ভাষা ।
সমাজ ব্যবস্থায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অথবা কবিস,লভ আন্তরিক প্রেরণাতেও গানগুলি রচিত হয়নি। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধকেরা নিগড়ে সাধনপদ্ধতির কথা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন গানে। কিন্তু সেই সংযোগে বাঙালী সংস্কৃতির হয়েছে অকল্পনীয়।
উপকার। বাঙালী পেয়েছে বাংলা ভাষার আদি লগ্নের ভাষার নিদর্শন, সেই সঙ্গে
সাধনপ্রক্রিয়া বর্ণনার আড়ালে তথ্যভিত্তিক সমকালীন সমাজচিত্র। ধর্মভিত্তিক
সাধন সঙ্গীত প্রাক-আধুনিক যুগের বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য। তারও সচনা
চর্যাগীতিতে। বাংলা সাহিত্য তার প্রকৃতির সন্ধান পেল সচনালগ্নে - বাংলা
সাহিত্যের পক্ষে এ কম গৌরবের কারণ নয়, তার শুভ ফলও দেখা গেছে পরবর্তী
সাহিত্যে।
উপকার। বাঙালী পেয়েছে বাংলা ভাষার আদি লগ্নের ভাষার নিদর্শন, সেই সঙ্গে
সাধনপ্রক্রিয়া বর্ণনার আড়ালে তথ্যভিত্তিক সমকালীন সমাজচিত্র। ধর্মভিত্তিক
সাধন সঙ্গীত প্রাক-আধুনিক যুগের বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য। তারও সচনা
চর্যাগীতিতে। বাংলা সাহিত্য তার প্রকৃতির সন্ধান পেল সচনালগ্নে - বাংলা
সাহিত্যের পক্ষে এ কম গৌরবের কারণ নয়, তার শুভ ফলও দেখা গেছে পরবর্তী
সাহিত্যে।
দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নাথধর্মের প্রভাব বিস্তৃত থাকলেও তার সেকালের কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এই সাহিত্য 'লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মাখে মুখে যগে পরম্পরায় আত্মরক্ষা করেছে, সেইসঙ্গে ভাষাগতভাবে পরিবর্তিতিও হয়ে গেছে। [ বস্তুত, 'মীনচেতন', গোরক্ষ বিজয়', 'গোর্খ' বিজয়'। 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' অথবা 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ভাষা বিচারে সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দশম-দ্বাদশ শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নাথ ধর্মের গল্পে, গোরক্ষনাথের মহিমার কাহিনী প্রচলিত ছিল। সাতরাং অনদমিত হয়, বাংলা দেশের কাহিনীগুলিও সমকালে রচিত ।
Tags
ইতিহাস
Bengali
Class 1
Class 10
Class 11
Class 12
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 7
Class 8
Class 9
Class B.A
Class B.ED
Class D.ED
Class M.A
Class P.G
Class PHD
Class U.G




.png)