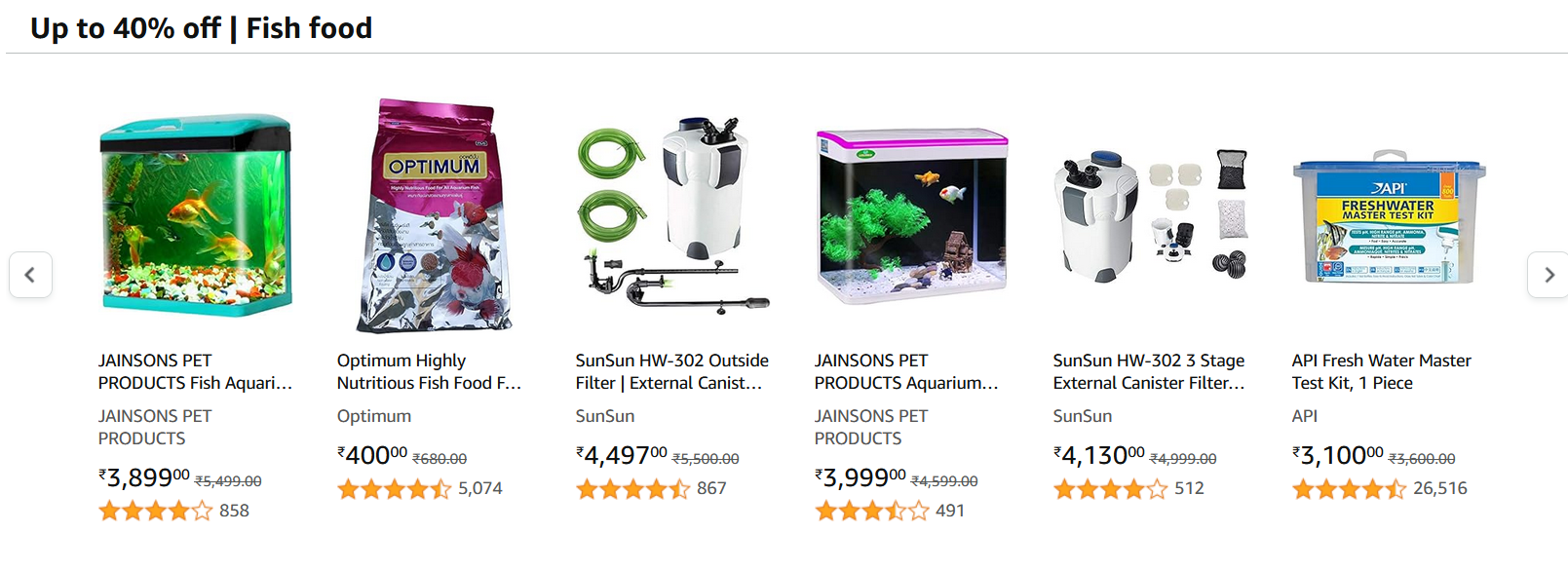সম্ভবত ২৭৩ খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্দে বিন্দুপারের মৃত্যু হলে পুত্র অশোক নগধ সাআাজ্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় চার বৎসর পরে; এই বিলম্ব নিয়ে পণ্ডিতের| অনেক,গবেষণা করেছেন। শোনা যায় যে পিতার জীবদ্দশায় অশোক তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্ধ পরিচালনায় লিপ্ত ছিলেন। পিতা মৃত্যুশয্যায় জানতে পেরে উজ্জয়িনী থেকে তিনি পাটলিপুত্রে উপস্থিত হন এবং পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। ভাইবোন অশোকের ছিল অনেক ; কিন্তু মনে হয় যে কোনও কোনও কাহিনীতে নিরানব্বইজন ভাইকে অশোক হত্যা করেছিলেন বলে যে রটনা আছে তা কাল্পনিক। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার চরিত্রে যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল, চণ্ডাশোক কেমন করে | ধৰ্মাশোকে পরিণত হলেন, একথা প্রমাণ করার জন্য ও ধরনের উদ্ভাবন ও অতিৰঞ্জন কাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে । তবে হয়তো একথা সত্য যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রতিদন্দিতা উপলক্ষ্যে অশোকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘটে) পরে শিলালিপিতে, আত্মীয়স্বজনের প্রতি দুব্যবহারের রেওয়াজ কিছুকাল ধরে বাড়ছে--একথ| যে অশোক বলেছিলেন, তার হয়তো বিশেষ একটা তাৎপর্য রয়েছে।
অশোকের শিলালিপিতে সাধারণত তাকে বলা হয়েছে-_-“দেবানাম্ পিয় পিয়দসি” ( দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী ): পিতামহ smeza নাকি এই “প্রিয়দর্শী” উপাধি প্রচলিত ছিল। “দেবানাম্ প্রিয়” এই আখ্যারও গুরুত্ব রয়েছে । বৌদ্ধধর্মের কোনও স্বকীয় দেবতা ছিল না; তাই দেবগণ বলতে হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী প্রচলিত দেবতার কথাই ভাবতে হবে। কোনও কোনও পণ্ডিত অশোকের সঙ্গে তুলনা করেছেন রোমান সম্রাট কন্স্টান্টাইন-এর ; কিন্তু কন্ট্রাণ্টাইন যেভাবে শ্রষ্টগর্মে দীক্ষিত হয়ে তাকে সাম্রাজ্যের ধর্ম বলে ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষে তার IIRA কিছু ঘটে নি। গৌতম বুদ্ধের মতোই তাঁর এই সম্রাট-ভক্ত হিন্দু ভারতের এতিহ থেকে pre হন নি; তাই “দেবগণের প্রিয়” উপাধি গ্রহণে কোনও সঙ্কোচ অশোকের মনে উদয় হয় নি, তাই ব্ৰাহ্মণ, শ্ৰমণ এবং অন্যান্য সন্নাসীকে সমভাবে দান করার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি তিনি দেখেন নি।
ধারাবাহিকভাবে, কালক্রম বজায় রেখে, অশোকের রাজ্যকালের বিবরণ আমরা জানি না। কিন্তু তার কলিঙ্গ বিজয়, সাম্ৰাজ্য সীমা, বৈদেশিক সম্পর্ক, শাসনব্যবস্থা, ধর্মপ্রচার কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে বহু সংবাদ আমর! রাখার স্থযোগ পেয়েছি । পর্বতগাত্রে, গুহাভ্যন্তরে, শিলা! ফলকে এবং স্তম্ভোৎকীৰ্ণ অবস্থায় যে শিলালেখ বহু বিদ্বানের একান্ত নিষ্ঠায় আবিষ্কৃত ও অধীত হয়েছে, যার পাঠোদ্ধার বিনা মানব-সভ্যতার এক প্রোজ্জল অধ্যায় অজ্ঞাত থেকে যেত, সেই লেখমালা থেকে আঁমরা বহু তথ্যের সন্ধান পেয়েছি এমন একজন ব্যক্তি (ও তাঁর যুগের ) সম্বন্ধে যিনি শুধু রাজকুলে নয়, সর্বদেশ ও সর্বকালের মহা পুরুষদের মধ্যে এক সমুন্নত স্থান নিয়ে আছেন।
আরো পড়ুন :- অশোকের ধর্মের বৈশিষ্ট্য
সিংহাসন আরোহণ করে অশোক প্রথমে গতান্ুগতিকভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। অভিষেকের পর থেকে অষ্টম বর্ষে তিনি কলিঙ্গ বিজয়ে উদ্যোগী হন। এই যুদ্ধকালীন যে ভয়াবহ ব্যাপার তার
দৃষ্টিগোচর হয় তাতে তার মর্ম মথিত হয়ে ওঠে, নিদারুণ যন্ত্ৰণা ও অভ্র লোকক্ষয় তীর হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে। পরম অন্ুশোচনায় তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখনও এ ভাবে যুদ্ধ জয়ের চেষ্টায় অসহনীয় বেদনা ও প্রাণনাশ ঘটাবেন না। কলিঙ্গ যুদ্ধের স্মারকরূপে ভ্রয়োদশশিলালিপিতে অশোকের এই হ্ৃদয়-পরিবর্তনের উল্লেখ আছে। তখন থেকে অহিংসাকে পরমধর্ম বলে মেনে তিনি যুদ্ধজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের নীতি ঘোষণা করেছিলেন | এমন ঘটনা শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ইতিহাসে একেবারে অনন্য |
ধর্ম প্রচার ও প্রচারিত 'ধম্ম'
কহলনের রাজতরদ্বিণীতে অশোক শিবের ভক্ত ছিলেন বলা হয়েছে; রাজতরদ্দিণী বহু পরে রচিত, এঁতিহাসিক যাথার্থ্যের দিক থেকেও সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু অশোকের দেবদ্বিজে ভক্তি থাকা অবিশ্বাস্ত নয়; বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পরও ব্রাহ্মণ, এমন কি আজীবিক প্রভৃতির প্রতি তার বদান্যতা, কমে নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল | যাই হোক, কথিত আছে A alae বিজয়ের পর সন্ন্যাসী উপগুপ্ত তাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। কারও কারও মতে তিনি বৌদ্ধ সজ্ঘে যোগ দিয়ে স্বয়ং ভিক্ষু হয়েছিলেন | অবশ্য রাজাদন তিনি পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু পূর্বাভ্যস্ত “বিহার-যান্ত৷” অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে বিলাসিতার পূৰ্ণ উপকরণ নিয়ে পরিভ্রমণ, পরিহার করে "ধর্মযাত্রা” অর্থাৎ তীর্থ-পরিক্রম! এবং বুদ্ধের শিক্ষা সৰ্বত্ৰ প্রচারের কাজে নেমেছিলেন। জনসাধারণের সর্বস্তরে ধর্মের বাণী বিতরণ করে যে আনন্দ তিনি পেতেন, তার বিবরণও পাওয়া গেছে । শাক্যমুনির জন্মস্থান লুম্বিনী উদ্যান প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে তিনি গেলেন, আর সৰ্বত্ৰ ধর্মের ও সদাচারের ব্যাখ্যা করলেন। সন্মাৰ্গ যে সকলের পক্ষেই উন্মত্ত সেজন্য যে সমাজে উচ্চ স্থান কিংবা বিশিষ্ট শিক্ষাদীক্ষার কোনও প্রয়োজন ছিল না, একথা তিনি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন সাত্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, : পর্বতগাত্রে ও প্রস্তর স্তম্ভে “ধম্ম লিপি” খোদিত করে দিলেন, সহজ প্রাকৃত _ ভাষায় তা সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়ে রইল। “রাজুক”, “প্রাদেশিক” “যুক্ত” প্রভৃতি নামধেয় যে কর্মচারীর দল বহু বিস্তৃত সাআাজ্যের সৰ্বত্ৰ নিযুক্ত ছিল, তাদেরও ধর্ম প্রচারের কাজে অশোক আহ্বান করলেন ॥ _ শুধু তাই নয়, “ধর্মমহামাত্র” নামে একদল নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করে
তাদের ধর্মের মূল নীতিগুলি প্রচারের আদেশ দিলেন । সকল রাজপুরুষকে নির্দেশ দেওয়া হল যাতে আলস্ত ও অবহেলা পরিহার করে সর্বদা প্রজা সাধারণের কল্যাণ চেষ্টায় তারা নিযুক্ত থাকে । বার বার অশোকের শিলালিপিতে “ ধর্ম ” শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । স্বত্তপিটকের অংশীভূত বিখ্যাত নীতিসঞ্চয়ন " ধম্মপদ ” থেকে বহু বাণীর উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছিলেন । কিন্তু শুধু মাত্র বৌদ্ধধর্ম নয় , প্রাচীন ভারতের ধর্মশিক্ষা থেকেও আহরণ করে অশোক সেই নীতি ও উপদেশ প্রচার করেন । তাই ধর্মাচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে মাতাপিতা ও স্থবির বৃদ্ধের শুশ্রূষা , হিংসা ও প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকা , আত্মীয় - বন্ধু ও ব্রাহ্মণ - শ্রমণদের প্রতি সম্যক্ ব্যবহার , দাস - ভৃত্য প্রভৃতির প্রতি সমুচিত আচরণ , অপর সম্প্রদায়ের নিন্দা বা বিরূপ সমালোচনা বর্জন প্রভৃতি কাজেই ধর্মের প্রকাশ ঘটে । দয়া , দান , দাক্ষিণ্য , সত্য , শুচি ও নম্রতার নীতিকে শিরোধার্য করে ক্রোধ , চণ্ডতা , নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পরিহার করে চলতে পারলেই প্রকৃত ধর্মাচরণ করা হবে । সকলের সঙ্গে মিলে থেকে ( “ সমবায় ” ) , চিত্তচাঞ্চল্যকে প্রশমিত করে ( “ সংযম ” ) , মনকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে ( “ ভাবশুদ্ধি ” ) যথার্থই ধর্মজীবন পালন করা হবে । ধর্মের সারবস্তু সংগ্রহ করে , মানুষের পরস্পর - সংশ্লিষ্ট জীবনে “ শীল ” -এর উপর জোর দিয়ে , স্হজ ভাষায় ও ভাবে অশোকের শিক্ষা প্রচারিত হয়েছিল । এখানে কোথাও সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নেই — সুনীতি , সদাচার , সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি সর্বগ্রাহ্য বিষয়ই অশোকের “ ধর্ম ” -এ রয়েছে । সর্বজন যাতে সুখী হয় , সর্বজনের হিতার্থে যাতে মানুষ নিজের শক্তি নিয়োজিত করে , সততার পরিবেশ যাতে সমাজ - জীবনকে স্নিগ্ধ ও শান্ত করে রাখে , এই ছিল অশোকের একান্ত কামনা ।রাজ ৷ অশোক
রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে অশোকের যে ধারণা ছিল , তারও মহিমা কম নয় । পূর্বে বলা হয়েছে যে আলস্থ্য ও অবহেলা ত্যাগ করে জনকল্যাণে লিপ্ত থাকার নির্দেশ সমস্ত রাজপুরুষকে দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু নিজেকেও কর্তব্য পালনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ রাখতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি হয় নি । প্রজারা যে কোনও সময় তাঁর কাছে অভাব - অভিযোগের কথা জানাতে পারত ; রাজা অন্তঃপুরে বা যেখানেই থাকুন না কেন , প্রজাদের ফিরিয়ে দেওয়া হত না । “ রাজুক " ( বা রজ্জুক ) নামধেয় যে কর্মচারীরা সম্ভবত বিভিন্ন জেলায় বিচার এবং ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত ছিল , তাদের সম্বন্ধে অশোকের এক স্তম্ভলিপিতে খোদিত আছে : “ সন্তানকে যেমন সুনিপুণ ধাত্রীর হাতে দিয়ে লোকে আশ্বস্ত হয় , ঠিক সেইরকম ‘ রজ্জুক ’ - দের নিযুক্ত করেছি , যাতে দেশবাসীর মঙ্গল ও সুখের জন্য একাগ্র চিত্তে ( ‘ অবিমনা ' ) তাঁরা কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন । ” ধৌলির বিখ্যাত শিলালিপিতে আছে অশোকের অবিস্মরণীয় ঘোষণা : “ সকল মানুষ আমার সন্তান ( ‘ সবে মুনিসে পজা মমা ' ) । নিজের সন্তান সম্বন্ধে আমি যেমন চাই যে তাদের হিত ও সুখ হোক , সকল মানুষ সম্বন্ধেও আমার তাই ইচ্ছা । ” কেবল শাসন নয় , রাজ্যের কল্যাণ , প্রজাদের হিতবিধান ও দুঃখ নিবারণ , সকলকে ধর্মের মর্মবস্তু শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের নিয়ত আয়োজন — এই ছিল অশোকের আদর্শ । দেশশাসনকল্পে দেশবাসীর মধ্যে প্রচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অশোকের পূর্বে কোনও শাসকের মনে এমনভাবে কখনও অনুভূত হয় নি ।
ধর্মবিজয়
দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের বাণী ঘোষণা করে অশোক চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন , ' ভেরীঘোষ ' - এর স্থানে ' ধৰ্ম্মঘোষ ’ , রণদামামার পরিবর্তে শান্তি ও শীল ছিল তাঁর কাম্য । দুর্দান্ত প্রতিবেশী ও অবাধ্য অরণ্যবাসী উপজাতিসমূহকে অস্ত্রবলে দমন করার কার্যক্রম পরিত্যক্ত হল ; অশোক বললেন যে “ ধৰ্ম্মবিজয় ” -এর পথে গিয়ে তিনি সুদুর দক্ষিণ ভারতে তামিল রাজ্য , সিংহল এবং পশ্চিম এশিয়ায় ও দক্ষিণ ইয়োরোপের গ্রীকদের স্বপক্ষে আনতে পেরেছিলেন । দক্ষিণ ভারতে চোল , পাণ্ড্য , সত্যপুত্র ও কেরল , এই চার রাজ্যের সঙ্গে তাঁর মৈত্রীবন্ধন অটুট হয়েছিল । বিদেশে ধর্ম প্রচারে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল । ব্রহ্মদেশে তিনি প্রেরণ করেন শোণ ও উত্তর নামে দুই প্রচারক ; তাম্রপর্ণী অথবা সিংহল দেশে নিজ ভ্রাতা ( কিংবা মতান্তরে পুত্র ) মহেন্দ্রকে এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠানোর কথা সর্বজনবিদিত । সিংহলের রাজ ৷ ‘ দেবানাম্ পিয় তিস্স্স ' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় সিংহল ভারত সভ্যতারই প্রায় অঙ্গীভূত হয়ে গেল । সম্ভবত দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়াতে সুমাত্রা অঞ্চলেও অশোক ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন । শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য - বিনিময় নয় , সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিজয়ের পুণ্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি বহুদূর অবস্থিত দেশে রাজদূতের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন । তাঁর দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ - সংখ্যক শিলালিপিতে নাম আছে সিরিয়ার ‘ অন্তিয়োক ( ‘ এন্টিওকস্ থিয়স্ ' ) , মিশরের ‘ তুরমায় ’ ( দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেল্ফস্ ) , ম্যাসিডনের ‘ অন্তেকিন ’ ( এন্টিগোনস্ ) , উত্তর আফ্রিকাস্থিত কাইরিনি - র ‘ মগা ’ ( ‘ যেগস্ ’ ) এবং খাস গ্রীস দেশের অন্তর্গত এপাইরস্ - এর ( কিংবা অন্যমতে কোরিস্থ ) ‘ অলিকসুদর ' ( আলেকজাণ্ডার ) , এই পাঁচজন গ্রীক রাজার । এদের সকলের কাছে অশোক দূত প্রেরণ করেছিলেন । কতটা বৌদ্ধধর্ম বা এ দেশের নীতির প্রচার সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটেছিল জানা নেই , কিন্তু অশোকের লক্ষ্য ছিল একান্ত স্পষ্ট । অবশ্য তখন বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই যোগাযোগ অনিবার্য হয়ে উঠছিল , কিন্তু ধর্ম , সংস্কৃতি ও সদাচারের দৃষ্টিকোণ থেকে অশোকের এই উদ্যোগিতার মূল্য তাতে হ্রাস পায় না ।
অশোকের যে শিলালিপি ভারতময় ছড়িয়ে রয়েছে , তাতে যেন একটা গোটা সাহিত্যের সন্ধান মেলে— তাতে ছিল অনুশাসন , ধর্মশিক্ষা , রাজপুরুষদের প্রতি নির্দেশ , রাজার স্বকীয় চিন্তা ও আদর্শের প্রচার । এই শিলালিপি থেকে আবার অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং দূরাবস্থিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় । বিদেশী বিদ্বান প্রিন্সেপ খ্রীষ্টাব্দের উনিশ শতকে অশোক - শিলালেখের অর্থোদঘাটন করে বিশ্বের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন । মৌর্য শাসন সম্বন্ধে আলোচনা পরে হবে ; এখানে বলে রাখা দরকার যে অশোকের কালে মগধ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল সম্ভবত পাটলিপুত্র থেকেই শাসিত হত , কিন্তু দূর প্রদেশে রাজার প্রতিনিধির উপর শাসনভার অর্পিত হত । এই প্রদেশগুলি ছিল উত্তরাপথ ( তক্ষশিলা এর রাজধানী ) । অবন্তী ( রাজধানী উজ্জয়িনী ) , কলিঙ্গ ( রাজধানী তোসলি ) , মধ্যদেশ ( রাজধানী সুবর্ণগিরি ) , ইত্যাদি । রাজ্যসীমান্তে সম্ভবত অশোককে সম্রাট বলে মানত এমন রাজাদেরও দেখা যেত ।
অনন্যচরিত্র অশোক
কথিত আছে যে গার্হস্থ্য গণ্ডগোলের ফলে বৃদ্ধ বয়সে অশোককে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছিল । তিষ্যরক্ষিতা নাম্নী মহিষীর মিথ্যা প্ররোচনায় তিনি নাকি পুত্র কুণালের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিলেন ; পরে বুঝি প্রকৃত সংবাদ জানতে পেরে আবার কুণালের উপর প্রসন্ন হন । তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য ক্রমশ যেন তার মহত্ত্ব হারাতে থাকে , একশো বৎসর বাদে তার অবসান ঘটে । অশোকের কীর্তি স্থায়ী হতে পারে নি । আদর্শের বাস্তবে রূপায়ণ সামাজিক পরিস্থিতি ও বিকাশ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল , কেবল ইচ্ছা শক্তির জোরে তা সম্ভব হয় না । কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় কবির ভাষায়— “ তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান্ ” । অশোকের যুগ থেকে নিরবধি কাল অনেক এগিয়ে এসেছে , দেশদেশান্তরে কত পরিবর্তন ঘটেছে , কিন্তু তাঁর পুণ্যস্মৃতি আজও পৃথিবী ভোলে নি , ভবিষ্যতেও ভুলবে না ।
অশোকের মতো রাজা জগতের ইতিহাসে যে একান্ত দুর্লভ , তা বলার অপেক্ষা রাখে না । কলিঙ্গ জয়ের মুহূর্তে , সাফল্য - মদিরার উন্মাদনাকে উপেক্ষা করে , বিবেকের দংশন অনুভব করার মতো সংবেদনশীলতা যে রাজার , তিনি সহজ ব্যক্তি নন । বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও ক্ষমতার লোভ বর্জন করে , রাজ্যলিপ্সা পরিহার করে , ধর্ম ঘোষণাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করা মহৎ ব্যক্তি ভিন্ন কারও পক্ষে সম্ভব নয় । দেশে বিদেশে সর্বপ্রাণীর হিত কামনা এই রাজতপস্বীর মনকে যেভাবে উদ্বেল করেছিল , তার তুলনা ইতিহাসে কোথাও নেই । দেশে এবং বিদেশে শান্তি ও শীলের বাণী বিকীরণে তিনি অক্লান্তকর্মী । আত্মপ্রসাদের লক্ষণ তাঁর কাজের মধ্যে কখনও দেখা যায় নি । বৃক্ষরোপণ , কৃপথনন , ওষধির বিস্তার , মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসা ও শুশ্রুষাগার স্থাপন , দীর্ঘবিস্তারী রাজপথপার্শ্বে অতিথিশালা , বিশ্রামগৃহ ইত্যাদির ব্যবস্থা , এমন একটি মনের পরিচয় দেয় যা প্রকৃত গৌরবের অধিকারী । ইতিহাসে তিনি যে অমর হয়ে থাকবেন , তাতে বিস্ময়ের বিন্দুমাত্র কারণ নেই ।
শিলালেখ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে অশোকের চরিত্রের কিছু পরিচয় মেলে । প্রথম জীবনে উচ্চাভিলাষ হয়তো তাকে ক্ষমতালিপ্সার পথে ঠেলে দিয়েছিল ; ভ্রাতৃহত্যার যে বিবরণ রয়েছে তা সত্য হলেও একেবারে অর্থহীন না - ও হতে পারে । শেষ জীবনে কুণাল সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারের যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায় , তাও নির্ভুল না হওয়ার সম্ভাবনা , কিন্তু হয়তো বলা যায় যে চতুর্থ শিলানুশাসনে পুত্র - পৌত্রাদিকে ধর্মে ও শীলে ‘ স্থিত ’ হয়ে থাকার যে উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন , তা থেকে নিজেই কখনও কখনও স্খলিত হয়ে পড়তেন । অহংবোধের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠতে তিনি পারেন নি । সম্ভবত তাঁর চরিত্রে কিছু আতিশয্য দোষ ছিল , যা প্রকাশ পেয়েছিল প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ করে দেওয়ার মধ্যে । কিন্তু একেবারে দোষমুক্ত চরিত্র দেবতার ক্ষেত্রে কল্পনীয় , মানুষের বেলায় নয় । আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনা অশোকের যে কি পরিমাণে ছিল , তাঁর কৃতকর্ম হল তার সাক্ষ্য । ধর্ম , সদাচার সম্বন্ধে পরম আগ্রহশীল এই নরপতির বাস্তব বোধও লক্ষ্য করার বস্তু । যুদ্ধকে নীতি হিসাবে পরিহার তিনি করেছিলেন , কিন্তু সমাজ রক্ষার জন্য দুষ্টের দমন যে প্রয়োজন তা স্বীকার করতেন , অপরাধীকে ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যে নীতিবিগর্হিত নয় তা মনে করতেন বলে প্রমাণ আছে । অশোককে একেবারে সর্ব ব্যাপারে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ মনে করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু তাঁর বহুগুণান্বিত চরিত্র ও ভাস্বর প্রতিভা অতি কঠোর বিচারেও জগৎকে মুগ্ধ করবে । তাই দেখা যায় যে , রোমান সম্রাট কন্স্টান্টাইন , ইয়োরোপে মধ্যযুগীয় সম্রাট চার্লস্ ( Charlemagne ) , মহামতি আকবর প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রাজাদের সঙ্গে কেউ কেউ মহামতি অশোকের তুলনা করেছেন । তুলনায় অবশ্য অশোকই যে সর্বশ্রেষ্ঠ , তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে নি । মনের যে ঔদার্য ও প্রসার , সর্বজীবে যে মমতা , এবং কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধের চরণারবিন্দ অনুসরণ করে করুণার যে সিঞ্চন অশোকের কৃতকর্মে দেখা যায় , তার তুল্য কোনও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই । এজন্যই ইংরাজ মনীষী এইচ . জি . ওয়েল্স পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলেছেন যে নানা দেশের অসংখ্য রাজার মধ্যে অশোক যেন সমুজ্জ্বল তারকার মতো একা উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছেন , তাঁর সমকক্ষ কোথাও কেউ নেই । ওয়েল্স শুধু একথা বলে ক্ষান্ত হননি ; ইতিহাসে ছয়জন শ্রেষ্ঠ মানবের নাম স্থির করতে গিয়ে বলেছেন যে গৌতমবুদ্ধ , যীশুখ্রীষ্ট , অ্যারিস্টটল , অশোক , রজার বেকন এবং এব্রাহাম লিঙ্কন - কে তিনি বাছাই করবেন ।
মগধ সাম্রাজ্যের পতন
অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্রাজ্য একশো বৎসর টিকে ছিল । বিশাল - বিস্তার মৌর্য সাম্রাজ্য ছিল উত্তর - পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত , অপর দিকে আরবসাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত । হয়তো বিপুল - আয়তন এই মৌর্য সাম্রাজ্য খুব বেশীদিন একচ্ছত্র আধিপত্যে রাখতে হলে পুরুষানুক্রমে রাজা এবং তার পরামর্শদাতা ও কর্মচারীদের মধ্যে এত বেশী নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন যে তা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত । তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সমসাময়িক জগতের মাপকাঠিতে যথেষ্ট ভালো হলেও আধুনিক কালের তুলনায় ছিল অকিঞ্চিৎকর । জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে রাষ্ট্রে তা রূপায়িত হতে তখন অনেক বিলম্ব ছিল । স্বয়ং অশোকেরই রাজ্যকাল শেষ হয়ে আসার সময় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল । বিন্দুসার এবং অশোক উভয় সম্রাটই দূরে অবস্থিত প্রদেশগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে বেগ পেয়েছিলেন । জলৌক , কুণাল , বন্ধুপালিত , সম্প্রতি ( বা সম্পদি ) , দশরথ ইত্যাদি অশোকের উত্তরাধিকারীর নাম জানা রয়েছে , কিন্তু খুঁটিনাটি খবর যা আছে তা খুব নির্ভরযোগ্য নয় । কোন কোন মতে অশোকের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য তাঁর ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল । যাই হোক , আনুমানিক ১৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে পুষ্যমিত্র নামে তাঁর এক ব্রাহ্মণ সেনাপতি হত্যা করে সুদ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন ।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে সনাতন হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করায় অশোক প্রাচীনপন্থীদের শত্রুতা উদ্রেক করেছিলেন , আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের মুখপাত্র হয়ে এসে পুষ্যমিত্র সুজ মৌর্য সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন । এক সময় খুব প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এই মত গ্রাহ্য নয় । অশোকের বিভিন্ন শিলালিপির পাঠোদ্ধার থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে অশোক ধর্ম ব্যাপারে একেবারে অসহিষ্ণু ছিলেন না , শ্রমণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদেরও ( এমন কি আজীবিকদেরও ) মর্যাদা দানে কুণ্ঠিত থাকেন নি । যে স্থনীতি প্রচারে তিনি শতমুখ হয়েছিলেন , তা শুধু বৌদ্ধ শিক্ষা নয় , ভারতবর্ষের সকল ধর্মচিন্তাধারার নির্যাস তাকে বলা চলে । হয়তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা প্রখর বৌদ্ধবিদ্বেষী , তারা অশোকের বহু কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট ছিল , কিন্তু তাদের সংখ্যা ও শক্তি এত বেশী হওয়া সম্ভব নয় যার ফলে সাম্রাজ্যের পতন সাধনে তারা সমর্থ হতে পারে । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের এক গৌণ কারণ হতে পারে বৌদ্ধবিরোধীদের অসন্তোষ , কিন্তু সেটা কিছুতেই মুখ্য ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে না ।
পূর্বে বলা হয়েছে যে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিশাল আয়তনে শাসনব্যবস্থাকে অটুট রাখা সম্ভব ছিল না ; এই বিশালত্ব সাম্রাজ্যের পতনের একটি হেতু বলে অবশ্য আমরা মনে করতে পারি । দূরে অবস্থিত প্রদেশে সম্রাটের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যে কত কঠিন ছিল তা আগে বলা হয়েছে । কহলণের “ রাজতরঙ্গিণী ” থেকে মনে হয় যে কাশ্মীর সাম্রাজ্য থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছিল ; মহাকবি কালিদাস - কৃত “ মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ” নাটকে দেখা যায় যে বিদর্ভ প্রদেশ ও সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করছে । খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ পাদে গ্রীক - বিবরণ থেকে জানা যায় যে তক্ষশিলাকে কেন্দ্র করে স্থভাগসেন নামে একজন “ ভারতবর্ষীয়দের রাজা " আখ্যা নিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে লেখা গার্গী সংহিতাতে এমন কথাও আছে যে এক গ্রীক সৈন্যবাহিনী পাটলিপুত্র পর্যন্ত এসেছিল । এই সব সংবাদের সত্যতা যাই হোক , অশোকের উত্তরাধিকারীদের আমলে সাম্রাজ্য যে পূর্বগৌরব রক্ষা করে চলতে পারে নি , তা নিশ্চিত । বিন্দুসার ও অশোকের রাজ্যকালেই তক্ষশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল , অশোককে তাই নিয়মিতভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে “ মহামাত্র ” প্রেরণ করে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল । তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব যখন রাজসিংহাসন থেকে অপসৃত হল , তখন অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে নেমে যাওয়া খুবই সম্ভব । মৌর্য রাজবংশে সংহতি তখন ছিল না ; সম্রাট বংশীয়েরাই পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল , শাসন ব্যাপারে অবহেলা করে চলছিল এবং কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিল । এর ফল হল অবশ্যম্ভাবী ; মৌর্য সাম্রাজ্যের গৌরবরবি একেবারে অস্তমিত হল পুষ্যমিত্র সুঙ্গের আঘাতে ।
আরও এক কারণ ছিল এই যে সম্ভবত ধর্মপ্রচারে অতিরিক্ত মনোনিবেশের ফলে অশোকের পক্ষে সাম্রাজ্যরক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না । তাঁর জীবদ্দশায় অবশ্য সীমান্তবর্তী কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি , ধর্মবিজয়ের নীতির মধ্যে যে রাষ্ট্রিক দুর্বলতার সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তা বুঝা যায় নি । কিন্তু অহিংসার প্রচারক হওয়ার পর সামরিক শক্তি অটুট রাখার দিকে স্বভাবতই অশোকের আগ্রহ হ্রাস পেয়েছিল । প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর যুদ্ধ - ভেরী শোনা যায় নি , শোনা গিয়েছিল ‘ ধর্মঘোষ ' ; খাপে - পোরা তলোয়ারে যেন জং ধরে গেল । রাজা যে শীকারে বেরুতেন তাও বন্ধ করে দেওয়া হল ! বাণভট্টের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে তাঁর সৈন্যের উপস্থিতিতেই পুষ্যমিত্র অবলীলাক্রমে হত্যা করেছিলেন । যোদ্ধাদের মনোবল যে বহুদিন হতেই ভেঙে যাচ্ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের যে বহুবিধ কারণ ছিল তা আমর! মনে রাখব, আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করব যে মগধকে কেন্দ্র করে চন্দ্ৰগুপ্ত স্থবিপুল সাম্ৰাজ্য স্থাপন করার পূর্বে যেমন এদেশে বিদেশী আক্রমণকারীরা ঢুকে পড়ার লৌভে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছিল, তেমনই মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর বিদেশীরা আবার এখানে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসে নামছে।




.png)