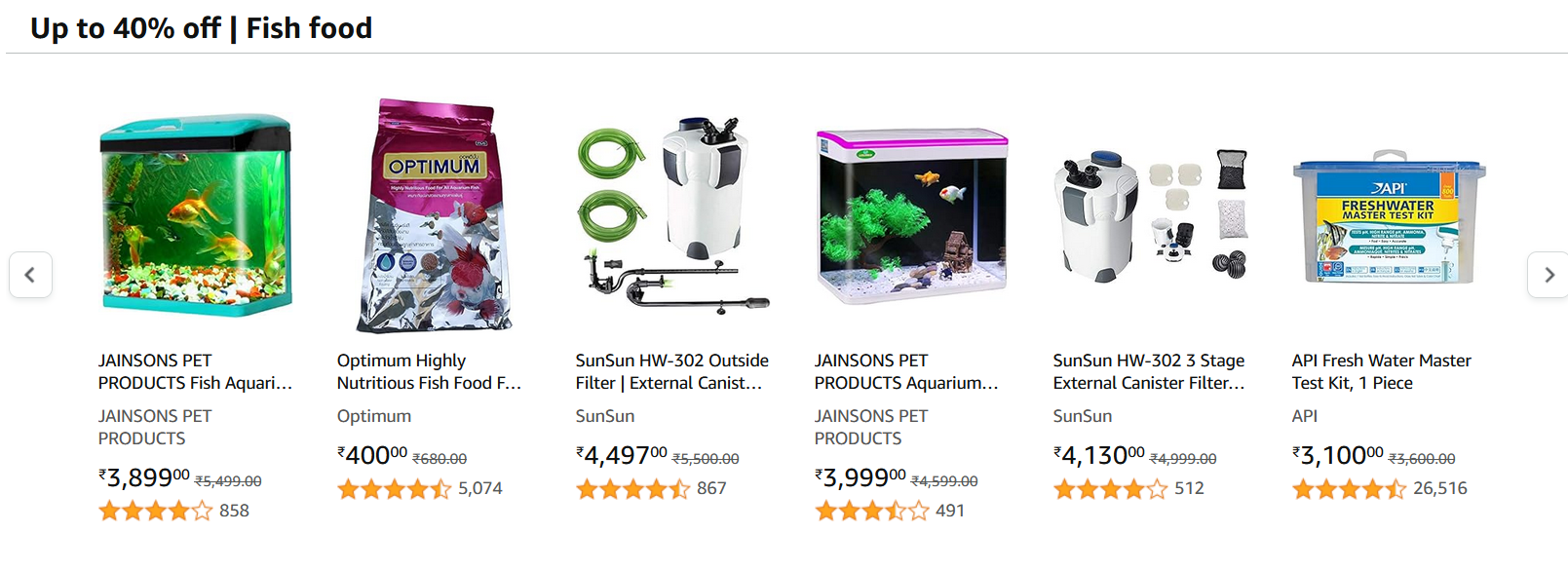■ হর্ষবর্ধন (৬০৬-৪৭ খ্রিঃ)
গৌড়রাজ শশাঙ্কের হস্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর মাত্র ষোল বছর বয়সে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সিংহাসনে বসেন (৬০৬ খ্রিঃ)। গ্রহবর্মার মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসন তখন শূন্য থাকায় কনৌজের শাসনভারও তিনি গ্রহণ করেন। এই যুগ্মরাজ্যের রাজধানী নির্বাচিত হয় কনৌজ। এ সময় থেকে কনৌজ উত্তর ভারতের সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। নিজের সিংহাসনারোহণ কালকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ সময় অর্থাৎ ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি একটি নতুন বর্ষ গণনা বা অব্দের প্রচলন করেন তার নাম 'হর্ষাব্দ' বা 'হর্ষ-সম্বৎ'। তাঁর উপাধি ছিল “শিলাদিত্য'।
হিউয়েন সাঙ বলেন যে, সিংহাসনারোহণের পর ছয় বছরের মধ্যে তিনি সমগ্র আর্যাবর্তে তাঁর সর্বময় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, এই মত ইতিহাস-সম্মত নয়। তিনি সর্বপ্রথম তাঁর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়রাজ শশাঙ্ক-র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ কারো রচনাতেই এই যুদ্ধের কোন বিবরণ নেই। শশাঙ্কের আক্রমণাত্মক মনোভাবে ভীত কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন, কিন্তু শশাঙ্কের জীবিতাবস্থায় তাঁদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রিঃ) তিনি মগধ, উড়িষ্যা, কঙ্গোদ ও পশ্চিমবঙ্গ জয় করেন। শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মনের রাজাভুক হয়। পশ্চিম ভারতে বলভী রাজ্যের (গুজরাট) মৈত্রকবংশীয় রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেন-এর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের পর ধ্রুবসেনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনি মিত্রতার স্থাপন করেন। দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্দেশ্যে হর্ষ এক অভিযান পাঠান, কিন্তু বাতাপির চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী-র কাছে পরাজিত হয়ে তিনি ফিরে আসেন। তিনি সিন্ধুদেশ ও কাশ্মীর-এর বিরুদ্ধেও অভিযান পাঠান, কিন্তু তা সফল হয়নি।

বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর একটি শিলালিপিতে হর্ষকে সকলোত্তর পথনাথ' বা সকল উত্তরাপথের অধীশ্বর বলা হয়েছে। কে. এম. পাণিক্কর তাঁকে নেপাল ও কাশ্মীরসহ বিন্ধোর উত্তরে সকল ভূখণ্ডের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-এর মতে, সম্ভাব্য সকল দিক বিচার করে বলা যায় যে, হর্ষ সমগ্র উত্তর ভারতের সার্বভৌম সম্রাট ছিলেন। বল বাহুল্য, এ মত ঠিক নয়। তিনি থানেশ্বর ও কনৌজ অর্থাৎ পূর্ব পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি জয় করেছিলেন মগধ বা বিহার, উৎকল, কঙ্গোদ এবং পশ্চিমবঙ্গ। বাণভট্টর মতে হয় পঞ্চ ভারত' এর অধীশ্বর ছিলেন। 'পঞ্চ ভারত বলতে–পাঞ্জাব, কনৌজ, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা বোঝায়। সুতরাং হর্ষের প্রাপ্ত ও বিজিত রাজ্যের সঙ্গে এই বর্ণনা মোটামুটি মিলে যায়। পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, নেপাল, কাশ্মীর, কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ তাঁর অধিকারের বাইরে ছিল। সুতরাং তাঁকে ‘সকলোত্তরপথনাথ' বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজ্য অনেক ক্ষুদ্র ছিল।
হর্ষবর্ধনের স্ম্রাজ্য
- কাশ্মীর
- গান্ধার
- পুরুষপুর
- তক্ষশিলা
- হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
- শতজ্ঞ
- মুলতান
- থানেশ্বর ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ
- মথুরা
- মালব
- প্রয়াগ
- সৌরা
- তাম্রলিপ্তি)
- মহানদী নং
- -কঙ্গোদ
- কলিঙ্গ
- -বঙ্গোপ সাগর
- কামরূপ এ
- নর্মদা নং
- রাষ্ট্রকূট | চালুক্য
- তা ন • অজন্তা
- কৃষ্ণা নং
- বাতাপি
- আ র ব কণাট
- গোদাব
- দাবরী ন
- চোল
- মাদুরা
- পাণ্ড্য
- সিংহল.
"This limit of Harsha's empire is much narrower than what is generally believed." Dr. R. C. Majumdar. The Classical Age
হর্ষবর্ধন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক সমরকুশলী ও প্রজাহিতৈষী নরপতি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারত বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লে কৃতিত্ব : রাষ্ট্রীয় ঐক্য হর্ষবর্ধন এ সময় অন্তত কিছু কালের জন্য উত্তর ভারতের কিছু অংশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেন ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তাঁরই ১০প্তায় কনৌজ ‘মহোদয়শ্রী’ অভিধায় ভূষিত হয় ও পাটলিপুত্রের গৌরব হরণ করে।
কেবলমাত্র রণকুশলী সমরনায়ক বা দক্ষ প্রশাসকই নন–তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তিনি স্বয়ং একজন বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁর রচিত ‘নাগানন্দ’, ‘রত্নাবলী’ ও ‘প্রিয়দর্শিকা’ নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। শিক্ষা ও সাহিত্য হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সাহিত্যসেবীদের জন্য রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ ব্যয় করতেন। বহু বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত ' রচয়িতা বাণভট্ট তাঁর সভাকবি ছিলেন। এছাড়া জয়সেন, ময়ূর, দিবাকর, কবি মৌর্য ও কবি ভর্তৃহরি তাঁর সভা অলংকৃত করতেন। এই যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ-বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল এবং হর্ষবর্ধন এখানে মুক্তহস্তে দান করতেন।
হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ধর্মবিশ্বাসে হর্ষ বৌদ্ধ ধর্মমত ছিলেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও তিনি বৌদ্ধ ছিলেন না—আজীবন তিনি ছিলেন শিব ও সূর্যের উপাসক এবং সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল।
তিনি একজন প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রজা-কল্যাণের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন। তাঁর দানশীলতা হিউয়েন সাঙকে বিস্মিত করেছিল। প্রজাদের সুবিধার জন্য অশোকের মতই তিনি সরাইখানা, , বিশ্রামাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক রোলিনসন (Rawlinson)-এর মতে—অশোক ও আকবরকে বাদ দিলে হর্ষবর্ধন ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী নরপতি। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-এর মতে হর্ষের মধ্যে অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের গুণাবলীর এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।
→ হিউয়েন সাঙের বিবরণ ঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে আসেন। দীর্ঘ চোদ্দ বছর (৬৩০–৪৪ খ্রিঃ) ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর ভারত ভ্রমণকথা ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। চিনা ভাষায় লিখিত এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটির নাম হল 'সি-ইউ-কি'। তাঁর বিবরণ থেকে সমকালীন যুগের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, জনসাধারণের অবস্থা এবং হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয় ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।
হিউয়েন সাঙ ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয়রা সৎ, নম্র, অতিথিপরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ ছিল। তারা সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত। জনসাধারণের মধ্যে বেশভূষার বাহুল্য ছিল না—একমাত্র ধনীদের মধ্যেই বেশভূষা ও অলংকার বহুল প্রচলিত ছিল। এই যুগে নারীর মর্যাদা ও অধিকার যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। নারীদের শাস্ত্রপাঠ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সেযুগে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে পর্দাপ্রথা ছিল না। হিন্দুসমাজে তখন বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শহর বা গ্রামের বাইরে বাস করত। সমাজে অস্পৃশ্যতার প্রভাব ছিল ব্যাপক। তিনি হর্যের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রাজা স্বয়ং রাজ্য পরিভ্রমণ করে শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। গুপ্তসম্রাটদের মত তাঁরও একটি মন্ত্রীপরিষদ ছিল। তাঁর সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল বিরাট। হিউয়েন সাঙের মতে হর্ষের পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে
৫০ হাজার, ১ লক্ষ ও ৬০ হাজার। করভার লঘু ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হত। বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটানো হত না। বণিকরা যাতে রাজকর্মচারীদের দ্বারা অত্যাচারিত না হয়, তার দিকে রাজার প্রখর দৃষ্টি ছিল। দেশে প্রচুর দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম ও অতিথিশালা ছিল। দেশে দস্যু-তস্করের বেশ কিছু উপদ্রব ছিল। হিউয়েন সাঙ স্বয়ং একাধিকবার দস্যুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। দণ্ডবিধি ছিল কঠোর এবং অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল।
হিউয়েন সাঙের মতে কনৌজ ছিল আর্যাবর্তের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগর—তৎকালীন উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র। শহরটির আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং তা চতুর্দিকে সুউচ্চ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বহু বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু নগরের মধ্যে তিনি প্রয়াগ, মথুরা, থানেশ্বর, বারাণসী ও তাম্রলিপ্ত-র কথা উল্লেখ করেছেন। মন্দির দিয়ে তিনি কনৌজকে সুসজ্জিত করেন। অন্যান্য জনবহুল হর্ষবর্ধন বিদ্যা ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নালন্দা ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নালন্দার ছাত্র ও শিক্ষকদের জ্ঞান-গরিমা, উন্নত চরিত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি আচার্য শীলভদ্র-র অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর মতে নালন্দা ছিল এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা সেখানে সমবেত হতেন। হিউয়েন সাঙ নিজেও সেখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে হর্ষবর্ধন প্রচুর অর্থব্যয় করেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও এখানে দর্শন, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী এবং হিমালয়সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সারা দেশই ছিল উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ। ভারতীয়রা বস্ত্র,
অলংকার শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিল এবং চিন, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তাম্রলিপ্ত ছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর। তাঁর রচনায় কনৌজের ধর্মসভা ও প্রয়াগের মেলার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মহাযান ধর্মমতের আলোচনা ও হিউয়েন সাঙের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ৬৪২ কনৌজের ধর্মসভা খ্রিস্টাব্দে হর্ষ কনৌজে এক ধর্মসম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ২০ জন মিত্ররাজা, ৪ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ৩ হাজার জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তিসহ পাঁচশ' হাতির বিরাট একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের হত। স্বয়ং হর্ষবর্ধন বুদ্ধমূর্তির পেছনে বসে চামর দোলাতেন। এই ধর্মসভার অধিবেশন আঠারো দিন স্থায়ী হয়। এই সম্মেলনে বৌদ্ধদর্শন নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে এক মেলা বসত। তিন মাস কাল স্থায়ী এই মেলায় হর্ষ বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের উপাসনা করতেন এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রয়াগের মেলা সকলকে অকাতরে প্রার্থিত বস্তু দান করতেন। এই স্থানটির নাম রাখা হয়েছিল 'দানক্ষেত্র' বা 'সন্তোষক্ষেত্র'। হিউয়েন সাঙ লিখছেন যে, এইভাবে তিনমাসের মধ্যে একমাত্র অশ্ব, হস্তী ও সামরিক উপকরণ ছাড়া রাজ্যের রাজকোষ ও রাজার পাঁচ বছরের সঞ্চিত সব অর্থাদি নিঃশেষ হয়ে যেত। কথিত আছে যে, এইভাবে পোষাক, অলংকার ও সর্বস্ব দানের পর তিনি ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে সাধারণ একটি কাপড় চেয়ে নিয়ে গৃহে ফিরতেন।
> "Harsha was a remarkable man and stands besides Asoka and Akbar among greatest rulers that India has produced."




.png)