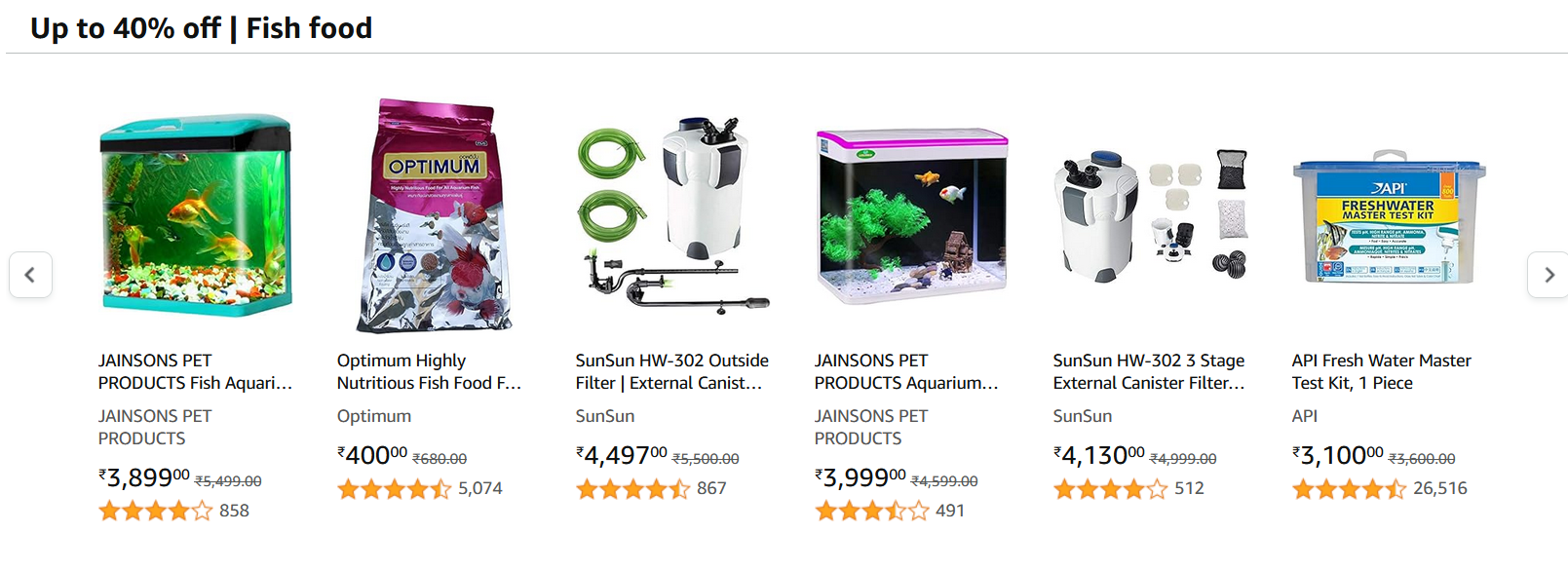বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস :
যদিও উভয়ের কাব্যরীতিতে কোনো মিল নাই। বিদ্যাপতির কবিতায় নাগরিক ঐশ্বর্য
– ছন্দ, অলংকার ভাষা- চাতুর্যের সমাবেশ এবং তা সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের
নিয়ম মেনে। চণ্ডীদাসের কবিতায় কাব্যকথা নির্মাণে কোনো সচেতন প্রয়াস নাই।
প্রাচীন কাব্য-রীতির পর্যায় পরম্পরাও তাই সেখানে নাই। হৃদয়োৎসারিত মর্ম
বেদনা সেখানে ভাষা পেয়েছে যেন অনায়াস চেষ্টায়, কেবল একান্ত আন্তরিকতায়।
গভীরতা তার আশ্রয়, ভাষার সহজ সরলতাই মার্জিত ঐশ্বর্য। বিদ্যাপতির কবিতার
মতো পাণ্ডিত্য সেখানে প্রকাশিত নয়, ভাব-গভীরতার মধ্যে অদৃশ্যে। প্রেমে ও
মিলনে বিদ্যাপতির কবিতায় সখের উল্লাস, চণ্ডীদাসের কবিতায় কেবল-ই আর্তি,
বিষাদ ও বেদনা। পূর্বেরাগ, আক্ষেপান রাগ ও ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতি
অনন্য। যদি আলংকারিক অননুশাসন কাব্যবিচারের মাপকাঠি হয় বিদ্যাপতি
অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু হৃদয়ের মিস্টিক ব্যঞ্জনার বিচারে চ'ডীদাস
দ্বিতীয়-রহিত। তাঁর কবিতায় প্রেম হয়েছে সাধনা এবং দঃখ তার অনযেঙ্গ । শিব - কাঙ্ক্ষিতা উমা অপর্ণার মতোই তাঁর রাধার প্রেম তপস্যা । কবি নিজেই বলেছেন ' রাধার বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমতি যোগিনী পারা । ' দ্বিধাহীন আত্মনিবেদনেই চণ্ডীদাসের রাধার তপস্যার পরিসমাপ্তি ।
ভাববিহ্বল রাধা কৃষ্ণের মরলীধধ্বনি শনেই পাগলিনীকৃষ্ণের দেহ - বর্ণ মরণেও সে উদাসিনী । তার অবস্থা কবির ভাষায়
সই , কে বা শানাইল শ্যাম নাম ।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আব্দুল করিল মোর প্রাণ ।বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শানে কাহারো কথা ॥
সদাই খেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা ।
এই ধ্যানমগ্না যোগিনী কৃষ্ণ - মিলনে প্রার্থনা করেছেসেটাই চণ্ডীদাসের রাধার পক্ষে ম্যাভাবিক । কারণ প্রেম তার কাছে কি একটি বাক্যের স্বল্প পরিসরেই সে তা ব্যক্ত করেছে ‘ বধূ , সে আমার প্রাণ । প্রেমের অতলান্ত চিন্তায় সে বুঝেছে কৃষ্ণপ্রেম ব্যাখ্যার অতীত । তাই ঘোষণা করেছে
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি ।
রাতি কৈন , দিবস দিবস কৈন , রাতি ।
বাঝিতে নারিন , বাঁধ , তোমার পীরিতি ।।
চণ্ডীদাসের রাধা সরলা গ্রাম্য বালিকা , চণ্ডীদাসের কাব্যেও গ্রাম্য সরলতা । চরিত্রের উপযোগী ভাষা , উভয়ে উভয়ের সহযোগী । এই দ্বৈতমিলনই চণ্ডীদাসের কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য । কবিও মানতেন নিখাদ প্রেম উচ্ছাসের বৈরী । তাই লিখেছেন
‘ শন বিনোদিনী পিরীতি না কহে কথা ' ।
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই চৈতন্যযাগের পর্বেবর্তীকালের কবি । সুতরাং চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাব তাঁদের কবিতায় নাই । তাঁরা ভক্ত নন , কবি ; সাধক যদি হন , তবে সে কাব্যসরস্বতীর । রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে । তাঁদের রাধা শখে , প্রেমের বশেই কষ্ণে অনুরোগিণী । উভয়ের আবির্ভাবে কালগত সদৃশতা থাকলেও উভয়ের মনোধর্মে— ছিল প্রচার বৈপরীত্য ।
বিদ্যাপতি ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং মিথিলার রাজসভাকবি । তার চিহ্ন আছে তাঁর চিত্রিত রাধাচরিত্রে । সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নায়িকার প্রেমের নানা পর্যায়ক্রম আছে । পূর্বেরাগ , অভিসার , মান ইত্যাদি সেই পর্যায়গুলি যথারীতি
সখি কি পছসি অনূভব মোয় ।
সোই পীরিতি অনরোগ বথানিএ
তিলে তিলে নতন হোয় ॥
অন্যপক্ষে , চণ্ডীদাসের কবিতায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় নাই , তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিদগ্ধ ছিলেন এমন কোন প্রমাণও নাই । তাঁর কবিতার ভাষায় আশ্চর্য সরলতা , রাধাচরিত্রেও সারল্য । সে প্রেম অন , ভব করে , কিন্তু তার ব্যাখ্যায় সম্পর্ণে— অপারগ— ‘ বসিয়া বিলে থাকয়ে একলে না শানে কাহারো কথা'— এই ভঙ্গিতেই তার প্রেমান , ভূতির প্রকাশ । আপন অনূভুতি সম্পর্কে তার বক্তব্য
বদন থাকিতে না পারে বলিতে
তেই সে অবলা নাম ।
‘ বেহসৌন্দর্যের লীলাচাঞ্চলা ' প্রকাশে বিদ্যাপতির দৃষ্টি দেহেই নিবদ্ধ , চণ্ডীদাসের দৃষ্টিভঙ্গি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত :
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর ।
কৃষ্ণের এ - উদ্ভিতে নাই কোন বাস্তব বর্ণনা , এ - ভাষার সংক্ষা ব্যঞ্জনা শব্দেই অনভববেদ্য । বিদ্যাপতিতে আছে দেহের তপস্যা , চণ্ডীদাসে বেদনার সাধনা । বেদনায় চণ্ডীদাস যদি একট , কটাক্ষ মেশান , তবে তা হয় যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেও
ঈর্ষণীয় সাহিত্য । পনেমিলনে রাধার প্রশ্ন—
দখিনীর দিন দখেতে গেল ।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ।
আমি এতেক সহিন , অবলা বলে ।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে
এমনি একটি কাব্যিক নিদর্শন ।
প্রার্থনার পদেই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের একট , কাছের মানুষ । তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম সমূত - মিত - রমণী সমাজে ’ বীতস্পৃহ হয়ে যখন তিনি দেহি তুলসী ভিল ' দেহ - নিবেদন করেছেন ভগবৎ - কপার অপেক্ষায় , তখন তিনি পাণ্ডিত্যের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে না পারলেও চণ্ডীদাসের মতোই ভক্তি - নিবেদিত প্রাণ কবি হয়ে উঠেছেন ।
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন , চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকল , বিদাপতি নবীন এবং
মধর । একের উপকরণ হৃদয়ের প্রগাঢ় উপলব্ধি , অন্যের উপাদান মহৎ সৃষ্টির উত্তরাধিকার । এখানেই দুই শ্রেষ্ঠ কবির চেতনা ও প্রকাশ রীতির বিশেষত্ব । এভাবেই রবীন্দ্র - উত্তির যথার্থতা অনুধাবন করা যায় ।
চণ্ডীদাস :
পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালীন অথবা সামান্য পরবর্তীকালের কবি । চৈতন্য তাঁর গান আম্বাদনে বিহ্বল হয়ে যেতেন , সুতরাং তিনি অন্তত চৈতন্যপরবর্তীকালে জন্মাননি । তাঁর কবিখ্যাতিতে মগ্ধ অনেক কবিই এই ভণিতায়
পদরচনা করেন । জানার উপায় নাই , আমাদের আলোচ্য চণ্ডীদাসের পদ ঠিক কতগুলি এবং ঠিক কতজন চণ্ডীদাস বাংলার কাৰ্যাকাশ আলোকিত করেছেন । তবে দঃখের পদাবলীকার চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যমাধহূর্যে শধে , ঐচৈতন্য বা বৈষ্ণবজন সমাজকেই নয় , আপামর বাঙালীর হৃদয় আলোড়িত করেছেন বিগত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে । অন্য কোনো কবি কেবল ভণিতাটক , ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি ।
সরলতা ও গভীরতা চণ্ডীদাসের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য । সরলতা যেমন কবির ভাষায় , তেমনি তাঁর চিত্রিত রাধা চরিত্রেও । বলাবহল্য , চণ্ডীদাসের পদরচনার বিষয় প্রেম । রাধা নানক একটি গ্রাম্য বালিকার সরল ও অকপট ' অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহ কি রূপান্তর ঘটাল , তারই অসাধারণ প্রকাশ তাঁর রচনায় । রাধা চরিত্র বর্ণনায় চণ্ডীদাস কখনো তাকে বিদগ্ধা করে তোলেন নি । তার বৈদগ্ধ্য যা কিছু জন্মেছে
তা শব্দে কৃষ্ণপ্রেমের অভিজ্ঞতায় ও প্রেমের রহস্য - উপলব্ধিতে । বিদ্যাপতির মতো
রসশাস্ত্র অনুযায়ী প্রেমিকার প্রেম - উপলব্ধির বিশ্লেষণ চণ্ডীদাস চিত্রিত করেন নি ,
তব্দ তাঁর রচনায় রাধার প্রেম - অভিজ্ঞতার নানা পর্যায় ব্যাখ্যাত হয়েছে ।
প্রথম প্রেম - অনভেবে সে সলজ্জা , যথেষ্ট চঞ্চলাও :
ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায় ।
কৃষ্ণের অঙ্গ - সাদৃশ্যে প্রকৃতির মধ্যেও সে খ’জে পায় প্রেমের উপাদান :
মন উচাটন বিশ্বাস সঘনসখীদের সঙ্গে যমনায় জল আনতে গেছে সে । কিন্তু সেখানেও কৃষ্ণপ্রেম প্রকৃতিতে
কদব - কাননে চায় ॥
অন্বিত হয়ে ধরা দেয় তার কাছে
সথীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয় ।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয় ॥
শয়নে - স্বপনে - জাগরণে সর্বত্রই তখন প্রেম তার হৃদয় জুড়ে অবস্থিত । কৃষ্ণপ্রেম
ও নিজের অন্তরকে বিশ্লেষণ করতে না পারলেও আপন উপলব্ধিকে সে সরল বিশ্বাসে
প্রকাশ করতে পারে
বধূ , সে আমার প্রাণ ।
-এই আপাতসাধারণ উত্তির মধ্য দিয়েই তার প্রেমের গভীরতা অনন্যসাধারণ হয়ে
ফটে উঠেছে ।
রাধার বিশ্বস্ত প্রেম প্রতিহত হয়েছে কষ্ণের প্রদত্ত বিরহদশায় । যাকে সে এত
ভালবাসে তার কাছে প্রেমের যোগ্য প্রতিদান লাভ সম্ভব হয়নি রাধার পক্ষে । অথচ
কৃষ্ণ - অনরোগ ভিন্ন অন্য চিন্তাও তো নাই রাধার । ফলে তার অন্তরের জ্বালা প্রেমিকের
মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে তার চৈতন্যোদয় ঘটাক এই কামনায় রাধা উচ্চারণ করেছে
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ।
সম্পর্ণে নিরাভরণ তার ভাষা । কিন্তু প্রেমিককে সচেতন করে তোলার শ্রেষ্ঠ
উপায়টকে , ব্যঞ্জিত হয়েছে এই আপাতসরল কামনার মধ্যেও ।
অবশেষে কামনায় সিদ্ধি । কৃষ্ণের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছে রাধার । কিন্তু তখন
তো বিরহানলে দগ্ধ - অন্তর রাধা মিলনের মাধ্যর্যের সঙ্গে বিরহের ব্যাকুলতার সঙ্গেও
পরিচিতা । প্রেমোন্মেষের প্রথম অভিজ্ঞতার সরলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছুটা
তিক্ত অভিজ্ঞতাও । সরলা হলেও রাধা তার সেই অভিজ্ঞতাকেও তো ভুলতে পারে
না । সহজ অথচ মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সে প্রকাশ করে আপন অনভেব :
দখিনীর দিন দখেতে গেল ।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ৷
রাধা জানিয়েছে সে ' অবলা ' বলেই এত কষ্ট সহ্য করতে পারল , পাষাণ হলে কিন্তু
এ দঃখভার সহনীয় ছিল না — ' ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ' ।
তব , কৃষ্ণভিন্ন অন্যতর চিন্তা তো রাধার অন্তরে নাই । কৃষ্ণ তাকে যত দুঃখ
দিক , কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়ে সে যত কষ্ট পাক , তার কৃষ্ণ - অনুরাগ তো কখনো নিবৃত্ত
হবার নয় । সুতরাং আত্মনিবেদনের বেলায় সে শব্দে , এ জন্মেই কৃষ্ণকে দয়িতরূপে
কামনা করেনি , জন্মজন্মান্তরেও তাকে পাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছে
বধূ কি আর বলিব আমি ।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হয়ো তুমি ||
এই চিরকালীন সমপি'তচিতোই চণ্ডীদাসের রাধা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । চণ্ডীদাসের
ভাষা কোন সচেতন প্রয়াসের ফল নয় , আত্মগত উপলব্ধির বাঙময় রূপ । সে ভাষার
দক্ষতায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্যের , দীর্ঘ দিনের অধ্যয়ন- তপশ্চর্যার প্রয়োজন নাই , অপরিহার্য কেবল অলোকসামান্য হৃদয়ান , ভর্তির । চণ্ডীদাস সেই সম্পদেই বলীয়ান । তাই তাঁর রচনা নিসর্গের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মতো আমাদের মনকে আবিষ্ট
করে জানায় এক কবির কথা হৃদয়ের অনাবিল ভাবপ্রকাশে যিনি সরল অথচ ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষাশ্রয়ী ।
বিদ্যাপতি - চণ্ডীদাসের উত্তরাধিকার :
বৈষ্ণব পদসাহিত্যের দুটি ধারা । একটি বিদ্যাপতি - প্রবর্তিত ভাষা - ভাষান যঙ্গের বর্ণাঢ্যতায় উচ্ছল ধারা ; গোবিন্দদাসে তার অনুক্রমণ । অন্য ধারা সহজ ভাষায় ভাবগভীরতার পরিচয় । সে - অবদান চণ্ডীদাসের , জ্ঞানদাস প্রমথের পদে তারই অনশীলন । ' সহজ কথা যায় না কহা সহজে ' , রবীন্দ্রনাথের এ উত্তকে অযথার্থ প্রমাণ করেছিলেন চণ্ডীদাস , আধ্যাত্মিকতাকেও সহজ ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন । চণ্ডীদাস সাধক , জ্ঞানদাস সচেতন শিল্পী । পদরচনায় তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ের পথই অনসেরণ করেছেন । কিন্তু তাঁর মানসিকতার সঙ্গে চণ্ডীদাসেরই ছিল আশ্চর্য সংযোগ । তাঁর শ্রেষ্ঠ পদগুলি চণ্ডীদাসকেই স্মরণ করায় । সারল্য ও আন্তরিকতায় যখন তাঁর কাব্যবীণা বাঁধা , তখনই তিনি অকৃত্রিম ও যথার্থ শিল্পী । মনোভঙ্গিতেই এই দুই কবি এক । চণ্ডীদাসের রাধার উক্তি ‘ ব'ধ , সে
আমার প্রাণ । জ্ঞানদাসের রাধা বলেছে
তোমায় আমায়
এবং একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি ।
তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে
" ভাবনা ও ভাষায় , কবি - চেতনায় ও প্রকাশে এই একাত্মতার কারণে একই পদে উভয়ের
ভণিতা দেখা যায় । রসজ্ঞ বৈষ্ণবের পক্ষেও সম্ভব হয় না । প্রকৃত পদকতার নাম
নির্ধারণ করা , যদিও সর্বজনস্বীকৃত মত এই যে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা বড়
কবি ছিলেন ।
এই সকল কারণে চণ্ডীদাসের উত্তরসূরী অথবা ভাবশিষ্যরূপে জ্ঞানদাসকে গ্রহণ
করা হয় ।



.png)