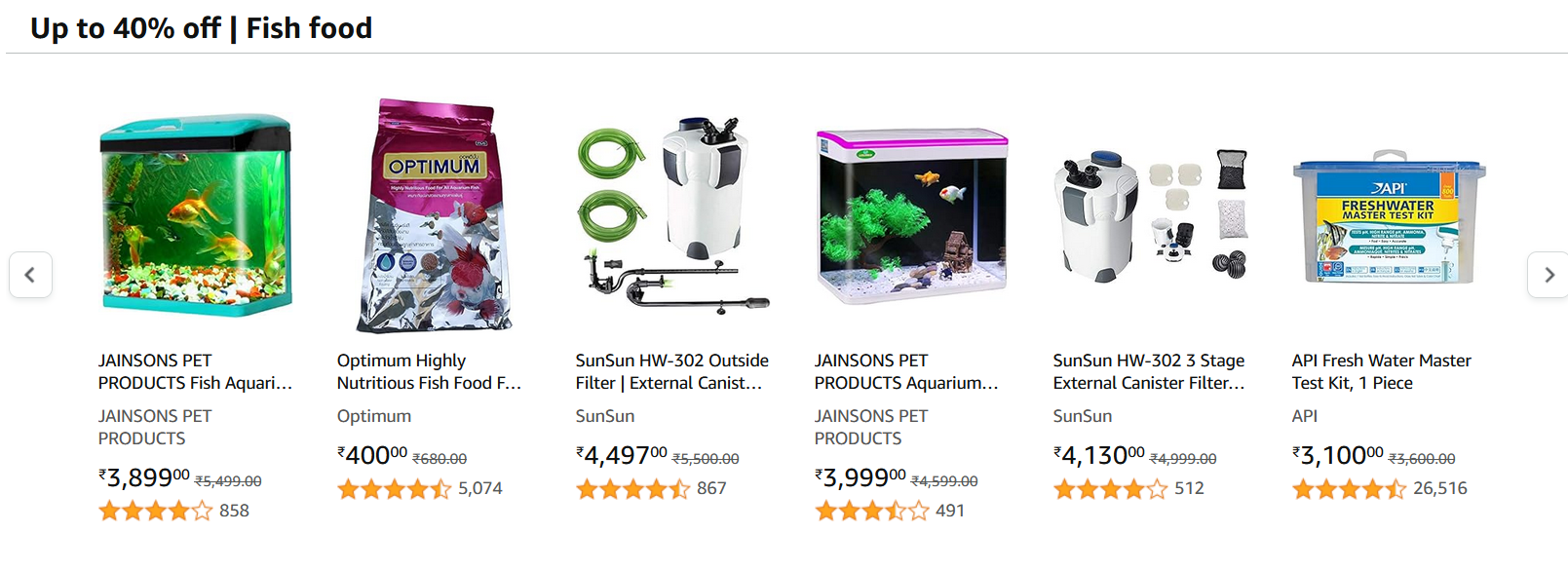মঙ্গল কাব্য
মঙ্গলস,চক গান, ব্রতকথা ও লোককাহিনী যখন কাব্যাকারে লিখিত হল তখন তার সাধারণ পরিচয় হল মঙ্গলকাব্য । ঠিক কবে থেকে এই লিখিত রূপের আবির্ভাব ঘটেছিল তা জানা যায় না। পঞ্চদশ শতক থেকে তার সাক্ষাৎ মেলে। সতরাং আশা করা যেতে পারে, আরও দু-একশ বছর আগে থেকেই এর প্রস্তুতিপর্ব অথবা কৈশোর কাল দেখা দিয়েছিল। বিশেষ, তার্কী আক্রমণের ফলশ্রুতিতেই অপৌরাণিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মিলন সম্ভব হয়েছিল এবং মঙ্গলকাব্য এই নবসৃষ্ট দেবদেবীরই বন্দনাগান। ফলত, ত্রয়োদশ শতকেই তার সূচনা হওয়া সম্ভব। লক্ষণীয়, মঙ্গল- কাব্যের আখ্যানের কাঠামো সন্দের অতীত থেকেই গ্রামীণ সমাজে মৌখিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। তারই নব রূপান্তর, সম্প্রসারণ ও লিখিতরূপে পাওয়া গেল মঙ্গল- কাব্যকাহিনীতে।
মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের প্রাথমিক রূপ অশিক্ষিত জনের ভয়-ভক্তি-সংস্কার- বিশ্বাসে সষ্ট। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ও রোগভীতি এই সৃষ্টির মলে কাজ করেছিল। বাংলায় আর্য আগমনের আগেই বাঙালীরা এই দেবদেবী রূপের কল্পনা করে। ফলত, এই দেবদেবীগুলি সভ্য সমাজের মার্জিত রুচির দেবতা নন; ক্রোধ ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির মানষী দুর্বলতা দিয়ে গড়া তাঁদের রুচি। অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলেই তাঁদের মাহাত্ম্যকথায় ভক্তের আসক্তি। মঙ্গল অর্থ' কল্যাণ। মঙ্গলসাধন করেন বলে এ'রা মঙ্গল দেবদেবী এবং এদের নিয়ে রচিত আখ্যান মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য নামের আরও কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ঐতিহাসিক। এই কাব্য গাঁত হত মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত; মঙ্গল সরে গাঁত হত এই গান বা আখ্যান; মঙ্গল নামক অসুর নিহত হয়েছিল দেবীকতক এবং এই জাতীয় কাব্যকাহিনী গলিতে দেবদেবীর বিজয় অর্থাৎ মাহাত্ম্য বর্ণিত । এই চত,বিধ কারণেও নাকি মঙ্গলকাব্য নামে আখ্যাত হয়েছে কাব্যগুলি । মলত মনসা, চণ্ডী ও ধর্মঠাকারের মাহাত্ম্য মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ।
মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ
তুর্কী আমলের 'তামস যুগের' অবসানে বাংলা সাহিত্য যখন আবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল তার অন্যতম মূখ্য ধারা হয়ে উঠল মঙ্গলকাব্য-ধারা । মঙ্গলকাব্য নামটি প্রাচীন নয়, মঙ্গল গানের কথা যদিও অশোকের সময়েও অজানা ছিল না। গৃহ ও গোষ্ঠী- কল্যাণমূলক গীতিই মঙ্গল গান আর ব্রতকথা ও লোকগাথার
ক্ষুদ্র পরিসর ছাড়িয়ে যখন তা ছন্দ অলংকারে সমৃদ্ধ বিশাল কাব্যে পরিণত,
তখন তার নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল কাব্যকাহিনীর প্রভাব বাঙালী সমাজে
ফল্গু,স্রোতের মতো অন্তঃসলিলা ছিল পঞ্চদশ শতকের আগে উনিশ শতকে এদেশে ইংরেজি
সভ্যতার প্রসারের পরে তার পরিণাম হয়েছে ক্ষীয়মাণ। মধ্যবর্তী কালে
(পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতকে ) মঙ্গলকাব্য রচনা ও পাঠের বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়
বাঙালী সমাজে।
কোমবদ্ধ আদিম জীবনধারায় বাঙালী কৃষি, গৃহশিল্প ও শিক্ষা—এই তিনের উপরই নির্ভরশীল ছিল। ভয়, ভক্তি, বিস্ময়ে সে দেবতার কল্পনা করেছে এবং তারই মাহাত্ম্য বর্ণনায় রচনা করেছে ব্রতকথা। গার্হস্থ্য জীবনে জন্ম বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি- স্বস্ত্যয়ন ও গৃহদেবতার প্রাত্যহিক পূজো এবং সামাজিক জীবনে ফসল বোনা, ফসল তোলা, ঋত, উৎসব, গ্রামদেবতার বাৎসরিক পূজা ইত্যাদিকে উপলক্ষ করে এইসব গান রচিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে ও পরবর্তীকালে আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মে'র বঙ্গদেশে প্রসারের ফলে এবং সমাজে বৈদিক ক্রিয়ান রক্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে লোকায়ত এই চিরন্তন প্রথা আর্যে তর অনভিজাত অশিক্ষিত জনসাধারণ, বিশেষ মহিলালের আশ্রয়ে লালিত হয়েছিল। তুর্কী আমলে উচ্চবর্ণের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও এই ধারা ছিল বহমান। অবশেষে পঞ্চদশ শতকে ও পরবর্তী তিন শতকে উচ্চনীচ ভেদাভেদে সকল শ্রেণীর বাঙালীর সাহিত্যচেতনা ব্রতকথা-ছড়া-পাঁচালীর চিরায়ত কাঠামোকে শিল্প সুষমামণ্ডিত করে রচনা করেছে মঙ্গল কাব্য ।
'মঙ্গল' শব্দটির অর্থ গৃহকল্যাণ। মঙ্গল দেবদেবীরা মূখ্যত বাস্ত ও গ্রাম- দেবতা। মহামারী, সর্প, ব্যাঘ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি জাগতিক অকল্যাণের হাত থেকে তাঁরা ভক্তকে রক্ষা করেন। বসন্ত রোগ নিরাময়ের দেবী শীতলা, চর্ম রোগের ধর্মঠাকরে। সর্গ ও ব্যাঘ ভয় দূর হয় যথাক্রমে মনসা ও দক্ষিণ রায়ের পূজোয় । এইভাবে এক একটি বিনাশের জন্য কল্পিত হয়েছেন এক একটি দেবতা অথবা দেবী। বাংলার গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে ভয়-ভক্তির মিশ্রণে এ সকল দেবদেবী আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন জৈন, বৌদ্ধ ও আর্য ধর্মে'র প্রভাবের পাশাপাশি। তুর্কী আক্রমণের ফলস্বরূপ আর্যধর্ম যখন বিধস্ত, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নিরক্ষর ও অন্ত্যজ শ্রেণী আত্মরক্ষায় ও সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার লোভে যখন দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে তৎপর, ক্ষয়িষ্ণু, হিন্দ, সমাজ দিশাহারা ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে কামনা করেছে এমন দেবদেবীর আবির্ভাব, যিনি এই সার্বিক দরবস্থার হাত থেকে বাঙালীকে উদ্ধার করতে পারেন। এ বিষয়ে মঙ্গলদেবদেবীরা আদর্শ স্থানীয়। কারণ, ভক্তকে তাঁরা শব্ধে রক্ষা করেন না, ভক্তের জন্য উচিত-অনুচিত সর্ব কর্মেই তাঁরা দড়। সতরাং নিম্নকোটির দেবদেবী তুর্কী আক্রমণের ফলশ্রুতিতে উচ্চকোটিরও উপাস্য হয়ে উঠলেন—সমগ্র হিন্দু সমাজ মক্তি ও শান্তির আশায় লোকায়ত দেবদেবীর
আরাধনায় আত্মনিয়োগ করল। মিলন ঘটল পৌরাণিক ও লোকায়ত দেবদেবীর। ব্যাধের
দেবী চণ্ডী ব্রাহ্মণেরও পূজো পেল। যা ছিল একসময়ে অন,চিত কর্ম, তা-ই
অপরিহার্য হয়ে উঠল সামাজিক পরিস্থিতিতে ।
করা হল।
- কিন্তু এইসব দেবদেবীর মধ্যে আর্যে তর প্রভাবে রুক্ষতা, ব্রুরেতা, কিছটা নাঁচতারও নিদর্শন ছিল। সেগালি যথাসম্ভব মার্জিত হল। সেই সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে একটি আত্মীয়তা কল্পনা করে তাঁদের আর্যে তর ভাবটাক কেও যথাসম্ভব দূরে এভাবে মনসা হলেন মহাদেবের মানসকন্যা, চণ্ডী শিবের পত্নী, ধর্মঠাকরে বিষ্ণু, অবতার ; কখনো বৃদ্ধ, শিবও সার্যের সঙ্গেও যুক্ত। আর্যে তর দেবদেবীর এই কৌলীন্যলাভে তাঁদের মাহাত্মা বর্ণনে ব্রাহ্মণেরও আগ্রহ দেখা দিল। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কবিরাও রচনা করলেন মঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মাকন্দরাম চক্রবর্তী, ধর্ম মঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ । সতরাং একটি বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায়, সমাজের দঃসময়ে বাঙালীর শাস্তি- বাসনায় ব্রতকথা, ছড়া, পাঁচালীর আখ্যানঅংশের মার্জনা ও সম্প্রসারণের দ্বারা মঙ্গল কাব্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল এবং মঙ্গলকাব্য সেইসব দেবদেবীর মাহাত্ম্যসচেক কাহিনী যাঁদের স্থান সংস্কৃত পরাণে ছিল না।
মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন
মঙ্গলকাব্য কাহিনীর সূত্র প্রাচীন ব্রতকথা ছড়া ও পাঁচালী। ফলত প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয়ই তার কাহিনী অংশে বিতে। মনসা মঙ্গলের নায়ক চাঁদ বেনে সওদাগর, চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক কালকেত, ব্যাধ, ধর্মমঙ্গলের নায়ক সামন্তরাজ লাউসেন। তাদেরই ভাগ্যবিপর্যয় ও দেবদেবীর প্রসাদে বিপত্তির ইতিহাস তিন মঙ্গলকাব্যের কাহিনী। অথচ বণিকবৃত্তি, শিকার উপজীবিকা ও স্বাধীন রাজত্বভোগ তখন বাঙালীর কাছে স্মৃতিমাত্র, বাস্তবে তার কোনো পরিচয় নাই । তবু এই কাহিনী ও দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রকাশের অবসরে কবিরা সমকালীন সমাজের যেটা কর তথ্য তুলে ধরেছেন বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে তার মূল্যেও কম নয় এবং মলত তার উপর নির্ভর করেই মধ্যযাগের বাংলার ইতিহাস রচিত ।
চতুর্দশ শতক থেকে বাংলার সংস্কৃতিতে দুটি ধর্মে'র প্রভাব হিন্দ, ও
মুসলমান ধর্ম । পঞ্চদশ শতকেও এই দাই ধর্মাবলম্বীরা পরস্পরের থেকে
বিচ্ছিন্ন। আছে বিদ্যাপতির কীর্তি' লতায় - "হিন্দ, তরকে মিলল বাস। একক
ধর্মে অংকে উপহাস’–হিন্দ-তরেকের বাস নিকটে, কিন্তু একের ধর্মকে অন্যে উপহাস
করে।
- এই বিচ্ছিন্নতাবোধ দূরে হয়েছে ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের
চণ্ডীমঙ্গলে। কালকেতুর রাজ্যের পশ্চিম অংশ হাসনহাটি ম, সলমান প্রধান অঞ্চল।
সেখানে
-
পাঠান বসিল নানা জাত ৷
বসিল অনেক মিঞা আপন টবর নিঞা
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
খুব ভোরে উঠে তারা নমাজ পড়ে, হাতে নেয় সোলেমানি মালা, পীরের মোকামে সন্ধ্যায় জ্বালায় বাতি। তারা কোরান পড়ে হাটে বিলায় পীরের শিরনি। গেলেও রোজা ছাড়ে না। 'কম্বোজ-বেশ ধারী এদের মাথা মুড়োন, বুক-ঢাকা দাড়ি । এদের সঙ্গে কিন্তু হিন্দুদের কোনো বিরোধ নাই ।
পাঠান সুলতানদের আমলে হিন্দুরাও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হতেন। [ চতুৰ্দশ শতকের সালতান জালালদের দিনের মহামন্ত্রী সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। সুলতান পণ্ডিতপ্রবর বৃহস্পতি মিশ্রকে বিশেষ সম্মান দিতেন। হাসেন শাহর দুই মন্ত্রী রূপে ও সনাতন ছিলেন হিন্দু । রাজস্ব আদায় ও এই সংক্রান্ত ব্যাপারে ও 'জমিদারী পরিচালনায় কায়স্থদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। রকোন্দিন বারবক শাহের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ছিলেন মালাধর বসু। পুরুষান ক্রমে এই পরিবার রাজকার্য করে গেছেন। কায়স্থদের রাজকর্মে'র উল্লেখ করে সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম লিখেছেন: 'কায়স্থ কারকুন যত করে লেখাপড়া। হোসেন শাহের কায়রে বৃদ্ধি ও প্রতাপে রাজারাও এক সেনাপতি রামচন্দ্র খান ছিলেন কায় । তাঁদের সমীহ করে চলতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরা তার সযোগও গ্রহণ করতেন । [ সপ্তগ্রাম মূলকের চৌধুরীদের বার্ষিক বিশ লাখ টাকা আদায়ের সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন গোবর্ধন দাস।] বৈদ্য ও বণিকরাও উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হত। বণিকেরা যারা 'লেখা জোখা করে টাকাকড়ি' তাদের লোকঠকানোর সকৌতুক ইতিহাস আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। তবু মুসলমান রাজা ও জমিদারদের হাতে হিন্দ প্রজারা নির্যাতিত হত না তা নয়। মামদ শরীফের নির্যাতনেই মন্দেরামকে গৃহত্যাগ করে বাঁকড়া রায়ের আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তাঁর কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে। 'নেউগি চৌধুরী নই, না রাখি তালকে। রাজব আদায় জমির মাপ নির্ধারণ সব ব্যাপারেই কিছুটা অবিচার প্রশ্রয় পেত এবং মুখ্যত ঠকত সাধারণ মানুষেরাই।
ব্রাহ্মণেরা মুসলিম নীতি-পদ্ধতিকে স্লেচ্ছ আচার বলে সযত্নে পরিহার করতেন। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ষোড়শ শতকেই একটা প্রীতির সম্পর্কে গড়ে উঠে। রুদ্ধে শ্রীচৈতন্য কাজির বাড়ি দলবলসহ হাজির হলে তিনি চৈতন্যের মাতামহের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কে'র কথা উল্লেখ করেছেন :
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা ।
দেহ সম্বন্ধে হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ।।
মাসলমানরাও হিন্দ, আচার পছন্দ করতেন না। তাঁরা মনে করতেন হিন্দ আচার গ্রহণে শাসকজাতির মর্যাদা হানি হয়। সুতরাং যবন হরিদাস যেহেত 'যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার তার জন্য ব্যবস্থা হয় 'ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।' ব্রাহ্মণদের যেমন জাতিত্বের গর্ব' ছিল মসলমানরাও নিজেদের 'মহাবংশজাত’ মনে করত। হিন্দুর পক্ষে চরম শাস্তি ছিল 'জাতিনাশ'। রোধ ও প্রতিহিংসার বশে তা করা হত। কখনো লোভের বশে হিন্দুরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করত। কিন্তু দারিদ্র্য ও মৃত্যু অপেক্ষাও ধর্মে'র স্থান ছিল উচ্চে। ব্রাহ্মণ্যবর্ণের লোকের কাছে দারিদ্র্য ছিল তচ্ছে। কৃত্তিবাস লিখেছেন 'ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড়রাত্রি উপবাসে'। ম কান্দরাম-
তৈল বিনা কৈল, স্নান করিল, উদক পান
শিশ, কাঁদে ওদনের তরে।
তবু, ধর্ম'কে সহায় জেনে তাঁরা দারিদ্র্যকে বরণ করেছিলেন।
বৃত্তিবিভাগ মোটামটিভাবে মেনে চলা হত এবং মিশ্রবর্ণের হিন্দ ও মাসলমানদের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি ছিল একচেটিয়া। 'শ্রীবাসের বা সি'য়ে দরজী যবন'। বাস্তব প্রয়োজনে উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের উপর কিছুটা নির্ভরশীল ছিল।
পঞ্চাদশ শতকের শেষভাগ থেকে নবদ্বীপ-শাস্তিপর অঞ্চল হিন্দ, সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায়
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ৷৷
ত্রিবিধ বসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ ।
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ৷৷
ন্যায় ও স্মৃতির চর্চা ছিল ব্রাহ্মণের একচেটিয়া। ব্যাকরণ- কাব্য-পরাণপাঠ অব্রাহ্মণেও করতে পারত। উচ্চশিক্ষার জন্য ছিল চতাপাঠী, সাধারণ শিক্ষার জন্য টোল । দরিদ্র কায়স্থ ও প্রাথমিক ভাষা ও গণিত শিক্ষা দিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। সাধারণ পূজোরী ব্রাহ্মণ ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দ, অলংকার, স্মৃতি, পরাণ পাঠ করেই পাঠে ক্ষান্ত হতেন। উচ্চ বর্ণের মহিলারাও পড়াশোনা করতেন। এমন কি তাঁদের দু-একজন কাব্যও রচনা করেছেন। চাকরির আশায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরা বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসীও শিক্ষা করত। বিশেষ তহশিলের কাজের জন্য কায়থকে শিখতে হত অঙ্ক। বেনেরা তেজারতি কারবারও করত।
দেশের প্রধান সম্পদ ছিল ধান। এছাড়া ছিল কাটির শিল্প, যার মধ্যে প্রধান ছিল কৰ্ম্ম-শিল্প। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত অবাধে । খেয়াঘাট ছাড়া শল্ক আদায় তেমন
হত না। পাঠান আমলে দেশের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও মোগল আমলে আর্থিক অবস্থার
অবনতি ঘটে। 'আঁঠ, ঢাকি বস্ত্ৰ দিহ পেট ভরি ভাত' অথবা 'আমার সন্তান যেন থাকে
দুধে ভাতে'—এটাই তখন হয়ে উঠেছিল সাধারণ বাঙালীর আকরিক কামনা।
যদ্ধেবিগ্রহ, শাসক শ্রেণীর বিলাসিতা এবং বাংলার অর্থ দিল্লিতে ও বাংলার
বাইরে চলে যাওয়াতেই এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে।
ত্বকী অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন এবং সেইসঙ্গে মসজিদ নির্মাণ। এর ফলে হিন্দুদের মনোবল ভেঙে পড়ে এবং তারা মনে করতে থাকে এই পরিণাম ঈশ্বরেরই দান এবং স্বীয় ফলে 'ধর্ম' হৈলা যবনরূপী ভাবতে তাদের কষ্ট হয়নি। মুসলমানের আরাধ্য পীর হিন্দুর দেবতা সত্যনারায়ণ রূপে —ধর্মাচরণে হিন্দ, হয়েছে কয়েকক্ষেত্রে মসলমানের অননুসারী ; যেমন ভোগ হিসাবে দেবতাকে শিরনি দান। অবশ্য চৈতন্যের আবির্ভাবে (১৪৮৬-১৫৩৩ খীঃ) নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বাঙালী হিন্দ— জাতবিচারের নির্মমতাও দূর হয়েছিল। কিন্তু কৌলীন্য প্রথার প্রভাব পরবর্তীকালে হিন্দরে এই সমন্বয় সাধনাকে অনেকাংশে বিপর্যস্ত করে সামাজিক নানা অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মে'র মত ব্যাপকতা লাভ না করলেও শৈবধর্ম ও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। [ অষ্টাদশ শতকে রচিত শাক্ত সাহিত্যে আছে তার পরিচয়। ]
মাসলমান শাসকেরা বিশ্বান না হলেও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। খাঁ মহাভারত অনুবাদে, রুকন,দিন বারবক সাহ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনায় প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করেন। সতরাং মধ্যযুগের বাংলায় সংস্কৃত, বাংলা গ্রন্থরচনা ও সাহিত্য। চর্চা শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাধাহীনভাবে এগোতে পেরেছে। ধর্মসাধনা ও অবসরবিনোদন উভয়েরই উপায় ছিল রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি পুরাণপাঠ ও শ্রবণ, মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার মঙ্গলকাব্য শ্রবণ, পাঁচালী কথকতায় সময়-যাপন এবং বৈষ্ণবদের পক্ষে নামসংকীর্তন। এই ধর্ম পরিমণ্ডলে বাস করে বাঙালী অল্পেত, ষ্ট, নিরভিমানী, বিনয়ী, সংযমী ও দারিদ্রাসহ একটি জাতিতে পরিণত হয়েছিল যার আদর্শ চরিত্র রাম ও সীতা- দঃখের বহতা ধারায় যাঁদের জীবন অভিবাহিত।



.png)