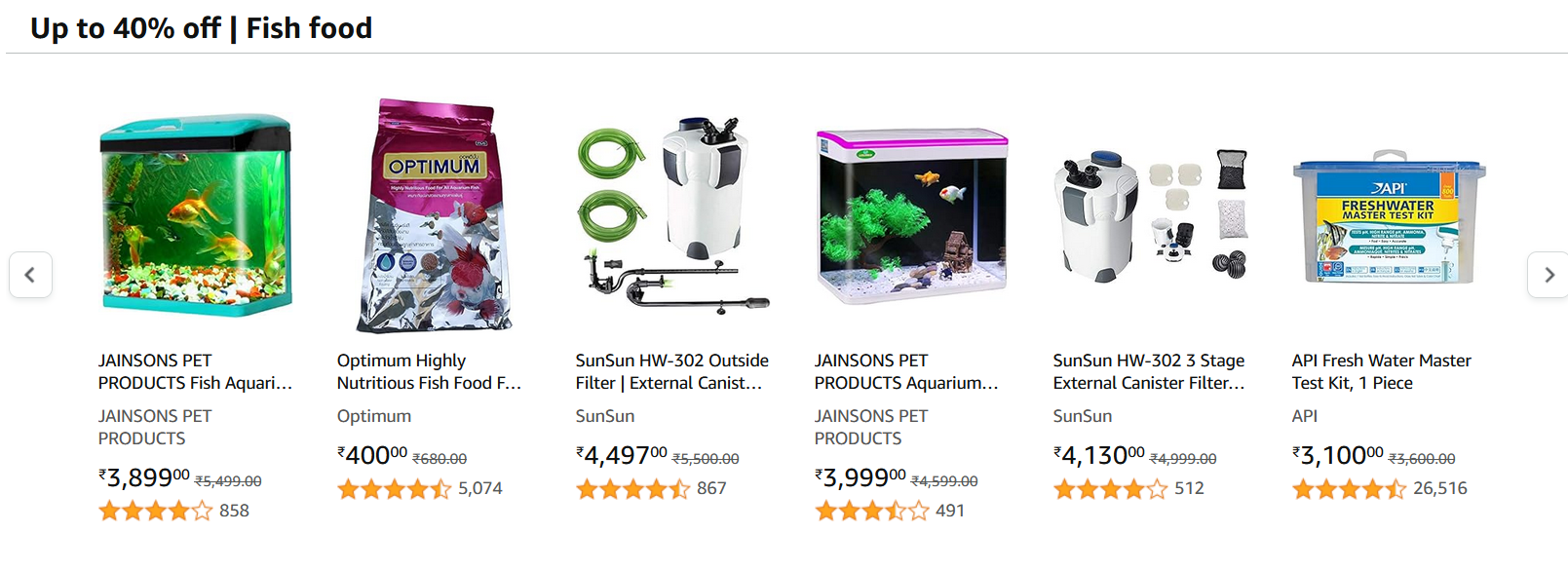বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূলে পথি পাওয়া যায়নি, অনলিখিত যে একটিমাত্র পাখি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তা-ও খণ্ডিত—আদি এবং অন্ত ও মধ্যের কয়েকটি পাতা নাই। তেরটি খণ্ডে বিভক্ত এই কাব্যের খণ্ডিত সহ মোট চারশ আঠারটি পদ বা গান পাওয়া গেছে। প্রতিটি পদের উপরে রাগের উল্লেখ আছে। মুখ্য চরিত্র তিনটি—কাষ্ণ, রাধা ও বড়াই। গৌণ চরিত্রও তিনটি—যশোদা, আয়ান ঘোষ ও তার মা। কাহিনীর বিস্তার কৃষ্ণ-রাধার জন্ম থেকে কৃষ্ণের দ্বারকায় গমনহেত, রাধাবিরহ পর্যন্ত বিস্তৃত। মূখ্য তিন চরিত্রের গতিবদ্ধ কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেজন্যে কাব্যটিকে অনেকে নাট্যগীতির মর্যাদা দান করেন।
-বড় চণ্ডীদাস ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ। তিনি কাহিনীসূত্রের সন্ধান করেছেন ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি পরোণ ও জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দে'র মধ্যে। কিন্তু শখে, সেগুলির উপর নির্ভর না করে তিনি প্রচলিত লোককথা, লোকগাথাকেও কাহিনীতে গ্রহণ করেছেন; বরং একট, অধিক পরিমাণে। ফলত বড়, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়পরবশ গোঁয়ার রাখাল – নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোনো পন্থাকেই সে অনাচিত মনে করে না। তার আকর্ষণ রাধার প্রতি, এগার বছর বয়সেই যে ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং সামাজিক ঔচিত্য সম্পর্কে সচেতন। সে যখন কৃষ্ণের বৃদ্ধির কাছে পরাজিতা, প্রেমের রহস্যে কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকলো- সমাজ-সংসার তুচ্ছ করে যোগিনী বেশেও কৃষ্ণসান্নিধ্যে অনুরাগিণী। বস্তুত, এ কাব্যে কবি প্রেমের সমস্ত দিকই উপস্থিত করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমের আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে স্থান দিয়েছেন প্রেমের বাস্তবতাকে। ফলে মনে হতে পারে কাব্যটি অশ্লীল ; কিন্তু যাগের কথা চিন্তা করলে, বিশেষ, রাধাপ্রেমের ব্যাক,লতা চিত্রণে কবির আশ্চর্য দক্ষতার কথা মনে রাখলে কাব্যটির সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নাই। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই কৃষ্ণপ্রেম বিভোরতাকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন; এ কৃতিত্বও কম নয়। সেজন্য চৈতন্য নিজেও ছিলেন এ-কাব্যের বিশেষ অনুরক্ত।
শ্রীকৃষ্ণেকীর্তনের পাখিটি আবিষ্কার করেন বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বাঁকড়ার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে । ভনিতা থেকে কবির নাম জানা গেলেও আদ্যস্ত না
থাকায় পাখির নাম বা রচনাকাল জানা যায় না। ইতিপূর্বে চৈতন্যজীবনচরিত কাব্য
থেকে জানা গিয়েছিল চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক কাব্যের অংশবিশেষ পছন্দ
করতেন। সেই সূত্র ধরে বসন্তরঞ্জন এই কাব্যটিকেই উল্লিখিত কাব্য ধরে নিয়ে
সম্পাদন ও প্রকাশের সময় (১৯১৬) নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যটির
ভাষা ও শব্দ এবং পাথিটির লিপি ও কাগজ বিচার করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে
এসেছেন যে কাব্যটি রচিত হয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এবং পাথিটির অন লিখনের
কাল ষোড়শ
শতক।
তবে
থাকায় পাখির নাম বা রচনাকাল জানা যায় না। ইতিপূর্বে চৈতন্যজীবনচরিত কাব্য
থেকে জানা গিয়েছিল চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক কাব্যের অংশবিশেষ পছন্দ
করতেন। সেই সূত্র ধরে বসন্তরঞ্জন এই কাব্যটিকেই উল্লিখিত কাব্য ধরে নিয়ে
সম্পাদন ও প্রকাশের সময় (১৯১৬) নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যটির
ভাষা ও শব্দ এবং পাথিটির লিপি ও কাগজ বিচার করে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্তে
এসেছেন যে কাব্যটি রচিত হয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে এবং পাথিটির অন লিখনের
কাল ষোড়শ
শতক।
তবে
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পাথিটিতে কাব্যটির কোনো নামোল্লেখ নাই । পাথিটির মধ্যে প্রাপ্ত একটি চিরকটে (যেখানে পাথিটির কয়েকটি পাতা ধার নেওয়া ও ফেরত দেওয়ার তথ্য লিপিবদ্ধ) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) নামটি উল্লিখিত। সুতরাং কাব্যটির প্রকৃত নাম “শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ” হওয়াও অসম্ভব
নয় ।প্রেম-আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যটিতে সমসাময়িক জীবনচিত্রও ধরা পড়েছে। সামাজিক নীতিবোধ, সংস্কার ও আচার, পালনীয় রীতিনীতি, ঘাটিয়ালের দৌরাত্ম্য, গোয়ালা-জীবন, আত্মীয়তাবন্ধনের রীতি, বেশ-অলংকার-রন্ধনপ্রক্রিয়া, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি জীবনের খুটিনাটি ইতস্তত প্রকাশ পেয়েছে কাহিনীর মধ্যে। তার দ্বারা সে যুগের একটি সামগ্রিক জীবন ছবি হয়তো ফটে উঠে না, কিন্তু পাওয়া যায় তার অনেক রসদ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের বাংলাভাষার একটি প্রামাণিক দলিল। চর্যাপদের পর (দ্বাদশ শতক ) একষ্ণকীর্তন বাংলা ভাষার পরিবর্তনের ধারাটি সম্পর্কে" আমাদের অবহিত করে। চর্যার ভাষা যে বাংলা সে কেবল পণ্ডিত ও গবেষকেরই বোধগম্য। বাংলা ভাষার প্রকৃতি তার প্রবাদ প্রবচন সমেত পরিস্ফুট হল
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ।চর্যার ভাষায় ছিল অপভ্রংশের প্রভাব। ঐকৃষ্ণকীর্তনে তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। অনেক ক্ষেত্রে সে-ভাষা ষোড়শ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যে সাপণ্ডিত বৈষ্ণব কবিদের রচনার মতোই দৃঢ়পিনিদ্ধ :
তীনভ,বনজন মোহি
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃত গৌরব রাধাচরিত্রের বিকাশে, তার মনোভঙ্গির ক্রমবিবর্তনের প্রকাশে। কাব্যটির আরম্ভে রাধা ছিল কৃষ্ণের প্রতি বিতৃষ্ণ। তার বিতৃষ্ণা রুমে রূপান্তরিত হয়ে অনরোগে পরিণত হল। কৃষ্ণের ক্ষণবিচ্ছেদেও তখন "তার অস্তরে দেখা দেয় বিরহের হাহাকার। কবি তার দুঃখাতিকে অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন :
পদাবলী
বিদ্যাপতি :
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কলে ।কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকলে ॥কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা ।দাসী হআঁ তার পাও নিশিবোঁ আপনা ৷
কষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার রান্না নষ্ট হয়েছে, আকল হয়েছে তার প্রাণ। কবি তার মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন তা যে কোন সাহিত্যের পক্ষেই গৌরব ।
যে-ভাষায়পদাবলী
পদ অর্থে' গান । পদ শব্দের ব্যবহার আছে কালিদাসের মেঘদূতে। জয়দেব রিচিত গীতগোবিন্দে গানকে বলা হয়েছে 'পদম। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে- সব গান রচিত হয় তার সাধারণ নাম পদ এবং পদের সমষ্টি পদাবলী – যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী । এইসব পদ প্রধানত গান হলেও কাব্য ও শিল্পরীতির উৎকর্ষের সাহিত্য পদবাচ্য-ও। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় নেগলির স্থান অপরিহার্য।
বিদ্যাপতি :
বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী, তিনি তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলীতে - রাধা কৃষ্ণে বিষয়ক পদরচনা করেন। মিথিলা তখন ন্যায়শাস্ত্র চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। যে-সব বাঙালী ন্যারে পাণ্ডিত্য অর্জনে মিথিলায় যেত তাদের দ্বারাই বিদ্যাপতির পদ বাংলাদেশে সপরিচিত হয়। কিন্তু লিখিত রূপে না এসে এগুলি এসেছিল কণ্ঠস্থ হয়ে। ফলে কালক্রমে পদগুলিতে বাংলা ভাষা মিশ্রিত হয়ে যায় ৷ এই মৈথিলী বাংলা মিশ্রিত ভাষার নাম ব্রজবুলি। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদের মধ্যে এই মিশ্রিত ভাষার লক্ষণ দেখা যায়।
বিদ্যাপতির জন্ম বিহারের মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী নামক গ্রামে। তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকরে । তাঁর পর্বে পরষেরা মিথিলা রাজবংশের সঙ্গে কর্ম সরে জড়িত ছিলেন, কেউ ছিলেন সভাপণ্ডিত, কেউ সেনাপতি। বিদ্যাপতির জন্মকাল সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে অন্য সূত্র থেকে জানা যায়, চতদশ শতকের শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতকের 'বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ছিল তাঁর জীবনকাল । সম্ভবত ১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের অল্প কিছ পরে তাঁর তিরোধান ঘটে। বিদ্যাপতি সংস্কৃত কাব্য, অলংকার ও নানা শাে স পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মিথিলার একাধিক রাজার সভাকবির পদও অলংকৃত করেন। কালধর্মে কবি ছিলেন শৈব; কিন্তু শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য সব
ধর্মে'র প্রতিই ছিল তাঁর সমদর্শিতা। সংস্কৃত, অবহটটে, মৈথিলী ভাষায় তিনি
অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদরচয়িতা
হিসাবেই তিনি সমাদৃত, কিন্তু মিথিলায় তাঁর খ্যাতি ন্যায় স্মৃতি ইত্যাদিতে
স পণ্ডিত এবং স্মৃতিসংহিতার রচয়িতা হিসাবেও।
ধর্মে'র প্রতিই ছিল তাঁর সমদর্শিতা। সংস্কৃত, অবহটটে, মৈথিলী ভাষায় তিনি
অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদরচয়িতা
হিসাবেই তিনি সমাদৃত, কিন্তু মিথিলায় তাঁর খ্যাতি ন্যায় স্মৃতি ইত্যাদিতে
স পণ্ডিত এবং স্মৃতিসংহিতার রচয়িতা হিসাবেও।
বিদ্যাপতির মাতৃ ভাষা মৈথিলী, সংস্কৃত ও অবহট্ টে সাহিত্য রচনা করেন । বাংলাভাষায় তাঁর কোনো পদ না থাকা সত্ত্বেও বাংলা দেশেই কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। তার কারণ, মৈথিলী ভাষায় রচিত তাঁর সাললিত রাধাকৃষ্ণে বিষয়ক পদ। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে মিথিলায় গিয়ে বাঙালী ছাত্র অধ্যয়নসমাপনে দেশে ফিরত ন্যায়বিদ্যার সঙ্গে কণ্ঠে নিয়ে বিদ্যাপতির পদ। এভাবে বাঙালী পরিচিত হল তাঁর অপূর্ব কবিপ্রতিভার সঙ্গে। শ্রীচৈতন্যও আনন্দস্নাত হতেন তাঁর সমধর পদমাধবে। এর ফলে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে তাঁর পদ আরও পরিচিত ও সমাদৃত হল । তিনিও পরিচিত হলেন বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে। বাঙালীর কন্ঠবাহিত হয়ে তাঁর মৈথিলী পদগুলি বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারল না। স্থানীয় ভাষা ও শব্দ মিশ্রিত হয়ে তা এক নবীন রূপ পেল যে মিশ্রভাষার নাম ব্রজবুলি । ফলত বিদ্যাপতি হয়ে গেলেন ব্রজবুলি ভাষার বাঙালী কবি। চণ্ডীদাসের পদ যদি হয় বৈষ্ণবপদগঙ্গার অলকানন্দা, তবে বিদ্যাপতির পদ মন্দাকিনী। উভয়ের মিলিত কাব্যধারায় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ অবগাহন। কবিখ্যাতিতে অক্ষম কবিরাও অননুপ্রাণিত হয়েছেন নিজেদের পদ তাঁদের ভণিতায় প্রকাশে। এমনকি অনেক বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকর্তা (বিশেষ গোবিন্দ দাস) ব্রজবুলির ছন্দ ও সুরতরঙ্গে প্রাণিত হয়ে তাতেই পদরচনায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ফলত মিথিলার কবি হয়েও বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন নানা ভাবে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এবং বাঙালী কতক তাঁর পদগুলিকে বাঙালীর সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করায় বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় বিদ্যাপতি হলেন অপরিহার্য।
বিদ্যাপতি সংস্কৃত কাব্য ও অলংকারশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। গীতগোবিন্দের ললিতকলামাধারীর তিনি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর পদাবলীতে এই দুই প্রভাব স্বতোৎসারিত। অলংকার শাস্ত্রানসারে তিনি রাধাকৃষ্ণের পর্বেরাগ, প্রথম মিলন, বাসকসজ্জা, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি লীলা পর্যায়ে তাঁর পদগুলিকে সজ্জিত করেছেন। ফলে তাতে আছে ঘটনার একটি ধারাবাহিকতা। অন্যপক্ষে ভাষা, পদবন্ধ ও চিত্রকল্প বয়নে তিনি ছিলেন অপরূপে রূপকার। মডনকলায় জয়দেবের সঙ্গেই তিনি তালনীয়। এই 'কবি সার্বভৌমে'র কাব্যকৃতির দুটি স্তর লক্ষ্য করেছেন সমালোচক। একটিতে মনোভঙ্গির প্রাধান্য, অন্যটিতে প্রাণভঙ্গির। ছন্দ ব্যবহারে তিনি ছিলেন নিপণে শিল্পী, অলংকার রচনায় দক্ষ কারিগর। সব মিলিয়ে বিদ্যাপতির পদ সাহিত্যের অনন্য সম্পদ ।তব, বিদ্যাপতি পদ নিখুঁত নয়। তাঁর রচনায় বিলাসের বীণা যত বেজেছে, ছন্দের
নিক্কণ যত ধ্বনিত, বেদনার বাঁশি তত বাজেনি। তাতে যত আছে ঐবর্ষ", তত নাই
গভীরতা। বাস্তবতা ও রমণীয়তার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগে উপেক্ষিত হয়েছে
আধ্যাত্মিকতা। দেহাতীত নয়, রপেজ প্রেমেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ ।
নিক্কণ যত ধ্বনিত, বেদনার বাঁশি তত বাজেনি। তাতে যত আছে ঐবর্ষ", তত নাই
গভীরতা। বাস্তবতা ও রমণীয়তার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগে উপেক্ষিত হয়েছে
আধ্যাত্মিকতা। দেহাতীত নয়, রপেজ প্রেমেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ ।
অভিসার, বিরহ ভাবসম্মিলন ও প্রার্থনার পদরচনায় বিদ্যাপতি অনন্য । বিরহাতরা রাধা যখন বলেন :
শানে ভেল মন্দির শনে ভেল নগরী।শনে ভেল দশ দিশ শনে ভেল সগরী ॥
অথবা কবি যখন প্রার্থনা করেন
মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপি'ল;
দয়া জন, ছোড়বি মোয় ।।
হয়ত খাজে পাওয়া যায় না কোনো সাধক বৈষ্ণব কবিকে, কিন্তু পেতে অসুবিধা হয় না অনভব গাঢ় একটি শ্রেষ্ঠ কবি আত্মাকে। প্রেমের রহস্য, প্রেমিকার মনস্তত্ত, ভাষার দীপ্তি, ছন্দ-অলংকারের সৌকর্য' প্রকাশে বিদ্যাপতি সে গেও ছিলেন। অতুলনীয়।
পরের যুগে যে বাঙালী কবির উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল তাঁর নাম গোবিন্দদাস। তিনি ষোড়শ শতকে জন্মগ্রহণ করেন।
Tags
ইতিহাস
Bengali
Class 1
Class 10
Class 11
Class 12
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 7
Class 8
Class 9
Class B.A
Class B.ED
Class D.ED
Class M.A
Class P.G
Class PHD
Class U.G



.png)