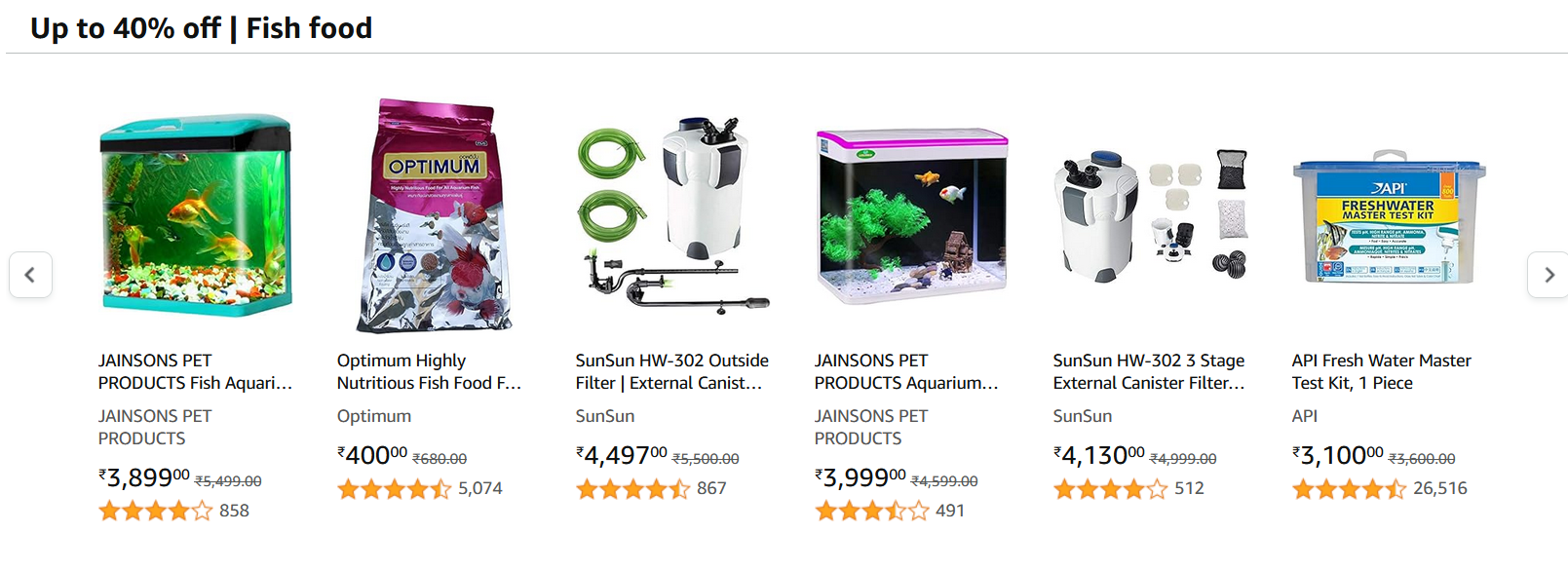তুর্কী বিজয় ও তার ফলশ্রুতি
ত্রয়োদশ শতকের শরতেই মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির 'নদীয়া' জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ইতিপূর্বে আর্যাবর্তের অন্য অংশে শিক হণে দল পাঠান মোগলে'র প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা দেশ ব্যতিক্রম হিসাবেই আপন স্বাধীনতা অক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনৈক শেখ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলেও ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে প্রচার অথবা প্রসার লাভ করেনি। তর্ক বিজয় আর্যভবনের পরে বাংলা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক বিরাট রূপান্তরের সচেনা করল, যা কেবল আর্য ও ইংরেজ আগমনের প্রভাবের সঙ্গেই তালনীয়।
তুর্কী আক্রমণের সামগ্রিক ফলাফল বিচার করে তুর্কী আমলকে 'তামস গ' (The Dark Age) নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতে শাসককালের অন্তর্নিহিত বন্দ। পারস্পরিক হত্যালীলা, নৃশংসতা, ধর্মান্ধতা, পরধর্ম বিদ্বেষ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন লিকে নিশ্চিহ্ন করার উদগ্র প্রবৃত্তি সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর যে আঘাত হেনেছিল তাতে বাংলার জীবন-আকাশ পূর্ণ তমসাবৃতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে এই দঃনের দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়ে নবযুগের ঊষাকিরণপাতও সম্ভব হয়েছিল। 'রাত্রির তপস্যা' ঈতি দিনের শুভ সূচনা না করলেও নবদিবসের আরম্ভ সংচিত করেছিল ।
যে ঘণ্য চক্রান্তে রাজপ্রাসাদ কলষিত ছিল তার বিষবাষ্প অবশ্য প্রাসাদের বাইরে সাধারণ জনজীবনে বিশেষ কোনো ছায়াপাত করতে পারেনি। রাজশক্তির সঙ্গে জন জীবনের বিচ্ছিন্নতার জন্য সমাজ ছিল এই নৃশংস পাশবিকতার মকে সাক্ষী মাত্র। সতরাং সে-ইতিহাস শব্ধে, রাজার ইতিহাস, বৃহত্তর বাঙালী সমাজের পরিচয় ভাতে নেই ।
এতকাল বাঙালী ছিল স্বাধীন, কিন্তু আপন সীমায় বন্ধ। তুর্কী শাসকের অতিরিক্ত ক্ষমতার লোভ ও অর্থ লোল পতা এবং স্বাধীন রাজা হওয়ার বাসনা দিল্লির সম্রাটের দৃষ্টি এই প্রান্তীয় রাজ্যটির উপর নিপতিত করল। দিলির সম্রাটের সঙ্গে বিবাদে ও যুদ্ধের পরিণামে বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি রাষ্ট্রনৈতিকভাবে ভারতীয় জনজীবনের বৃহৎ পরিসরের অঙ্গীভূত হয়ে গেল ।
প্রাক্-তুর্কী আক্রমণকালে বাঙালী ধর্মপ্রাণ, কৃষিনির্ভর জাতি হিসাবে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছিল। সে সমাজে দারিদ্র্য হয়ত ছিল, কিন্তু অভাব-অনটনের তীব্রতা ছিল না। বাংলার কৃষিজ সম্পদও শিল্পজাত দ্রব্য বরং বাঙালীকে সংখের মুখেই দেখিয়েছিল। তার্কী আক্রমণের পরে ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে যোগসূত্রে বাংলার অর্থনীতিতে নতেন দিক সূচিত হল। বাংলার কৃষিজ শিল্পজাত সম্পদ ( বিশেষভাবে রেশমী কাপড়, কাগজ ইত্যাদি ) বাংলার বাইরে বিক্রীত হয়ে অর্থাগমের নবদিগন্ত উন্মোচন করল। কিন্তু এর ফলে বাঙালী শধে, লাভবানই হতে পারেনি। বাঙালীর অর্থ" শাসকশ্রেণীর দ্বারা বাংলার বাইরেও প্রেরিত হল। যুদ্ধবিগ্রহে অর্থনাশ ছাড়া দিল্লির সালতানের বশ্যতার স্বীকৃতির পও বাংলার অর্থ দিল্লির সালতানের কোষাগারে জমা পড়ল। ইলতুৎমিসের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ খিলজির যুদ্ধের পরিণামে জরিমানা স্বরূপে আশি লক্ষ টাকা দিল্লির সালতানকে দিতে হয় । ফলত অর্থাগম ও অর্থ ক্ষতি দায়েরই কারণ হয়েছিল তুর্কী আক্রমণ ও শাসন। তথাপি বাংলাদেশ সেকালে ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। মার্কোপোলা (১৩শ শতকে বাংলায় আসেন ) এবং ইবনে বত তার ( ১৪শ শতকে আসেন) বিবরণ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বত, তার তথ্য কল্পিত নয়। তিনি জানিয়েছেন তৎকালে সাত টাকায় ২৮ মণ ধান বা প্রায় ৯ মণ চাল, সাড়ে তিন টাকায় ১৪ সের ঘি, অথবা ১৪ সের চিি পাওয়া যেত। এই তথ্য বাঙালীর সচ্ছলতারই নিদর্শন।
তার্কী আক্রমণের ফলে গ্রাম-নির্ভর বাঙালী সমাজে নগরের সূত্রপাত ঘটল ! রাজ্যশাসনকে কেন্দ্র করে, ব্যবসার কেন্দ্ররূপে বর্ধিষ্ণ, গ্রাম গৌড়, লক্ষ্মণাবতী, তাণ্ডা, দেবকোট, পান্ডুয়া ইত্যাদি নগরে পরিণত হল ।
তার্কী আক্রমণের ফলে বাঙালী সমাজ নবভাবে গঠিত হল। তুর্কী শাসকের আমন্ত্রণে পীর, ফকির, আউলিয়া, মুরশিদ ইত্যাদি ধর্মগিরেরা বাংলা দেশে এলেন। প্রলোভন ও উৎপীড়ন দইে পদ্ধতিতেই তাঁরা হিন্দাদের মসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে লাগলেন। হিন্দু সমাজের অনদার নীতিও এব্যাপারে তাঁদের কম সহযোগিতা করেনি। অন্ত্যজ শ্রেণীভক্ত করে বাঙালীর এক বৃহৎ গোষ্ঠীর জন্য ইতিপূর্বেই মন্দির বার রদ্ধে করা হয়েছিল। তাছাড়া বৌদ্ধরাও ব্রাহ্মণদের হাতে কম উৎপীড়িত হন নি। ফলত এই পাটি বাঙালীগোষ্ঠী দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হয়ে সামাজিক বিন্যাসের নতেন দিক সাচিত করল। ইসলাম ধর্মে'র প্রসারে হিন্দ ও মাসলমান এই দুই ধর্ম মত বাংলাদেশের প্রধান দুই ধর্মমতে পরিণত হল। শাসক- কালের দ্বারা আমন্ত্রিত পীর, ফকির, দরবেশ সম্প্রদায় এবং ধর্মান্তরিত হিন্দ, অর্থাৎ নব মুসলমানরা মিশে বাংলাদেশে সংখ্যাগতভাবে উল্লেখযোগ্য একটি মুসলমান সম্প্রদায় সৃষ্টি করল।
তুর্কী আগমনের প্রথম পর্যায়ে হিন্দ, নিধন ও নির্যাতনই ছিল শাসকদের লক্ষ্য।
সতেরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ভেদরেখা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু
পরবর্তীকালে সম্প্রদায় নির্বিশেষে যোগ্য ব্যাক্তিকে রাজকার্যে নিযুক্ত
করায় সামাজিক এই বিভেদের রেখা অনেকটা দূরীভতে হয়।
করেছিল। তার আগেও এদেশে ব্রাহ্মণ ছিল, কিন্তু বৈদিক ধর্মাচরণ প্রচলিত ছিল
না। নবাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শাসকশ্রেণীর আনকলো বাংলাদেশে সমাজপতির আসন
গ্রহণ করেছিল, আর পরনো ব্রাহ্মণেরা বর্ণরাহ্মণে অথবা ব্রাহ্মণ্ডের জাতির
অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। লোকায়ত ধর্ম ছিল আচার-অনষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ
সামাজিক ব্যাপার এবং প্রধানত নিম্নবর্ণের বাঙালীর ধর্ম চর্চার উৎস। ফলে
তুর্কী আক্রমণের কালে বাংলাদেশে প্রধানত চারটি ধর্ম মত প্রচলিত ছিল:
প্রাচীন ঐতিহ্য অনসারী ধর্ম (প্রাক-আর্য যুগ থেকে নব গৃহীত নানা দেবদেবী এই
ধর্মে'র অন্তর্ভুক্ত ), বৌদ্ধ-মহাযান ধর্মে'র রূপান্তর সহজিয়া ধর্মমত,
নাথধর্ম ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম' (বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী এই ধর্ম মতের
প্রধান দেব-দেবী)। তুর্কী আক্রমণের দু-তিন শতকের মধ্যেই চারটি ধারা পৌরাণিক
ও অপৌরাণিক ( অর্থাৎ লোকায়ত ) এই দুটি ধারায় পরিণত হল। মধ্যযুগের বাংলা
সাহিত্যে আবার এই উভয়বিধ ধারার দেবদেবী স্বাতন্ত্র্য সত্তেও অভিন্ন বলে
পরিগণিত হলেন। চণ্ডী ও দর্গ, ভাঙড় ভোলানাথ ও মহাদেবের মিলন ঘটল এভাবে।



.png)