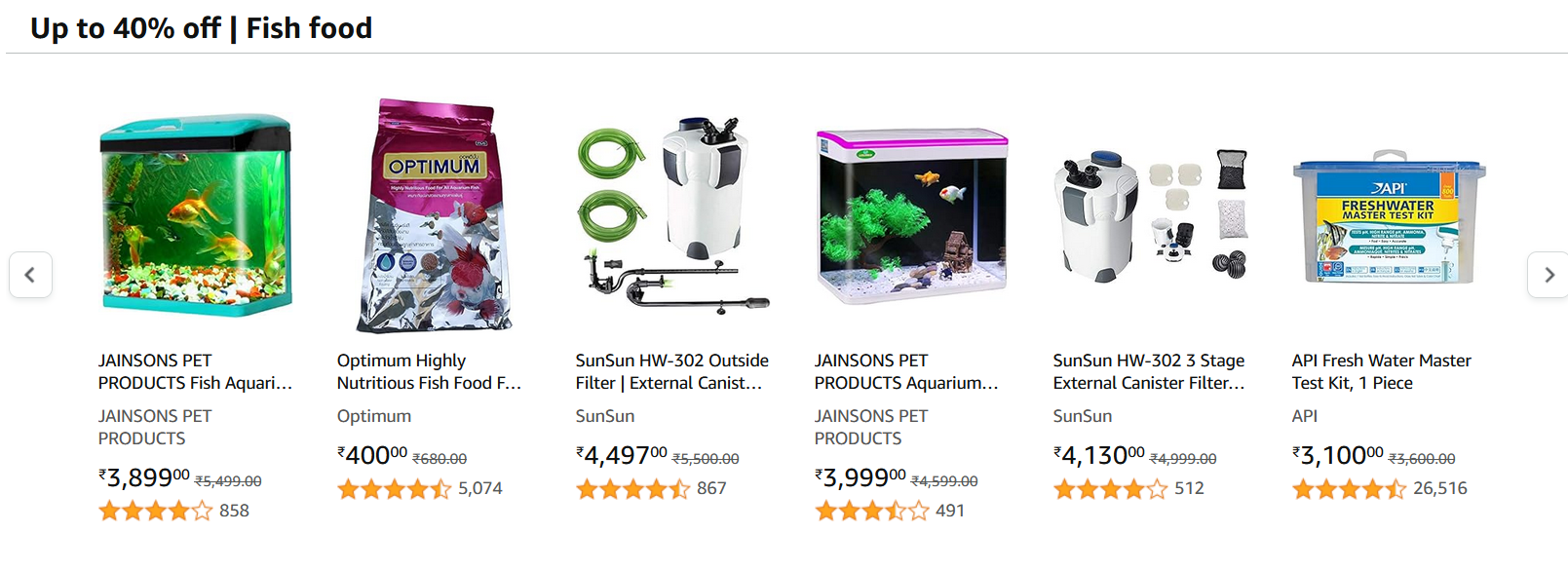চর্যাপদে চিত্রিত সমাজচিত্র :
নদীমাতৃক বাংলার চারদিকে খালবিল, 'বাম দাহিন জো খালবিখলা'। তাছাড়া কোথাও কোথাও আছে 'উচা উচা পাবত'। সেখানে বাস করে অস্পৃশ্য শবর জাতি। তাদের 'হাঁড়ীত ভাত নাহি। তব, বাঙালী চিরকালই অতিথি পরায়ণ। সেজন্যই আছে নিত্য অতিথি সমাগম — "নিতি আবেশী। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ধান যখন পাকে আনন্দের সীমা থাকে না বাঙালীর মনে- 'কঙ্গ চিনা পাবেনা রে শবর শবরী মালো'। আনন্দ প্রকাশের উপায় নাচ-গান-বাজনা - নাচন্তি বাজিল গান্তি "দেবী। সাজসজ্জাতেও বাঙালীর বড় অন রাগ। বস্ত্রের উপকরণ কাপাস তুলার অভাব নেই –‘কড় এবেরে কপাস, ফাটিলা। জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণদের চিন্তা কম। তাম্রশাসন ('শাসনপড়া) দ্বারা রাজা তাদের নিষ্কর জমি ভোগের সুযোগ দেন। হরি, ব্রহ্মা, আগম-পথিপাঠ নিয়ে কাটে তাদের সময়। কিন্তু আছে চোর ডাকাতের ভয়—'অদঅ বঙ্গালে লড়িউ, 'চৌকড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ সেস। ডাকাত ছাড়া আছে চোর—'কানেট চোরে নিল অধরাতী'। অবশ্য চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে রক্ষা -করতে ছিল প্রহরী 'তথতা পহারী'। তালাচাবিরও ব্যবস্থা ছিল- 'কোণ্ডা ভাল'। আর ছিল দারোগা—'দুযোধী, থানা ছিল, কাছারিও 'উআরি'। সর্বোপরি ছিল সখী দাম্পত্য জীবন— 'জোইনি জালে রজনী পোহা'।
মায়া,চর্যাগীতি ধর্ম—-সংগীত—যে ধর্মে বলা হয়েছে জীবন ও জগৎ অসার, অলীক, মিথ্যা চর্যা-রচয়িতা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য এ-জগতকে ভালবাসতে পারেননি।জাগতিক দঃখ থেকে মুক্তিই ছিল তাঁদের কামনা। সতরাং জীবনানরোগ অথবাঃ
জগৎ-প্রীতি তাঁদের রচনায় আশা করা অনুচিত। কিন্তু তত্ত কথাকে তাঁদের রূপে।
দিতে হয়েছে এই তথাকথিত অস্তিত্বহীন জীবনের উপমানে। ফলত, সমাজ-চিত্র ও
সাহিত্যসম্পদ সেখানে উদ্দেশ্য না হয়েও অদৃশ্য থাকেনি।
ছিল এ-কালের মতোই। বিবাহে যৌতুক গ্রহণ বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় ছিল দাবা খেলা, নাচগান ও অভিনয় ।
চর্যায় সাহিত্য সম্পদ :
জগৎ-প্রীতি তাঁদের রচনায় আশা করা অনুচিত। কিন্তু তত্ত কথাকে তাঁদের রূপে।
দিতে হয়েছে এই তথাকথিত অস্তিত্বহীন জীবনের উপমানে। ফলত, সমাজ-চিত্র ও
সাহিত্যসম্পদ সেখানে উদ্দেশ্য না হয়েও অদৃশ্য থাকেনি।
চর্যাপদে ডোম, শবর, চণ্ডাল, কাপালিক ইত্যাদি নিম্নবর্ণের লোকের কথাই বেশি । ব্রাহ্মণেরা তাদের অস্পৃশ্য মনে করত। ডোমেরা থাকত গ্রাম বা নগরের বাইরে, তাদের বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা, ঝুড়ি-গড়ি তৈরি ও খেয়া পারাপার। নৃত্যে তারা ছিল বিশেষ পারদর্শী। শহরেরা পাহাড়ে, বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, পশ, শিকারে অভ্যস্ত ছিল। গলায় গুঞ্জাফলের মালা, মাথায় ময়ূরেপচ্ছে ও কানে বজ কণ্ডেল ধারণ ছিল তাদের বিলাস। সঙ্গীতে তারাও পারদর্শী ছিল। কাপালিকদের স্থান ছিল সবার নিচে। তারা নরকঙ্কালের মালা পরে নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াত ।
অন্ত্যজ শ্রেণীর বৃত্তির মধ্যে ছিল ধান ও তুলার চাষ, কাপড় বোনা, মদ তৈরি, কাঠের কাজ। অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকেরা ছিল শ্রমজীবী, কায়িক শ্রমই ছিল তাদের সম্পদ। শ্রমের বিনিময়ে জটত না উপযুক্ত অর্থ'। সতরাং অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন- যাপনও ছিল অনন্নত। অন্যপক্ষে, ব্রাহ্মণেরা রাজান, গ্রহে নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করত, সোনা-রূপাও দান হিসাবে পেত। তাদের বৃত্তি ছিল বেদানা কলে শাস্ত্ৰচর্চা। ফলে কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হত না, অর্থেরও অভাব ছিল না। সেই সমাজে চোর-ডাকাতের উপদ্রব অজানা ছিল না, সেজন্য তালাচাবি, প্রহরী, দারোগা ও কাছারির ব্যবস্থাও ছিল।
*শর-শাশাড়ি-ননদ, শালী- স্ত্রী-ছেলের বৌ নিয়ে ছিল সেকালের যৌথ পরিবার, সেখানে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের সুযোগ ছিল না।
বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান করা হত, নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেছিল এ-কালের মতোই। বিবাহে যৌতুক গ্রহণ বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় ছিল দাবা খেলা, নাচগান ও অভিনয় ।
চর্যায় সাহিত্য সম্পদ :
বৈচিত্র্যময় জীবনের খণ্ডচিত্রই চর্যায় লভ্য। সে চিত্রে যেমন আছে সমাজ-পরিচয়। তেমনি আছে সাহিত্যসম্পদ। চর্যাগানে প্রধানত জীবনের দুটি অন ভবের প্রকাশ- বিষাদ ও শঙ্গার। নিসর্গ প্রীতিও অলক্ষ্য থাকেনি।
বিষাদবোধ ফটে উঠেছে সামাজিক অভাব, অত্যাচার ও অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে।
টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ৷
লোকালয়ে বাস অথচ নাই প্রতিবেশী। ঘরে নাই অন্ন অথচ অতিথির নিত্য সমাগম।
একটি গানে বলা হয়েছে নির্দয় জলদস্য, দেশ লণ্ঠন করল, নিজের গৃহিণীকে অপহরণ
করল চণ্ডাল। আগে পরিবার নিয়ে ছিলাম মহাসঃখে; এখন সোনার পা কিছুই থাকল না—
'জীবন্তে মইলে নাহি বিশেষ— এখন মরা বাঁচা দইই সমান ।
শৃঙ্গারের প্রকাশ প্রধানত গণ্ডেরীপাদ ও শবর পাদের রচনায়। শবরপাদ প্রেমিকার রূপবর্ণনায় বলেছেন 'মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গঞ্জেরী মালী'-শবরীর পরণে ময়ূরের পালক, গলায় গুঞ্জাফলের মালা, তাকে দেখে— 'উমতো শবরো'- শবর উন্মত্ত।
নিসর্গ' সৌন্দর্য চর্যাগানে প্রাধান্য না পেলেও চিত্রিত। 'নানা তরুবর মউলিলরে 'গঅণত লাগেলী ডালী' – নানা তরবের মক্কলিত, তাদের পুষ্পিত শাখা আকাশে লেগেছে; অথবা
তইলা বাড়ীর পাসে'র জোহা বাড়ী উএলা।ফিটোল অন্ধারিরে আকাশ ফলিআ ৷৷
সেই বাড়ির পাশের জ্যোৎস্নায় বাড়ি উজ্জ্বল, অন্ধকার কেটে যাওয়ায় মনে হচ্ছে আকাশ জুড়ে ফল ফুটেছে। এ তো যেন সাধনসঙ্গীত নয়, কোনো কবিমনের অন্তরঙ্গ প্রকাশ। এই পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাকা কঙ্গ চিনা ধানের ঘ্যাণ, তাতে মিলনমত্ত হয়েছে শবর-শবরী- এ চিত্রে 'সন্ধ্যাভাষা'র রহস্যময়তার অন্তরাল ভেদ করে বেরিয়ে আসে জীবন-রহস্য – সাহিত্য সম্পদ।
বিষাদ, নিসর্গ ও প্রেম– রোম্যান্টিক কবিতা তথা বাংলা কবিতার তিন মখ্য উপাদান- চর্যাগানকেও সাহিত্যসম্পদে ভরিয়ে তালেছে। বস্ত্ত চর্যার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবলগ্নেই বাংলা সাহিত্যের মূলে প্রকৃতিটি পরিস্ফুট হতে পেরেছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির প্রধান কারণ এই শৈশবে আত্ম-আবিষ্কার।
পদকর্তারা নানা প্রকার নিগড়ে তান্ত্রিক ধর্মাচরণের কথা বলেছেন গানগুলিতে এবং সেটিই ছিল গীত রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তারই ফাঁকে পাওয়া গেছে তাঁদের কবিপ্রতিভা, ছন্দ ও রূপনির্মাণ পদ্ধতির পরিচয়। বাংলার বিশিষ্ট ছন্দ এবং প্রাক-আধুনিক যুগের কবিতায় সর্বত্র ব্যবহৃত ছন্দ পয়ার ও ত্রিপদীর আদি নিদর্শন পাওয়া যায় পদগুলিতে। নির্বাণতত্তকে অনেক পদে দয়িতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যেও দয়িত-দয়িতার রূপক বিশেষ মর্যাদা পায়।
-সতেরাং চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যের পরিচয়ই শঙ্খ, নয়, বাংলা কাব্য
- কামলিপাদের একটি গানে আছে—
- কামলিপাদের একটি গানে আছে—
রীতিরও পরিচয়।
সোনে ভরিতী করুণা নাবী।রূপো থোই নহিকে ঠাবী ॥ (৮ নং চৰ্যা )
-
করণার পে নৌকা সোনায় ভর্তি, রূপা রাখার স্থান নাই — শন্যতা-জ্ঞানে (সোনা )
করণা নৌকা পূর্ণে, ইন্দ্রিয় জগতের মিথ্যা জ্ঞান ( রূপা) রাখার জায়গা
-নাই সেখানে। একথা হয়ত নিৰ্বাণতত্ত সম্পর্কে সত্য; কিন্তু চর্যাগানে আমরা
পাই -সহজযানের ধর্ম-দর্শন-সাধনরীতিরূপ সোনার সঙ্গে দৃশ্যমান' রূপ জগতের
রূপকায়িত -পরিচয়ও।'
করণা নৌকা পূর্ণে, ইন্দ্রিয় জগতের মিথ্যা জ্ঞান ( রূপা) রাখার জায়গা
-নাই সেখানে। একথা হয়ত নিৰ্বাণতত্ত সম্পর্কে সত্য; কিন্তু চর্যাগানে আমরা
পাই -সহজযানের ধর্ম-দর্শন-সাধনরীতিরূপ সোনার সঙ্গে দৃশ্যমান' রূপ জগতের
রূপকায়িত -পরিচয়ও।'
Tags
ইতিহাস
Bengali
Class 1
Class 10
Class 11
Class 12
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5
Class 7
Class 8
Class 9
Class B.A
Class B.ED
Class D.ED
Class M.A
Class P.G
Class PHD
Class U.G



.png)